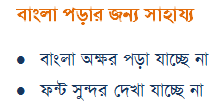আ রা কা নে র ই তি হা স
৮
নে উইনের শেষ আঘাত
ক্ষমতা দখলের আগে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে শুরু করে জেনারেল নে উইন আরাকানের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর যতবার যতভাবে আঘাত করেছেন, প্রতিটি আঘাতই ছিলো একটি জাতির কোমর ভেঙ্গে দেয়ার মত। তবে সবচে’ চূড়ান্ত এবং সবচে’ ভয়াবহ আঘাতটা এসেছে ১৯৮২ সালের ১৫ই অক্টোবর।
বার্মার সামরিক সরকার সেদিন নাগরিকত্ব আইন নামে এমন একটা কালো আইন পাশ করে, যা আরাকানভূমিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের অস্তিত্ব ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কেই অস্বীকার করার শামিল।
এই একটা আইনের মাধ্যমেই আরাকানের বিশাল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আরাকান ও বার্মার নাগরিকত্ব থেকে আইনগত ভাবেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে। শত শত বছর ধরে আরাকানের ভূমিতে তাদের অধিবাস, তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি, কবর ও কবরস্তান সবকিছ মুহূর্তের মধ্যে যেন ‘মিথ্যা’ হয়ে যায়। তারা হয়ে পড়ে রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী। বলাবাহুল্য, ফিলিস্তীনীদের পর রোহিঙ্গারাই হলো পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী। তবে ফিলিস্তীনের মুসলিমান তাদের পিতৃভূমির কিছু অংশ হলেও এখনো দখলে রাখতে পেরেছে। পক্ষান্তরে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী আরাকানের একখ- ভূমিরও মালিকানা রক্ষা করতে পারেনি। তাছাড়া ফিলিস্তীনের আরব মুসলিম জনগোষ্ঠী যারা ইহুদিবাদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে আজ নিজেদের হাজার বছরের পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত, তাদের পক্ষে জাতিসঙ্ঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মুখের প্রতিবাদটুকু হলেও করেছে। ইহুদীবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করেছে এবং একের পর এক প্রস্তাব পাশ করেছে। কিন্তু আরাকানের মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী! তারা এমনই দুর্ভাগা যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মৌখিক সমবেদনাটুকুও তাদের ভাগ্যে জুটেনি। জাতিসঙ্ঘ তো এখনো পর্যন্ত সিদ্ধান্তই নিতে পারেনি যে, মিয়ানমারের সামরিক জান্তার হাতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যে জাতিগত নিধনের শিকার হয়েছে তার জন্য উপযুক্ত শব্দ কী হতে পারে! অনেক ভেবে চিন্তে জাতিসঙ্ঘ প্রধান বলেছেন, এটা হচ্ছে জাতিগত নিধনযজ্ঞের ‘পাঠ্যপুস্তকীয় উদাহরণ’, কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদ তাতে আবার একমত হতে পারেনি। তামাশা আর কাকে বলে!
নাগরিকত্ব আইনের স্বরূপ
স্বাধীনতা লাভের আগে থেকেই বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিভিন্ন মঞ্চ থেকে এবং বিভিন্ন আড়াল অবলম্বন করে জোর প্রচারণা চালাতে থাকে যে, রোহিঙ্গা নামে কোন জনগোষ্ঠী বার্মার ভূখ-ে কখনো ছিলো না, এখনো নেই। আসলে এরা ভারতের বাংলা প্রদেশ থেকে, বিশেষ করে পূর্ববাংলা থেকে অনুপ্রবেশকারী অবৈধ জনগোষ্ঠী। বৃটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘রাখাইনে’ এরা ভূমি দখল করে বসতি গড়ে তুলেছে।
নতুন আইন অনুযায়ী তারাই শুধু বার্মার বৈধ নাগরিক বলে গণ্য হবে যারা বৃটিশ দখলদারির পূর্ব থেকে বার্মায় বসবাস করে আসছে। এর পরে, অর্থাৎ বৃটিশ দখলদারির আমলে যারা বার্মায় এসেছে তারা নাগরিকত্ব লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। এর অর্থ কী দাঁড়ায়? এর অর্থ তো শুধু এই দাঁড়ায় যে, বার্মা যে একসময় বৃটিশ ভারতের একটি প্রদেশ ছিলো তা গায়ের জোরে অস্বীকার করা হচ্ছে। এমনকি বাংলাপ্রদেশের সঙ্গে আরাকানের দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক যোগাযোগ ছিলো তাও বেমালুম ভুলে যাওয়া হচ্ছে। সর্বোপরি এটা তো ইতিহাসের অকাট্য সত্য এবং ইতিপূর্বে আমরা তা আলোচনা করে এসেছি যে, বর্মিজ শাসক বোধপায়ার আরাকান দখলের বহু পূর্ব থেকেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আরাকানের ভূমিতে বিদ্যমান ছিলো এবং এ জনগোষ্ঠী শুধু বাঙ্গালী রক্ত দ্বারা গড়ে উঠেনি, বরং এর প্রথম উপাদান ছিলো আরব রক্ত, তারপর পারসিক রক্ত, তারপর মোঘল রক্ত, তারপর চতুর্থ পর্যায়ে হলো বাঙ্গালী রক্ত।
আলোচ্য আইনে সহযোগী নাগরিক হিসাবে অদ্ভুত একটা ধারা তৈরী করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, যারা ১৯৪৮ সালের নাগরিকত্ব অ্যাক্টের অধীনে আগেই নাগরিকত্বের আবেদন করেছে তাদের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যারা যুগ যুগ ধরে আরাকানের ভূমিতে বসবাস করে আসছে, কোন্ বিবেচনায় তারা এরূপ আবেদন করবে? রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্যরা কি এ আবেদন করেছে, না তাদের করতে বলা হয়েছে? এরূপ আবেদন করার অর্থ কি এটা দাঁড়ায় না যে, নিজেরাই আগে বেড়ে নিজেদের শত শত বছরের অধিবাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে?
আরো অদ্ভুত একটা জিনিস হলো ‘অভিবাসী নাগরিক’। অর্থাৎ যারা জন্মসূত্রে বার্মার নাগরিক নয় তারা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবে, তবে কয়েকটি শর্তে। যথা-
যারা বার্মার স্বাধীনতা লাভের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারির পূর্বে বার্মায় প্রবেশ করেছে এবং যাদের সন্তান বার্মায় জন্মগ্রহণ করেছে। আর এ দু’টো বিষয় সরকারী কাগজপত্র তথা দালিলিক প্রমাণের মাধ্যমে তাদেরই সাব্বস্ত করতে হবে।
তাছাড়া বার্মার রাষ্ট্রীয় ভাষায় তাদের দক্ষ হতে হবে।
বলাবাহুল্য যে, অশিক্ষিত ও প্রায় নিরক্ষর এবং অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত, সর্বোপরি বারবার যারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, জাতিগত নিধন, উচ্ছেদ, জ¦ালাও পোড়াও এবং ভয়াবহ গণহত্যার শিকার হয়েছে এমন একটি জনগোষ্ঠীর পক্ষে ‘কাগজপত্র’ উপস্থিত করে এরূপ আইনী জটিলতা অতিক্রম করা শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভবও। তাছাড়া বার্মার সংবিধানে কোথাও এটা নেই যে, প্রতিটি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সদস্যকে বর্মিজ ভাষা জানতে হবে, তদুপরি তাতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাছাড়া নাগরিকত্ব প্রদানের দায়িত্ব যে কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে ঐ কমিটির প্রত্যেক সদস্যই ছিলো রোহিঙ্গা বিদ্বেষী মগজন-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যে কোন অজুহাতে, এমনকি বিনা অজুহাতেও তাদের অধিকার ছিলো যে কোন ‘কাগজ’ প্রত্যাখ্যান করার।
নাগরিকত্ব আইন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিন্দা সমালোচনা এড়ানোর জন্য সামরিক জান্তা শুরুতে বেশ কৌশলী নীতি অনুসরণ করেছে। প্রথম দিকে আইনটার তেমন প্রয়োগ দেখা যায়নি। বলা যায়, এটা ছিলো সামরিক জান্তার পক্ষ হতে তৈরী করা একটা টাইম বোমা, যা খুব নীরবে শুধু টিক টিক করে বিস্ফোরণের নির্ধারিত সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। এত ধীরে ধীরে একং এত নিঃশব্দ পর্যায়ক্রমে এটা প্রয়োগ করা হচ্ছিলো যে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বলতে গেলে কোন প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হয়নি। যেমন ১৯৮৯ সালে তিন ধরনের নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র জারি করা হয়। পূর্ণাঙ্গ নাগরিকত্বের জন্য গোলাপী রঙের পরিচয়পত্র, সহযোগী নাগরিকত্বের জন্য নীল রঙের পরিচয়পত্র, আর অভিবাসী নাগরিকত্বের জন্য সবুজ রঙের পরিচয়পত্র।
আশ্চর্যের বিষয় হলো, হাজার বছর ধরে আরকানের ভূমিতে বসবাস-কারী, যাদের ঘাম ও শ্রমের বিনিময়ে আরাকানের বিশাল পতিত জমি ও জঙ্গলভূমি আবাদযোগ্য হয়েছে, যাদের পূর্বপুরুষ আরাকানকে সবুজশ্যামল শস্যভা-ারে রূপান্তরিত করার জন্য মৃত্যুর ঝুঁকি বরণ করেছে, এমনকি হিং¯্র প্রাণীর খোরাকে পরিণত হয়েছে, তাদের কোন প্রকার কার্ডই প্রদান করা হয়নি, না গোলাপী, না নীল, আর না সবুজ। তাই যৌক্তিক কারণেই এটাকে বলা যায় সহজ সরল রোহিঙ্গাজন-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এটা ছিলো সামরিক জান্তার ‘তেরঙ্গা’ ষড়যন্ত্র।
ধীরে ধীরে চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, এমনকি শিক্ষা ও চিকিৎসার মত ক্ষেত্রেও পরিচয়পত্রের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। আর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, অবশেষে তাদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় সাদা রঙ্গের কার্ড।
প্রথমে তেমন করে বুঝতে না পারলেও একসময় তারা ঠিকই বুঝতে পারে, এই ‘তেরঙ্গা’ চক্রান্ত তাদের জাতীয় জীবনে কত বড় সর্বনাশ ডেকে এনেছে!
প্রথমে তারা দেখতে পায় ব্যবসা বাণিজ্য এবং সরকারী বেসরকারী সর্বপ্রকার চাকুরীতে তারা প্রবেশাধিকার হারিয়েছে, কারণ তাদের হাতে গোলাপী, নীল ও সবুজ কোন রঙ্গের কার্ডই নেই। তখনো শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়নি। সরকারী বড় হাসপাতাল- গুলোতে রোহিঙ্গাদের চিকিৎসা-গ্রহণ পদ্ধতিগত কারণে নিষিদ্ধ হলেও উত্তর আরাকানের সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে তাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যসেবা তখনো চালু ছিলো। অবশেষে শিক্ষাঙ্গন ও হাসপাতালের দুয়ারও তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেলো। আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সেবাসংস্থাগুলো বিভিন্ন-ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো রোহিঙ্গাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু করার, কিন্তু জ্যান্তা সরকারের চরম নেতিবাচক ভূমিকার কারণে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়, এমনকি সর্বশেষ একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো কতিপয় রোহিঙ্গা নারীকে ধাত্রিবিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রদানের, যাতে জরুরি মুহূর্তে তারা মুমূর্ষু রোগীর কাজে আসতে পারে। সেটাও সম্ভব হয়নি, সরকারের অসহযোগিতার কারণে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বার্মা সরকারের হঠকারিতার কাছে জাতিসঙ্ঘ ও তার সমর্থনপুষ্ট সংস্থাগুলো এতটাই অসহায়ত্ব প্রদর্শন করছিলো যে, বিশ^াসই হতে চায় না, এরাই পূর্বতিমুরে এবং দক্ষিণ সুদানে ...।
সম্প্রতি জনৈক মার্কিন কংগ্রেস সদস্য প্রস্তাব করেছেন, আরাকানের ভূখ-কে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়ার, যাতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়। যদিও প্রস্তাবটা নিছক ‘তামাশা’, তবু এ প্রসঙ্গে তিনি মার্কিন জাতির সামনে যে প্রশ্নটি রেখেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, পূর্ব তিমুরে যদি আমেরিকাএধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে তাহলে আরাকানে কেন পারবে না?
আসলে প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত রয়েছে। পূর্ব তিমুরে ছিলো খৃস্টান জনগোষ্ঠী, (ফিলিস্তীনে ও) আরাকানে হলো মুসলিম জনগোষ্ঠী।
আরো চারবছর পর ১৯৯৪ সালে রোহিঙ্গা শিশুদের জন্মনিবন্ধন বন্ধ করে দেয়া হয়। এমনিতেও অশিক্ষিত নিরক্ষর রোহিঙ্গাজন-গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মনিবন্ধনবিষয়ক সচেতনতা ছিলো খুবই কম, যার কারণে এ পদক্ষেপ আরাকানে আভ্যন্তরীণ কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করেনি, তবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কিছুটা অস্থিরতা তৈরী হয়। জাতি-সঙ্ঘের উদ্বাস্তুবিষয়ক হাইকমিশনার বেশ জোরালোভাবে দাবী জানাতে শুরু করে নিবন্ধনকার্যক্রম আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য। ফলে ১৯৯৫ সাল থেকে আবার রোহিঙ্গা শিশুদের জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করা হয়।
আইওয়াস হিসাবে রোহিঙ্গাদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় একধরনের সাদা পরিচয়পত্র, যাতে জন্মের স্থান ও তারিখ লেখা ছিলো না। ফলে এই কার্ড না তাদের পক্ষে মিয়ানমারের নাগরিকত্ব প্রমাণ করে, আর না তাদের আরাকানে অবস্থানের বৈধতার সাক্ষ্য দেয়। এককথায় এই সাদা কার্ড তাদের কোন কাজেই আসে না। কিছুদিন পর তাও বন্ধ করে দেয়া হয়। নবজাতক শিশুর নাম শুধু লিখে রাখা হয় নাসাকা বাহিনীর খাতায়।
মিয়ানমারের সামরিক জান্তা অসহায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যে বর্বর ও নিষ্ঠুর আচরণ করছিলো তাতে শুধু একথাই বলা যায় যে, পুরো আরাকানভূমি তাদের জন্য ছিলো এক উন্মুক্ত কারাগার। ভালো করে বুঝুন, উন্মুক্ত কারাগার শব্দটার মধ্যে কোন রূপকতা নেই। শাব্দিক অর্থেই প্রতিটি রোহিঙ্গা গ্রাম ও বসতি তাদের জন্য একটি বড় জেলখানার মতই ছিলো, আর ঐ সব জেলখানায় আক্ষরিক অর্থেই তারা বাস করছিলো বন্দীজীবন। মিয়ানমারের অন্যান্য অঞ্চলে যাওয়া তো দূরের কথা, পাশের গ্রামে কোন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ারও অনুমতি ছিলো না। আধুনিক সভ্যতার আলোতে বাস করে বিশ^াস করা কঠিন, তবু এটাই সত্য যে, পাশের গ্রামে যাওয়ার জন্যও তাদের যোগাড় করতে হতো ‘ট্রাভেল পাস’। আর এটা জারি করার একক ক্ষমতা ছিলো সীমান্তরক্ষী নাসাকার হাতে। বলাবাহুল্য ট্রাভেল পাস যোগাড় করা এতই কঠিন ছিলো যে, একান্ত অনন্যোপায় না হলে নাসাকা-দফতরে যাওয়ার কথা কেউ চিন্তাও করতো না। প্রশাসনিক জটিলতা তো ছিলোই, সেই সঙ্গে ছিলো নাসাকা কর্মকর্তা -দের উগ্র আচরণ বরদাশত করে তাদের ‘সন্তুষ্ট’ করার ‘ধকল’। এরপরো ছিলো আরো বড় ভোগান্তি। অর্থাৎ পাসের মধ্যে গ্রামে ফিরে আসার সময় লেখা থাকতো। কোন কারণে বিলম্ব হলেই শুরু হতো নতুন গর্দিশ। হয় নাসাকার লোকদের হাত ‘গরম’ করো, আর না হয় ‘ছোট’ জেলখানায় গিয়ে গরম পানির সাজা ভোগ করো। হাঁ, এজন্য নির্ধারিত ছিলো দীর্ঘ সময় গরম পানিতে চুবানোর সাজা!
নে উইনের উত্থান পতন পরিণতি
জেনারেল নে উইন জন্মগ্রহণ করেন ১৪ই মে ১৯১১ (মতান্তরে ১০ই জুলাই ১৯১০)। রেঙ্গুন থেকে প্রায় দু’শ মাইল দূরবর্তী পংডেল-এর একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বর্মিজ চীনা পরিবারে তার জন্ম।
সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার মাধ্যমে তার কর্ম জীবনের শুরু। ধীরে ধীরে তিনি সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদে ‘উপনীত’ হন। পেশাদারিত্বের চেয়েও বেশী কুশলতা তিনি প্রদর্শন করেন উপরের ক্ষমতাসীনের সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে। বস্তুত এই কুশলতাই তাকে অল্প সময়ে শীর্ষ পদে উন্নীত হতে সাহায্য করেছে। এমনকি একসময় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী উনু সেনাপ্রধান হিসাবে তার হাতে অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষমতা অর্পণ করেন। (২৯শে অক্টোবর ১৯৫৮ - ৪ঠা এপ্রিল ১৯৬০)
যথাসময়ে উনূর হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করে নে উইন উনূর প্রতি
তার ‘বিশ^স্ততা’র পরিচয় দেন।
তবে তা ছিলো খুবই সাময়িক। ২রা মার্চ ১৯৬২ প্রধানমন্ত্রী উনূকে হতবাক করে দিয়ে সেনাবাহিনীর নামে তিনি ক্ষমতা দখল করে নেন। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম অজ্ঞাত কারণে এ অভ্যুত্থানকে শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীন বলে অভিহিত করে। যদিও এটা সত্য যে, শীর্ষস্থানীয় কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়নি এবং তার প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। তারপরো এটা বাস্তব সত্য যে, নে উইনের সামরিক অভ্যুত্থান যথেষ্ট রক্তপাত ঘটিয়েছিলো সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে যেমন তেমনি বেসামরিক পর্যায়েও।
২রা মার্চ ১৯৭৪ সালে তিনি বিপ্লবী কাউন্সিল বিলুপ্ত করেন এবং সরকারকে বেসামরিক রূপ দিয়ে বার্মার নতুন নাম রাখেন বার্মা সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র। নিজেকে তিনি এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সিন উইনকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন। মূলত এ পর্যন্তই ছিলো তার উত্থানকাল, যা পাঁচ সাত বছর পর্যন্ত স্থিতি লাভ করেছিলো। তারপর থেকেই শুরু হয় তার পতনের প্রক্রিয়া।
রাষ্ট্রপতির পদ থেকে তো তাকে অনেক আগেই ইস্তিফা দিতে হয়েছিলো, তবে ২৩শে জুলাই ১৯৮৮ তিনি দলীয় পদ থেকেও সরে যেতে বাধ্য হন।
এর মধ্যে ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ স মংয়ের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। পুরোনো কৌশল প্রয়োগ করে এখানেও তিনি নিজেকে ক্ষমতার কাছাকাছি রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন এবং কিছুটা কৃতকার্যও হন। তবে ১৯৯৮ থেকে তিনি নয়া সামরিক জান্তার রোষানলে পড়ে যান। প্রথমে কন্যা সান্দার উইন এবং জামাতা আই জ উইনকে দোষী সাব্বস্ত করে মৃত্যুদ- ঘোষণা করা হয়। পরে নে উইনকে রাখা হয় কঠোর গৃহ নজরদারিতে। অন্যদিকে তার তিন পুত্রকেও মৃত্যুদ-ের মুখোমুখি করা হয়। নে উইন হয়ত তখন বুঝতে পেরেছিলেন, ‘মৃত্যু ও হত্যা’ যারা বেঁচে থাকে তাদের জন্য কতটা মর্মজ¦ালার কারণ হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত ঐ সব মৃত্যুদ- কার্যকর করা হয়নি। নে উইনের মৃত্যুর বেশ পরে একে একে তাদের মুক্তি দেয়া হয়।
প্রবল পতাপের অধিকারী এই জান্তার শেষ জীবন ছিলো বড়ই দুর্বিষহ। অন্তরীণ অবস্থায় অত্যন্ত করুণভাবে তার মৃত্যু ঘটে। কথিত আছে, তিনি পানির জন্য যখন ছটফট করছিলেন, কিছু দূরে কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা মদ্যপ অবস্থায় হৈচৈ করছিলেন। তার দিকে ফিরে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করা হয়নি।
৫ই ডিসেম্বর ২০০২ সালে তার মৃত্যু ঘটে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংবাদ-মাধ্যমে খুব সাধারণভাবে তার মৃত্যুর খবর প্রচার করা হয়। তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়নি। মাত্র ত্রিশজন মানুষ তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলো।
নতুন শাসনে আরো দুর্দশায় রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠী
বার্মার রাজনীতিতে সামরিক নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটেছে তবে হতভাগ্য রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর ভাগ্যের তাতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি, বরং নয়া জান্তার অধীনে তাদের উপর নেমে এসেছে আরো ভয়াবহ দুর্যোগ।
সন্তানধারণ ও বিবাহ আইন
মিয়ানমারে এরূপ কোন আইন নেই যে, দু’টি ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না, তবে রোহিঙ্গাদের জন্য এটা ছিলো অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ ও দ-নীয় অপরাধ। কোন পরিস্থিতির কারণে বা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ফলে কোন রোহিঙ্গা যুবক যদি কোন মগ নারীকে বিবাহ করতো তাহলে আইনের কোন না কোন বেড়াজাল তৈরী করে তাকে কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি দেয়া হতো। দৈহিক শাস্তি থেকে শুরু করে, অর্থদ- ও কারাদ- কোন কিছুই বাদ যেতো না। তারপর ঐ সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য রোহিঙ্গা যুবককে বাধ্য করা হতো।
এমনিতে রোহিঙ্গা যুবকদের মধ্যে মগ সম্প্রদায়ে বিবাহ করার কোন প্রবণতা ছিলোও না। হাঁ, বিচ্ছিন্ন একদু’টি ঘটনা ঘটেছে। তবে পুরো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঘটনা ঘটে যখন সামরিক জান্তা আইন জারি করে যে, প্রত্যেক রোহিঙ্গা যুবককে বিবাহের আগে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী অনুমোদন নিতে হবে। অনুমোদনের দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিলো সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকার হাতে। এজন্য ম্যারেজফি নামে বিরাট অঙ্কের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হতো। তারপরো বিবাহের অনুমোদন পাওয়া ছিলো কঠিন, বরং প্রায় অসম্ভব। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ‘সন্তুষ্ট’ করার একটা অলিখিত বিষয় ছিলো, আর সবসময় সেটা ‘অর্থকেন্দ্রিক’ হতো না। ফলে বাধ্য হয়েই রোহিঙ্গা যুবকরা ‘আইন-বহির্ভূত’ বিবাহের আশ্রয় গ্রহণ করতো। তাদের মধ্যে আইনসিদ্ধ বিবাহের হার ছিলো খুবই কম। এজন্য বিভিন্ন উপলক্ষে বিবাহিত রোহিঙ্গা যুবকরা চরম নাজেহাল অবস্থার সম্মুখীন হতো। ফলে তাদের পারিবারিক জীবন হয়ে পড়েছিলো অত্যন্ত দুর্বিষহ।
যারা মুসলিম ধর্মমতে বিবাহ করতো, সরকারী অনুমোদন নেই বলে তারা কখনো সন্তান ধারণ করতে পারতো না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একান্ত অনন্যোপায় হয়েই গোপন গর্ভপাতের আশ্রয় নিতে হতো।
পক্ষান্তরে সরকারী অনুমোদনের জন্য যারা আবেদন করতো তাদের এমর্মে মুচলেকা দিতে হতো যে, তারা দু’য়ের অধিক সন্তান ধারণ করবে না।
শিক্ষা থেকে বঞ্চিত
শুরু থেকেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী প্রধানত কৃষিজীবী। তাই অল্প বয়সেই আপন সন্তানদের তারা কৃষিকাজে নিযুক্ত করে। ফলে পুরো জনগোষ্ঠী, বলা যায় শিক্ষাবিমুখ। তদুপরি যারা অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে চায় তাদের চরম বৈরী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে শুরু থেকেই।
পক্ষান্তরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করার কোন সুযোগই বলতে গেলে তাদের জন্য রাখা হয়নি।
উত্তর আরাকানে, যেখানে রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর বসবাস, সেখানে প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা এমনিতেই হাতে গোণা। তদুপরি দূরবর্তী গ্রামের স্কুলে পড়তে যাওয়ার জন্যও ট্রাভেল পাস সংগ্রহ করা ছিলো বাধ্যতামূলক।
উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন ছিলো অপরিহার্য। আর সে অনুমোদন ছিলো বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতা দ্বারা আবদ্ধ। সেটাও আবার বন্ধ করে দেয়া হয় ২০০১ সালে। তারপরো একটা সুযোগ ছিলো দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে ঘরে বসে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার এবং বিশ^বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয়ার। ২০০৫ সাল থেকে সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়। এভাবেই তৈরী হয়েছে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত একটি নিরক্ষর জনগোষ্ঠী।
শিক্ষার ক্ষেত্রে মিয়ানমার সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি সম্পর্কে যত কিছু বলা হবে তা কমই হবে, কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, রোহিঙ্গানেতৃবৃন্দ, যারা রাজনীতির ময়দানে কিছুটা হলেও সক্রিয় ছিলেন, তারা রোহিঙ্গাদের মধ্যে শিক্ষা-সচেতনতা সৃষ্টি করার তেমন কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেননি, যখন সেটার সুযোগ ছিলো। বেসরকারী উদ্যোগে প্রচুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব ছিলো এবং সেটা তাদের রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রেও অনুকূল হতো। কিন্তু তারা তা করেননি। নির্বাচনের সময় তারা নির্বাচন করেছেন, এমনকি নির্বাচনে জয়ীও হয়েছেন, কিন্তু শিক্ষিত ও সচেতন ভোটার গড়ে তোলার কোন চেষ্টাই তারা করেননি।
সাধারণ শিক্ষার দুয়ার বন্ধ হওয়ার কারণে, তদুপরি ধর্মানুরাগের কারণে মাদরাসা শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিলো রোহিঙ্গাদের মধ্যে। একারণে পুরো উত্তর আরাকান জুড়ে বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য মাদরাসা গড়ে উঠেছিলো। সর্বোচ্চ দাওরা স্তরের মাদরাসাও ছিলো বেশ ক’টি, যেখান থেকে প্রথাগত আলেম তৈরী হতো, যাদের মাধ্যমে কিছুটা হলেও দ্বীনী শিক্ষা ও দ্বীনী চেতনা রোহিঙ্গা সমাজে জাগরূক ছিলো। কিন্তু একসময় মসজিদ-মাদরাসার উপরো নেমে আসে নির্যাতনের খড়গ। বহু আলেম ওলামাকে গোপনে ও প্রকাশ্যে হত্যা করা হয় এবং মসজিদ-মাদরাসা বন্ধ করে দেয়া হয়।
২০১২ সালের দিকে এসে তা চরম আকার ধারণ করে। পুরো আরাকানজুড়ে এখন একটা মসজিদ বা মাদরাসা অক্ষত নেই। এমনো হয়েছে যে, মুছল্লী -ভর্তি মসজিদে এবং ছাত্রভর্তি মাদরাসায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।
আলেমসমাজের হতাশাজনক ভূমিকা
এক্ষেত্রে একটা তিক্ত সত্য আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বিপুল সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকা সত্তেও শুরু থেকেই আরাকানের আলেম- সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করেননি। মাদরাসাগুলোকে কেন্দ্র করে তারা আধুনিক দ্বীনী শিক্ষার বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারতেন। রোহিঙ্গা শিশু-কিশোর ও তরুণ সমাজকে তারা এমনভাবে গড়ে তুলতে পারতেন যাতে আমলে আখলাকে, চিন্তায় চেতনায় এবং সমকালীন যোগ্যতায় তারা জীবন ও সমাজে প্রভাবক শক্তিরূপে ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষার গ-ি অতিক্রম করে নতুন কোন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা তারা চিন্তাও করেননি।
কতটা বেদনাদায়ক বিষয় ছিলো যে, আরাকানের মাটিতে বসে তারা উর্দুকে গ্রহণ করেছিলেন শিক্ষার মাধ্যমরূপে। না ইংরেজী ভাষা শেখানোর প্রয়োজন বোধ করেছেন, না স্থানীয় বর্মিজভাষা, আর না আধুনিক বিষয়সমূহ। এভাবে তথাকথিত দ্বীনী শিক্ষার নামে গড়ে উঠেছে বিশাল একটি শ্রেণী যারা সমাজ থেকে ছিলো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ফলে বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগের সময় প্রয়োজনীয় কোন অবদানই তারা রাখতে পারেনি।
যে কোন জাতির মধ্যে এ অংশটি যখন এরূপ অথর্ব হয়ে পড়ে তখন চরম পরিণতিই হয়ে থাকে ঐ জাতির ভাগ্যলিপি।
রোহিঙ্গাজাতির নতুন দুর্ভাগ্য অং সান সু চি
মিয়ানমারের রাজনীতির আকাশে অং সান সু চির ভাগ্যতারকা উদিত হতে শুরু করে ১৯৮৮ সালের দিকে। সভ্যপৃথিবী তখন তাকে গণতন্ত্রের মানসকন্যা এবং মানবাধিকারের আপোশহীন নেত্রীরূপে বরণ করে নেয়। আরাকানের মজলুম রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীও অন্ধকার দিগন্তে যেন বেঁচে থাকার মত একটুখানি আশার আলো দেখতে পায়। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে তারা দলে দলে সু চির সমর্থনে সমবেত হতে থাকে। কিন্তু ...
দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যরূপৈ উপমহাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির সাধারণ ধারা কোন না কোন পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, যাকে এককথায় বলা যায় ‘পরিবারতন্ত্র’। হয়ত পরিবার আলাদা, পাত্রপাত্রী ভিন্ন, কিন্তু বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। ভারতে আমরা যেমন দেখতে পাই নেহরুপরিবার, তেমনি বাংলাদেশে দেখতে পাই মুজিবপরিবার ও জিয়াপরিবার, পাকিস্তানে ভুট্টোপরিবার... একসময়ের বৃটিশভারতের প্রদেশরূপে গণ্য বার্মার ইতিহাসও তা থেকে ভিন্ন নয়। সেখানেও পুরো রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে অং সান পরিবারকে কেন্দ্র করে। তবে কিছুটা পার্থক্য এই যে, বার্মায় স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা সামরিক-বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
অং সান সূ চী ও নতুন দুর্ভাগ্য
যেহেতু জাতিগতভাবে নির্যাতিত রোহিঙ্গাজনগোষ্ঠীর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যেমন জড়িয়ে আছে সামরিক জান্তা ও শাসকদের নাম তেমনি জড়িয়ে আছে অং সান সুচিরও কলঙ্কিত নাম, তাই এখানে তার সম্পর্কেও সংক্ষেপে কিছু বলা সঙ্গত মনে হয়।
আধুনিক মিয়ানমার ও সাবেক বার্মার ‘জাতির জনক’রূপে পরিচিত অং সান সম্পর্কে আগেই আলোচনা হয়েছে। তারই কন্যা হলেন অং সান সু চি, সারা বিশে^ একসময় যার পরিচয় ছিলো গণতন্ত্রের আপোশহীন লড়াকু নেত্রীরূপে।
১৯৪৭ সালের ১৯শে জুলাই বার্মার (পরবতীকালে যা মিয়ানমাররূপে পরিচিত) স্বাধীনতাচুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র ছয়মাস আগে অং সান যখন তার রাজনৈতি সহকর্মী ও বন্ধু উ (আব্দুর)রাজ্জাকসহ আততায়ীর গুলিতে নিহত হন তখন সু চির বয়স মাত্র দু’বছর।
অং সান এর স্ত্রী খিন কুই প্রথম দিকে বার্মা সরকারে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেন। ১৯৬০ সালে তিনি ভারত ও নেপালে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব লাভ করেন। সেই সুবাদে সু চির লেখাপড়া ও বেড়ে ওঠাও সেখানে হচ্ছিলো। পরে তিনি উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ^বিদ্যালয়ে পাড়ি জমান। (চলবে ইনশাআল্লাহ্)