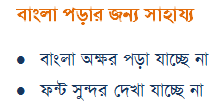সঙ্কোচের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, আবারো আপনাকে ‘সম্ভব’ ও ‘ধারণা’ শব্দদু’টির মুখোমুখি হতে হবে। তদুপরি ‘ধারণা’র সঙ্গে আপনাকে যেতে কিছু দূর, আর সম্ভবত’র সঙ্গে যেতে হবে বহুদূর! বস্তুত যে ইতিহাস নিয়ে আলাদা আলাদা বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর এত গর্ব ও গৌরব, আবার সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতার এত অহঙ্কার তার পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে এই ধারণা ও সম্ভাবনা শব্দদু’টির উপর ভর করে। বুনিয়াদ ও ভিত্তি যদি কিছু থেকে থাকে তা আছে ইসলামের ইতিহাসের। শুধু কনিষ্ঠতার সুবাদে নয়, এ জাতি প্রধাণত ধর্মীয় প্রয়োজনে শুরু থেকেই ইতিহাসের প্রতি উচ্চমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। হাদীছের শাস্ত্রে সনদের যে বিশাল সৌধ, তা গড়েই উঠেছে প্রায় পাঁচলাখ মানুষের জীবন ও জীবনী চর্চার উপর, যার নাম আসমাউর রিজাল। আচ্ছা, ভূমিকা রেখে চলুন মূল আলোচনায়।
যে কোন জাতি, জনগোষ্ঠী ও জনপদের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে শুরুতে যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তার মধ্যে একটি হলো, ঐ জনপদের গোড়াপত্তন হয়েছে কখন থেকে? ঐ জনগোষ্ঠীর আদিপরিচয় কী? কাশ্মীরের মত ঐতিহ্যবাহী জনপদ ও জনগোষ্ঠী এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় হলো, আরো কম ঐতিহ্যের জনপদ ও জনগোষ্ঠীর বিপরীতে কাশ্মীর নামের জনপদ এবং কাশ্মীরী জনগোষ্ঠীর আদি ইতিহাস বলতে গেলে কিছুই জানা নেই। ভূখণ্ডের উৎপত্তি সম্পর্কে তো যাকিছু ‘তথ্য’ পাওয়া যায় ‘ইতিহাসের পাতায়’ তা পিছনে পরিবেশন করা হয়েছে। এবার জনপদ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কে।কাশ্মীরের বিষয়ে তথ্যভিত্তিক ইতিহাস চর্চা করতে যারা পছন্দ করেন, যেমন অধ্যাপক মুহম্মদ শফী, তার মতে (এবং আগে ও পরে আরো অনেকের মতে) কাশ্মীর ভূখণ্ডে মানববসতি শুরু হয়েছে খৃস্টপূর্ব ৩০০ (তিনহাজার) বছর পূর্বে। তাহলে এই ত্যথকে সঠিক ধরে নিয়ে কী সিদ্ধান্তে আসা যায়? কাশ্মীর উপত্যকায় মানববসতির বয়স প্রায় পাঁচহাজার বছর। সম্ভবত হযরত নূহ আ.র সময়ে যে, মহাপ্লাবন ঘটেছিলো, যার বয়ান কোরআনে, তার আগে তাওরাতে এসেছে, এমনকি হিন্দু পুরাণ ও মহাভারতেও যার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিছুটা রূপকথার মত করে, সম্ভবত ঐ মহাপ্লাবনের কয়েক শতাব্দী পরের ঘটনা। প্রত্নতত্ত্ববিশারদদের মতে, প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের ভিত্তিতে মানবজাতির ইতিহাসকে যে কয়টি ভাগে উল্লেখ করা হয় তার সবক’টির নিদর্শন কাশ্মীর উপত্যায় পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ করে কাশ্মীরের ইতিহাসবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি পারভেজ দীওয়ান এ বিষয়ে জোরালো আলোচনা করেছেন তার সুবিখ্যাত A History of Kashmir বইয়ে, একই নামে যার বাংলা তরজমা পাওয়া যায়। কাশ্মীরের আদি বাসিন্দা বা ভূমিপুত্র বলতে যাদের বোঝায়, ঐতিহাসিকগণ তাদের মোটামুটি তিনটি ভাগ করেছেন, নাগ, পিশাচ ও ইয়াক্ষা।অনেকের যুক্তিভিত্তিক প্রবল ধারণা যে, শুরুতে আদী বাসিন্দাদের অভিন্ন নাম ছিলো ‘কাশ’।
তাদের যুক্তি হলো, হযরত নূহ আ. এর পুত্রদের একজনের নাম ছিলো হাম। হামের একপুত্র হলেন কাশ, যার নামে বিশাল একজনগোষ্ঠী বিস্তার লাভ করে মধ্য এশিয়া ও তার আশেপাশের অঞ্চলে। বিভিন্ন স্থানের নামের মধ্যে এই উপজাতির নামের ছাপ রয়েছে। যেমন, মধ্যএশিয়ায় বুখারার একটি গ্রামের নাম ‘কাশ’, মারও এলাকার একটি গ্রামের নাম কাশমোহরা, সমরখন্দেও রয়েছে এ নামের একাধিক এলাকা। আর চীন-অধিকৃত তুর্কিস্তানের কাশগর শহরের খ্যাতি তো দুনিয়াজোড়া। আফগানিস্তানেও পাওয়া যায় কাশকার ও কাশহিল নামের এলাকা। সম্ভত এখান থেকে কাশ জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য একটা অংশ আরো দক্ষিণে হিন্দুকুশ অতিক্রম করে বিভিন্ন স্থানে বসতি গড়ে তোলে। সেখানেও পাওয়া ‘কাশ’শব্দযুক্ত বিভিন্ন স্থানের নাম। তো কাশজনগোষ্ঠীর একটা অংশ কাশ্মীর উপত্যকায় এসে জমে বসে যায় এবং তাদেরই নামে পুরো উপত্যকার নাম হয়ে যায় কাশ্মীর। ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যহীরুদ্দীন মুহম্মদ বাবরও এই মত প্রকাশ করেছেন।
কাশ্মীর উপত্যকায় মানববসতির গোড়াপত্তন এবং উপত্যকার নামকরণ সম্পর্কে যত মত প্রচলিত আছে, তার মধ্যে এটাই হলো সবচে’ উপযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত। এখানে আমরা হিন্দু ইতিহাসের নমুনা হিসাবে একটা দু’টো মত তুলে ধরতে চাই। হিন্দু ঐতিহাসিকগণ বেশ আত্মশ্লাঘার সঙ্গে লিখেছেন, আর্যরা ভারতীয় উপমহাদেশে আসার পর, যখন কাশ্মীর উপত্যকার দিকে অভিযাত্রা করলো তখন আদি বাসিন্দাদের একটি অংশ বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করে এবং হিংস্রতাপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তাই তাদের কারো নাম হলো নাগ (সাপ), কারো নাম হলো পিশাচ (অপ-আত্মা)। আর্য ঐতিহাসিকদের মতে, কাশ্মীরের আদিবাসীরা আর্যদের হাতে সম্পূর্ণ নিমূল হয়ে গিয়েছিলো, তখন আর্যরা পরিচিতি পায় উচ্চ জাতি (ব্রাহ্মণ পণ্ডিত) হিসাবে। ভালো কথা, তবে প্রশ্ন হলো, কাশ্মীরের পণ্ডিত সমাজ তো মুষ্টিমেয়। নিম্নবর্ণের এই বিশাল জনগোষ্ঠী তাহলে এলো কোত্থেকে! ব্যাখ্যার তো অভাব নেই! বলা হলো, নিম্নবর্ণের লোকেরাও মূলত উচ্চবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সামাজিক অনাচারের কারণে কিছু মানুষ একঘরে ও সমাজচ্যুত, এমনকি বর্ণচ্যুত হয়েছে। এভাবে আর্যদের থেকে অচ্ছুত সমাজের বিস্তার ঘটেছে। বড়িয়া বাত! তাহলে তো বলতে হয়, মূলের চেয়ে শাখার বিস্তারই বেশী ঘটেছে। আর্য ঐতিহাসিক -দের এ বক্তব্যের আড়ালের উদ্দেশ্য তো পরিষ্কার! কিন্তু নিরপেক্ষ ও নির্মোহ ঐতিহাসিক যারা, তাদের দৃঢ় মত এই যে, কাশ্মীরের পণ্ডিতসমাজই শুধু আর্যভুক্ত, বাকি বিশাল জনগোষ্ঠী আসলে কাশ্মীরের আদি বাসিন্দাদের উত্তরপুরুষ।
ইতিহাসের বিভিন্নমুখী বক্তব্য থেকে যে সত্যটি সবার অজান্তে বেরিয়ে এসেছে তা এই যে, কাশ্মীরের বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে মূলত ‘আর্য-আদি’ সঙ্ঘাত থেকে, যা শুধু যুগের পর যুগ চলেছে, তাই নয়, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী অব্যাহত ছিলো। কখনো তা হানাহানি পর্যন্ত ছিলো, কখনো খুনাখুনি পর্যন্ত গড়িয়েছে।এটাও সত্য যে, বহিরাগত দাম্ভিক আর্যরা আদিবাসীদের পক্ষ হতে ভয়ঙ্কর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, যা আর্যদের পক্ষ হতে তাদের নাগ ও পিশাচ নামকরণ থেকেই আন্দায করা যায়। সবসময় যে আর্যরা জয়ী হয়েছে, আর আদিবাসীরা পরাজিত, ঘটনা এমন নয়, যদিও আর্য ঐতিহাসিক -দের ঝোঁকটা দেখা যায় সেদিকেই। প্রকৃত সত্য এই যে, সাহসে, শৌর্যবীর্যে আদিবাসীরা ছিলো অনেক এগিয়ে। তাছাড়া তাদের নৈতিক শক্তি ছিলো এই যে, তারা হলো ভূমিপুত্র, কাশ্মীর তাদের; আর্যদের নয়। আর্যরা বাইরে থেকে আসা হানাদার, আদিবাসিরা মাটি ও মানুষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। তাদের লড়াই ছিলো অস্তিত্বরক্ষার লড়াই, গর্ব ও গৌরবের লড়াই। ‘কাশ্মীর হামারা হ্যায়’ এটা কিন্তু শুধু হিন্দুত্ববাদী দখলদার ভারতের বিরুদ্ধে কাশ্মীরীদের আজকের শ্লোগান নয়। আর্য-আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও একই শ্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। আর্যদের ধূর্ততা ও চাতুর্যের কাছে হয়ত সেদিন কাশ্মীরীদের প্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছিলো, তবে ঐ গোড়া থেকেই প্রজন্ম-পরম্পরায় দেশপ্রেমের জীয়নকাঠি তারা ধারণ করে এসেছে। তাই দশ লাখ ভারতীয় যোদ্ধা আজ পর্যুদস্ত কাশ্মীরী প্রতিরোধের সামনে।
তো বলছিলাম, কাশ্মীর উপত্যকার আদিবাসীদের শক্তি ছিলো আত্মিক ও নৈতিক, পক্ষান্তরে আর্যদের শক্তি ছিলো রক্তের আভিজাত্যের মিথ্যা দম্ভ, আর অপেক্ষাকৃত উন্নত জ্ঞান। সমর- শক্তিতে আর্যরা যথেষ্ট অগ্রসর ছিলো, সন্দেহ নেই। তবে যুদ্ধের ইতিহাস যখন থেকে শুরু তখন থেকেই এ সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে, হাতের অস্ত্র তখনই কাজ করে মনে যখন মনোবল থাকে। তাছাড়া আদিবাসীরা একেবারে নিরস্ত্র অবশ্যই ছিলো না। হাঁ, যে জাগয়গায় আদিবাসীরা বরাবর মার খেয়েছে এবং পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছে সেটা হলো আর্যদের চতুরতা ও ধূর্ততা। অথচ কাশ্মীরের ভূমিপুত্ররা ছিলো সহজ সরল এবং অল্পতেই বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত। এ ধারা আজো আমরা দেখতে পাই, কাশ্মীরের পণ্ডিত সমাজ এবং যারা কাশ্মীরের ভূমিপুত্র তাদের মধ্যে। একদিকে সরল বিশ্বাস, অন্যদিকে গরল আর গরল। প্রতীকরূপে আমরা বলতে পারি, একদিকে পণ্ডিত নেহরু, অন্যদিকে বেচারা শেখ আব্দুল্লাহ্! আরো পরে যদি বলি, একদিকে কংগ্রেস, বিজেপী; অন্যদিকে ওমর আব্দুল্লাহ্ ও মুফতী মেহবূবা।
আর্যদের কথা যদি বাদ দেই। বিভিন্ন সময় কাশ্মীরে বিভিন্ন সূত্রে মানুষ এসেছে, তবে ঘৃণা ও অহঙ্কার নিয়ে নয়, বরং ভালোসা দিতে এবং ভালোবাসা নিতে। তারা কিন্তু সহজেই কাশ্মীরের আদিবাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এর একটা বড় কারণ ছিলো, এশিয়ার পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে হাজার মাইল দীর্ঘ রেশমিপথ নামে পরিচিত যে কোলাহলপূর্ণ বাণিজ্যিক পথ ছিলো, তার সঙ্গে কাশ্মীর গভীরভাবে যুক্ত ছিলো। ফলে মশলা ও ঘোড়া-চামড়া এবং লবণের আমদানি-রপ্তানি যেমন হয়েছে তেমনি হয়েছে জ্ঞান ও দর্শন এবং প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার লেনদেন। একই ভাবে আগমন ঘটেছে বিভিন্ন ধর্ম ও র্সস্কৃতির। সুতরাং অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে বলা যায়, কাশ্মীর ছিলো বহুসভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলনমোহনা। তবে চীন ও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির তুলনায় মধ্যএশিয়া ও পারস্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ছিলো অনেক বেশী। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞানী-গুণী ও সাধকদের কাশ্মীর উপত্যকায় আসার এবং এসে স্থায়ী হয়ে যাওয়ার পিছনে সবচে’ বড় অনুঘটকরূপে যে জিনিসটি কাজ করেছে তা হলো কাশ্মীরের জ্ঞানবান্ধব ও সধনার অনুকূল ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত পরিবেশ। পাহাড়বেষ্টি উপত্যকা বাইরের সমস্ত কোলাহোল থেকে মুক্ত, যাতে রয়েছে অপার্থিব এক ভাবগম্ভীরতা, যা মানুষকে ঊর্ধ্ব-জাগতিক রহস্যাবলী সম্পর্কে ধ্যানমগ্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন আপনা থেকেই সত্য ও মহাসত্য আত্মার দিগন্তে উন্মোচিত হতে থাকে। পুরো উপত্যকা যেন বহু বর্ণের, বহু সুবাসের ফুল দিয়ে সাজানো একটা ‘গুলদাস্তা’, সেই সঙ্গে অসংখ্য ঝর্ণার সঙ্গীতমুখরতা এবং জলবায়ুর স্নিগ্ধতা, এসবই যে কোন জ্ঞানসাধকের কাছে মনে হবে আদর্শ স্থান।
এছাড়া কাশ্মীর উপত্যকার আকাশে, বাতাসে, মাটিতে, পানিতে এবং মানুষের মাঝে রয়েছে এমন কিছু অপার্থিব সৌন্দর্য, বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা যার ‘স্বর্গীয় স্পর্শ জ্ঞানসাধক বলো, আর বলো ধ্যানসাধক, সবাইকে হৃদয় ও আত্মার জগতে বিশুদ্ধতা অর্জনের আকুতি সৃষ্টি করে। এ বর্ণনার ভাষা ও বিন্যাস হয়ত আমার, কিন্তু এ অনুভূতির কথা বলেছেন এবং লিখেছেন কাশ্মীরের উপত্যকায় যারাই এসেছেন পরম সত্যের সন্ধানে, বা জ্ঞানের সাধনার উদ্দেশ্যে। ফলে শুরু থেকেই কাশ্মীর উপত্যকা ছিলো ‘সাধু ও সাধকদের পীঠস্থান। কাশ্মীরের ‘ভূস্বর্গ’ থেকেই বহু জ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে, বিশেষ করে আধ্যত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে।
খৃস্টের জন্মের বহু-শতাব্দী আগে থেকে পাঞ্জাবের তক্ষশীলা ছিলো জ্ঞানের বিদ্যাপীঠ। গবেষকগণ একমত যে, তক্ষশীলার উপর কাশ্মীরী জ্ঞানের যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। এখান থেকেও জ্ঞানী-গুণীরা ওখানে গিয়েছেন, আবার ওখান থেকেও এসেছেন এখানে। সাংস্কৃতিক বিনিময়ও ঘটেছে ভারত এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন জনপদের সঙ্গে কাশ্মীরী জনপদের।
***
সভ্যতার অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গত কারণেই যুক্ত হয় শাসন, আর শাসনের অনিবার্য উপসর্গ হলো শোষণ। পক্ষান্তরে কখনো কখনো কারো কারো ক্ষেত্রে যুক্ত হতে দেখা যায় ন্যায়পরতা ও সুশাসন। বিশ্বের জাতিবর্গের ইতিহাসে এটা যেমন সত্য, কাশ্মীরউপত্যকার ক্ষেত্রেও তা সমান সত্য। কাশ্মীরউপত্যকার শাসনযুগের ইতিহাসের শুরুটা অবশ্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। গবেষকগণ এতটুকু বলতে পেরেছেন মোটামুটি নিশ্চয়তার সঙ্গে যে, পাণ্ডু রাজবংশ খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত কাশ্মীর শাসন করেছে বেশ প্রতাপের সঙ্গে। তারপর মৌর্য রাজবংশ তিন শতাব্দীর কাছাকাছি সময় কাশ্মীর শাসন করে। এভাবে চলতে চলতে ১১০১ সালে শুরু হয় লেহারা রাজবংশের শাসন, যা স্থায়ী হয় ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত। তারপর কাশ্মীরউপত্যকার শাসন -ইতিহাসের ঘটে মোড়পরিবর্তন। শুরু হয় মুসলিম যুগ। সুলতান আমল দিয়ে যার শুরু এবং চাক, মোঘল ও আফগানদের মাধ্যমে যার সমাপ্তি। সমগ্র মুুসলিম শাসনের বিস্তৃতিকাল হচ্ছে আঠারোশ উনিশ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ বছর। মুসলিম শাসনের বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিলো নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার উদীয়মান নতুন দাবীদারদের সম্পর্কে উদাসীনতা এবং প্রজাশাসনের ক্ষেত্রে কোন কোন শাসকের চরম স্বেচ্ছাচার।এভাবেই ক্ষমতা চলে যায় পাঞ্জাব -কেন্দ্রিক শিখশক্তির হাতে। শিখশাসন খুব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। ১৮১৯ থেকে ছেচল্লিশ সাল পর্যন্ত মাত্র চব্বিশ পঁচিশ বছর। তারপর গোড়াপত্তন হয় ডোগরা শাসনের যার স্থায়িত্ব -কাল হলো ১৮৪৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।ভারতভাগের মাধ্যমে কাশ্মীর- উপত্যকাও ভাগ হয়ে যায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। জাতিসঙ্ঘের একটি সিদ্ধান্ত এখনো ঝুলে আছে ভারতের হিন্দু শাসকদের অন্যায় দম্ভের কারণে; ‘কাশ্মীরীদের গণভোট’। এসম্পর্কে যথাসময় কথা হবে আশা করি।কাশ্মীরউপত্যকায় ধর্মের উন্মেষ ও বিকাশ এবং ধর্মের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সঙ্ঘাত যদি আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে, আর্যদের মাধ্যমে সেখানে হিন্দুধর্মের, আরো সুনির্দিষ্টভাবে ব্রাহ্মণবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং ধীরে ধীরে তা সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে, যদিও ওখানকার ভূমিপুত্রদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসও অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলো।
বস্তুত কাশ্মীরের বর্তমান যে পণ্ডিত-সমাজ, তারা ভালো-মন্দ স্বভাব ও প্রকৃতিসহ গোড়ার দিকের সেই ব্রাহ্মণবাদেরই প্রতিনিধি। পরে সম্রাট অশোকের আমলে কাশ্মীর উপত্যকায় বৌদ্ধধর্মের আগমন ঘটে। শুরুতে কিছুটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেও, অল্পসময়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে, এমনকি একসময় তা হিন্দু ব্রাহ্মণবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। মৌর্য রাজবংশের শ্রেষ্ট সম্রাট ধরা হয় মহামতি অশোককে। তার সময় ২৫০ খৃস্টপূর্বাব্দে পাটলী-পুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যার সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্ত। মূলত তারই তত্ত্বাবধানে ‘মধ্যান্তিকা’ নামের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে কাশ্মীর ও গ্যান্ধারায় পাঠানো হয় বৌদ্ধধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে।উল্লেখ্য, মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় থেকে মুসলিম শাসনের পূর্ব পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময়কাল তাতে ব্রাহ্মণদের শিবধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তর্কযুদ্ধ যেমন হয়েছে তেমনি হয়েছে রক্তযুদ্ধ। উভয় ধর্মের উত্থানপতনের ক্ষেত্রে শাসকদের পরিবর্তন ও ক্ষমতার পালাবদলের বিশেষ ভূমিকা অবশ্যই ছিলো।
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হানবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম চরম প্রতিকূলতা ও বৈরী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, পক্ষান্তরে সেটা ছিলো শিবধর্মের নব-উত্থান কাল। হানশাসক মিহিরাকুলা অজ্ঞাত কারণে ছিলেন বৌদ্ধধর্মের উপর খড়গহস্ত। তিনি বৌদ্ধধর্মকে নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। বলা যায়, এক্ষেত্রে তিনি অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন। ব্যপক বৌদ্ধহত্যার কারণে তাকে কশাই বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের পক্ষ হতে। পক্ষান্তরে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের কাছে আজো তিনি মহান হিরিকুলা! ইতিহাসের চেহারা-চরিত্র বোঝা সত্যি কঠিন। কোনটি যে ইতিহাসে মুখ, আর কোনটা যে মুখোশ, সনাক্ত করা খবু সহজ নয়। তাই তো ভারতের ইতিহাসে আমরা বাদশাহ আকবরের দু’রকম চেহারা দেখতে পাই। একই অবস্থা আওরঙ্গযেব-কে নিয়ে। মুসলিম ইতিহাসে তিনি হলেন আদর্শ শাসক, দরবেশ বাদশাহ, অথচ হিন্দু ইতিহাস!
সে যাক, কথা হচ্ছিলো হানরাজা মিহিরাকুলার আমলে বৌদ্ধধর্মের মহাবিপর্যয় সম্পর্কে।মিহিরকুলার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন মেঘবান। তিনি অজ্ঞাত কারণে ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল। এমনকি বলা হয়, তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তা পালনও করতেন নিষ্ঠর সঙ্গে। সিংহাসনে বসার পর তার প্রথম কাজ ছিলো রাজফরমানের মাধ্যমে সর্বপ্রকার জীবহত্যা নিষিদ্ধ করা। এরপর আবার নেমে আসে বৌদ্ধ-ধর্মের উপর মহাবিপর্যয়। ৯৫০ থেকে ৯৫৮ এই সংক্ষিপ্ত সময়কালের রাজা কিশমাগুপ্ত বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের উপর চরম নির্যাতন চালান এবং বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেন। নতুন কোন বৌদ্ধবিহার তৈরীর অনুমতি দেয়া দূরের কথা, পুরোনো অনেক বৌদ্ধবিহার তিনি ধ্বংস করেছেন।
কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ যদি নির্ধারণ করতে হয়, তাহলে সেটা হলো কুশান রাজবংশের শাসনকাল, এমনকি রাজা কানুশকা নিজেও একসময় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময় কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাশ্মীরউপত্যকায় বৌদ্ধধর্মের বিশেষ উত্থানে বিরাট ভূমিকা ছিলো চতুর্থ বৌদ্ধসম্মেলনের। সম্মেল উপলক্ষে সেখানে ভারত, মধ্যএশিয়া, তিব্বত ও চীন থেকে প্রায় দেড়হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুগণ কাশ্মীর উপত্যকায় সমবেত হন। পুরো সম্মেলনটি রাজপৃষ্ঠ-পোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের পর থেকেই বিশেষ করে ভারত ও তিব্বত থেকে বৌদ্ধদের আগমন বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এরই ধারাবাহিক-তায় দক্ষিণ ভারতের প্রস্দ্ধি বৌদ্ধ দার্শনিক নাগর্জুনা কাশ্মীর উপত্যকায় আগমন করেন। কথিত আছে, কাশ্মীরের ব্রাহ্মণসমাজ, যারা শিবপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন, নাগর্জুনার কাছে ধর্মতর্কে পরাজিত হন, যার ব্যাপক প্রভাব পড়ে উপত্যকার ধর্মবিপ্লবে। তখনই হিন্দুধর্ম, তথা শিববাদ, তথা ব্রাহ্মণবাদ বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক উত্থানের সামনে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজ।
বিভিন্ন শাসকের আমলে কঠিন সময় পার করলেও একটা বিষয়ে তারা বৌদ্ধধর্মের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে জয়ী হন। শুরুতে বৌদ্ধধর্মে মূর্তির স্থান ছিলো না। ধ্যানই ছিলো তাদের প্রধান ধর্ম। কারণ স্বয়ং বুদ্ধ শুধু ধ্যান করেছেন, তিনি কোন মূর্তি নির্মাণ করেননি, না নিজের, না অন্যকোন উপাস্যের। বিভিন্ন যুক্তি ও দার্শনিক তত্ত্ব দ্বারা কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ সুকৌশলে বৌদ্ধদের মাঝে এ বিশ্বাস প্রচার করেন যে, বুদ্ধ মূলত বিষ্ণুরই দ্বিতীয় রূপ! শত্রু-ধর্মের লোকদের প্রচারণায় অন্য ধর্মের বিশ্বাসে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাওয়া ধর্মের ইতিহাসে সত্যি বড় আশ্চর্যের বিষয়! এর বড় উদাহরণ অবশ্য একত্ববাদে বিশ্বাসী খৃস্টধর্মে সাধু পোলের প্রচারিত ত্রিত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি খৃস্ট ধর্মের অনুসারী বলেই পরিচিত ছিলেন। যাহোক, বৌদ্ধধর্মে যারা নতুন দীক্ষা গ্রহন করতো, বিশেষভাবে তারা এই নতুন দর্শনে অনুরক্ত হয়ে পড়ে। মূলত তাদেরই মাধ্যমে বিষ্ণুপূজার মত বুদ্ধের মূর্তির পূজা শুরু হয়।
প্রবীণ বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা নবীনদের যথা-সাধ্য বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, এটা ধর্ম থেকে বিরাট বিচ্যুতি! কিন্তু চিরন্তন বাস্তবতা এই যে, সত্য বা মিথ্যা, তরুণরা যখন যেটা গ্রহণ করেছে সেটারই জয় হয়েছে, প্রবীণদের বাধা কখনোই ফলপ্রসূ হয়নি। এক্ষেত্রে উপায় হলো শৈশব থেকে শিশুদের নিজ নিজ আদর্শের উপর গড়ে তোলা চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাওয়া।
***
কাশ্মীরের উপত্যকায় হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের যে মর্মন্তুদ ইতিহাস সেটা ছিলো মূলত উভয় পক্ষের তথাকথিত সুশীল সমাজের বিষয়, উপত্যকার তৃণমূল পর্যায়ে মানুষ এ কারণে শুধু ভোগান্তির শিকার হয়েছে। তাই সাধারণ মানুষ দুর্বল হলেও তাদের মধ্যে উভয়ধর্মের উপরই একটা ক্ষোভ তৈরী হয়েছিলো। কিন্তু অভাব-অনাহার এবং চরম দারিদ্র্যের শিকার এই সাধারণ মানুষের মুখে ভাষা ছিলো না, তাই কোন প্রতিবাদও ছিলো না। সমস্ত অনাচার তারা, যাকে বলে মুখবুজে সহ্য করা, তাই করে যাচ্ছিলো। অর্থাৎ আদর্শমুখী, ন্যায়, সত্য ও সুন্দর নতুন কোন চিন্তা বা ধর্মমতের জন্য কাশ্মীর উপত্যকা পূর্ণ প্রস্তুত ছিলো, বরং বলা যায়, কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নিপীড়নের মুখে নতুন কোন ন্যায়ধর্মের প্রতি উন্মুখ ছিলো। পরিস্থিতির এমনই প্রেক্ষপটে যমীনের উপর আল্লাহর বিশেষ দানরূপে কাশ্মীরের উপত্যকায় ইসলামের শুভপ্রবেশ সম্পন্ন হয়। নির্যাতিত, নিপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত কাশ্মীরের অসহায় মানুষ যেন তাদের পিপাসার পানি পেয়ে যায়।
কাশ্মীরের মানুষ এই প্রথম জানলো এবং জেনে অবাক হলো যে, পৃথিবীতে এমনো ধর্ম আছে, যার শিক্ষার মধ্যে মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য নেই, উঁচু-নীচু নেই এবং সাদা-কালো নেই। স্রষ্টা চোখে সব মানুষ সমান। যার নেকি ও পুণ্য বেশী, স্রষ্টার কাছে তার মর্যাদা তত বেশী। এমনো ধর্মের অনুসারী আছে যারা মানুষ নন, দেবতা, অথচ তারা বলেন, আমরা তোমাদেরই মত সাধারণ মানুষ। বহু জনপদের মত কাশ্মীরেও ইসলামের আগমন কোন রাজ-শক্তির মাধ্যমে ঘটেনি। কোন শাসকের তলোয়ার এর প্রচার-প্রসারের পক্ষে কাজ করেনি। মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, স্বঃতস্ফ‚র্তভাবে, ইসলামের শিক্ষার সৌন্দর্যে এবং মুসলিমের আখলাক ও চরিত্রের পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে। এর আগে যুগ যুগ ধরে তারা দেখেছে, ধর্মমানেই হলো শাসকের শোষণের হাতিয়ার। ধর্ম মানেই হলো মানুষের উঁচু নীচু বর্ণভেদের অভিশাপ। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কথায় যদিও কিছু পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে যাদের হাতে ধর্মের ক্ষমতা তাদের শোষণচরিত্র উভয় ধর্মে অভিন্ন। পক্ষান্তরে যে নতুন ধর্মের সঙ্গে তাদের মাত্র পরিচয়, তার সঙ্গে না শাসকের সম্পর্ক, না শোষনের। শাসক যদি শোষণ করে, যুলুম নিপীড়ন করে সেটা তার নিজের স্খলন, ধর্ম থেকে তার বিচ্যুতি। শাসকের শোষন ও যুলুমের পক্ষে ইসলামের কোন সমর্থন নেই। অথচ এর আগে তারা দেখেছে ধর্ম মানেই হলো শোষণের হাতিয়ার!
কাশ্মীরউপত্যকার সৌভাগ্য যে, ইসলামের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছে এমন এক মহাপুরুষের মাধ্যমে, আচরণে উচ্চারণে এবং চিন্তায় চরিত্রে যিনি ছিলেন পূর্ণ মুসলিম, যেন ইসলামের জীবন্ত ছবি! কাশ্মীরের ইতিহাসে সৌভাগ্যের মূর্ত প্রতীক যে মহামানবের আগমন, তিনি হলেন হযরত বিলাল শাহ! উপত্যকার সাধারণ মানুষের মাঝে যার পরিচয় ছিলো ‘বুলবুল শাহ’ নামে। ক্রমে তাঁর আসল নাম ‘বিলাল’ সাধারণ মানুষের দেয়া এই নতুন নামের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। সাধারণ মানুষ কেন তাকে বুলবুল শাহ বলে ডাকতে শুরু করলো? জানা যায়, এর কারণ হলো, তাঁর একটি পোষা বুলবুল ছিলো। তিনি যেখানেই যেতেন পোষা বলবুলটি তাঁর কাঁধে বসে থাকতো। এ দৃশ্যটি সাধারণ মানুষকে এমনই মুগ্ধ করে যে, তারা তাঁকে বুলবুল শাহ বলেই ডাকতে থাকে আদর করে, সম্মান করে। ইতিহাসের বিবরণ হলো, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মপুরুষদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিলো চরিত্রে এবং মানুষের সঙ্গে আচরণে। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে, সমগ্র সত্তা থেকে এমনই স্বর্গীয় জ্যোতির প্রকাশ ঘটতো যে, দেখামাত্র মানুষ শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়তো। তাঁকে কিছু বলতে হতো না, নিজের ধর্ম তাঁকে কথার সাহায্যে প্রচার করতে হতো না; মানুষ নিজেই বিশ্বাস করে নিতো। এমন মহামানবের ধর্ম অবশ্যই সত্য। যদি বলা হয়, তিনি ছিলেন কাশ্মীরের খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি, তাহলে মোটেই ভুল হবে না।
হযরত বুলবুল শাহকে কেন্দ্র করে কাশ্মীর উপত্যকায় অত্যন্ত নীরবে যে বিপ্লবটি ঘটো যায় তা হলো, কাশ্মীরের বৌদ্ধ শাসক ‘রিনচনা’ সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করেন। আগে থেকেই মানুষ হযরত বুলবুল শাহের হাতে ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করছিলো। উপত্যকার শাসকের ইসলাম গ্রহণ করার ফল এই হলো যে, বিশিষ্ট-সাধারণ সবার মাঝে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন গতি সৃষ্টি হলো। মানুষ এখন একজন দু’জন করে নয়, দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। তদুপরি এখন শুধু সাধারণ মানুষ নয়, উপত্যকার বিশিষ্ট লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। মূল আলোচনা এগিয়ে নেয়ার আগে এখানে রাজা রিনচনার কিছুটা পরিচয় তুলে ধরা যায়। তিনি উপত্যকার মূল অধিবাসী ছিলেন না, ছিলেন বহিরাগত। তিনি কাশ্মীরের শাসক হন ঘটনা প্রবাহের অনিবার্য পরিণতিরূপে।
(চলবে ইনশাআল্লাহ্)