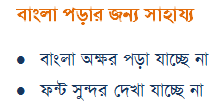ইউরোপে স্বদেশবাদ ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ
পিছনে আমরা বলে এসেছি যে, উগ্র স্বদেশবাদ ও জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা ও ভৌগলিকতা ছিলো প্রজন্মপরম্পরায় ইউরোপীয় স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বরং এটা ইউরোপের প্রাণসত্তায় এবং রক্তমাংসে মিশে গিয়েছিলো, যা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ইউরোপ কল্পনাও করতে পারে না। তবে ইউরোপে খৃস্টধর্মের আগমনের ফলে ধর্মের হাতে তা কিছুটা অবদমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলো। কারণ যদিও খৃস্টধর্ম তার আসল রূপ ও প্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছিলো এবং তাতে নানা দোষ-দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো, তবু এটা তো সত্য যে, তাতে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর আসমানি ধর্মের শিক্ষা-দীক্ষার কিছু না কিছু ছাপ ও বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিদ্যমান ছিলো। আর, কোন আসমানি ধর্ম, শত বিকার-বিকৃতির পরো মানুষে মানুষে কৃত্রিম কোন ভেদ ও বিভেদ এবং ভাষা, বর্ণ ও জাতীয়তার পার্থক্য স্বীকার করতে পারে না। তাই বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত ইউরোপকে খৃস্টধর্ম রোমান গীর্জার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেছিলো এবং খৃস্টজগতকে অভিন্ন পরিবারে পরিণত করেছিলো। history of morality-এর লেখকের ভাষায়, ‘ইউরোপের স্বদেশপ্রেম ও সম্প্রদায়প্রীতি সাধারণ মানব -হিতৈষণায় পরিবর্তিত হলো। এই মানসিক পরিবর্তন কতটা সুদূর প্রসারী ছিলো তা খৃস্টান পন্ডিতদের বক্তব্য-মন্তব্য থেকেও কিছুটা অনুমান করা যায়। যেমন, ট্রটোলীন বলেন, আমরা একটি প্রজাতন্ত্রের কথাই জানি, ‘বিশ্বপ্রজাতন্ত্র’। অরজিন বলেন, ‘আমাদের একটিই স্বদেশ, যার ভিত্তি হচ্ছে একটিমাত্র শব্দ, ‘ঈশ্বর’।
কিন্তু মার্টিন লুথার (১৪৮৩- ১৩২৬) যখন বৈপ্লবিক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দিলেন এবং রোমান গীর্জার বিরোধিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন তখনই ধর্ম-প্রভাবে অবদমিত ইউরোপীয় স্বভাব আবার জেগে উঠলো। লুথার স্বজাতি জার্মানদের সহযোগিতায় এতটাই সফল হলেন যে, শেষ পর্যন্ত রোমান গীর্জাকে পরাজয় মেনে নিতে হলো, আর বিক্ষিপ্ত ইউরোপকে যে ঐক্যসূত্রে গাঁথা হয়েছিলো তা ছিঁড়ে গেলো, কোন বন্ধনই আর থাকলো না। ফলে ইউরোপীয় জাতিবর্গ ক্রমে আভ্যন্তরীণভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। বস্ত্তত ইউরোপে খৃস্ট- ধর্মের পতন এবংসাম্প্রদায়িক- তা ও জাতীয়তাবাদের উত্থান শুরু হয়েছিলো সমান্তরালে। অর্থাৎ ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ যেন ছিলো দাঁড়িপাল্লার দুই দিক; একটি যত নীচে নামে অন্যটি তত উপরে উঠতো। আর ধর্মের পাল্লাই ভার হারিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলো এবং জাতীয়তাবাদের পাল্লা ভারী হয়ে নীচে নামছিলো। আমেরিকায় এক- সময়ের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত সুপ্রসিদ্ধ পন্ডিত লর্ড লুথিয়ান, ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া ভাষণে এ ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছিলেন-
‘ইউরোপে একসময় ঐরকম সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য বিদ্যমান ছিলো, যেমন ছিলো ভারতে ‘খৃস্টীয়তা’র প্রথম সময়ে। কিন্তু পনের শতকে (মার্টিন লুথারের) ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যখন ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য বিলুপ্ত করে দিলো তখন সমগ্র মহাদেশ বিভিন্ন জাতীয়তায় বিভক্ত হয়ে গেলো, যাদের পারস্পরিক সঙ্ঘাত শুধু ইউরোপ নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী হুমকি হয়ে দেখা দিলো।’
ধর্মের অপসৃতি এবং ধর্মীয় নীতি ও নৈতিকতার বিলুপ্তির কারণে স্বদেশবাদ ও জাতীয়তাবাদের যে প্রবল উত্থান ঘটেছিলো, একই ভাষণে তিনি সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন-
‘ধর্ম হলো মানুষের অপরিহার্য পথপ্রদর্শক এবং জীবনে নৈতিক ও আত্মিক মর্যাদাবোধ অর্জনের একক মাধ্যম। কিন্তু ধর্মের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হওয়ার অনিবার্য ফলরূপে পাশ্চাত্য এমন সব রাজনৈতিক মতবাদ ও চিন্তাধারায় আক্রান্ত হয়ে পড়লো যার ভিত্তি ছিলো নিছক জাতিগত ও শ্রেণীগত ভেদ-বিভেদ। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার প্রভাবে পাশ্চাত্য এ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হলো যে, বস্ত্তগত উন্নতিই হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। এজন্যই ইউরোপে এখন জীবনের সমস্যা ও জটিলতা বেড়েই চলেছে এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সমন্বয় দুরূহ হয়ে পড়েছে, অথচ এটাই হলো ‘যুগের বড় দুর্যোগ’ জাতীয়তাবাদের কবল থেকে মুক্তির উপায়।’
পাশ্চাত্যের অহং ও প্রাচ্যবিদ্বেষ
ধর্মব্যবস্থার পতন ও জাতীয়তা- বাদের উত্থানের প্রথম ফল এই হলো যে, আত্মবিভেদ সত্ত্বেও ইউরোপ সমগ্র প্রাচ্যের বিপক্ষে এক অভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হলো এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, কিংবা ইউরোপ ও গর-ইউরোপ, আরো পরিষ্কার ভাষায় আর্য ও অনার্য জাতিবর্গের মাঝে এমন একটি স্থায়ী পার্থক্যরেখা টেনে দেয়া হলো যে, ‘এপারের’ সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতি ‘ওপারের’ সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বেঁচে থাকার, সমৃদ্ধি অর্জন করার এবং শাসন করার অধিকার এপারের একচ্ছত্র; অন্য কারো, বা অন্য কিছুর বেঁচে থাকার ও বিস্তার লাভ করার অধিকার নেই। বলাবাহুল্য যে, এটাই ছিলো স্ব-স্ব উত্থানকালে গ্রীক ও রোমক জাতির স্বভাবচিন্তা। তাদের চোখে শুধু তারাই ছিলো পৃথিবীর সভ্য জাতি, আর বিশেষ করে আটলান্টিকের পূর্বতীরের সবকিছু ছিলো ‘বর্বর’।’
জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক- তার এ চরম উগ্র ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার ফল এই ছিলো যে, বহিরাগত যে কোন ব্যক্তি, বস্ত্ত, শিক্ষা ও দর্শনের প্রতিই তারা ছিলো চরম বিদ্বেষী। এমনকি ইউরোপের কোন কোন জনগোষ্ঠী স্বয়ং যীশু ও তাঁর ধর্মের প্রতিও বিদ্বেষ পোষন করতো। কারণ তিনি বহিরাগত, সুতরাং তাঁর ধর্ম বহিষ্কারযোগ্য। যেমন জনৈক জার্মান শিক্ষাবিদ বলেন, ‘আমাদের সন্তানদের কেন আমরা ভিন্ন জাতির ইতিহাস শেখাবো? কেন তাদের ‘ইবরাহীম-ইসহাকের’ কাহিনী শোনাবো? আমাদের চাই খাঁটি জার্মান ঈশ্বর।’
সেখানে এমন সম্প্রদায়ও ছিলো যারা যীশকে শুধু ইসরাঈলী হওয়ার ‘অপরাধে’ প্রত্যাখ্যান করেছিলো। পক্ষান্তরে তাঁর প্রতি অটল বিশ্বাসীরা তাঁকে ‘আর্যরক্তীয়’ প্রমাণ করার জোর প্রয়াসী ছিলো। এমনকি একসময় জার্মান জাতির উপাস্য প্রাচীন দেব-দেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন বা প্রবণতাও দানা বেঁধে উঠেছিলো।
তদ্রূপ আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রবক্তা রাশিয়াও উগ্র জাতীয়তাবাদে তার প্রাচীন শত্রু জার্মানির চেয়ে কোনভাবেই পিছিয়ে ছিলো না। সেখানে বহু মানুষ বিশ্বাস করে যে, আধুনিক যুগের যা কিছু মৌলিক আবিষ্কার -উদ্ভাবন, তাতে সিংহভাগ অবদান হলো রুশবিজ্ঞানীদের। তাদের মতে পদার্থের যৌগিকতা -বিষয়ক সূত্রের আবিষ্কারক ফরাসী রসায়নবিদ lavoisier নন, বরং তিনি রুশ বিজ্ঞানী মিশেল লোমুতূসেভ-এর কাছে ঋণী। তদ্রূপ বিদ্যুৎ শক্তির উদ্ভাবক টমাস এডিসন নন, বরং রুশ বিজ্ঞানী লিউজীন তার ছয় বছর আগে বিদ্যুৎ উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রাবদা পত্রিকার মতে, রুশ বিজ্ঞানিগণ মার্কিন বিজ্ঞানী স্যামুয়েল মুরিস-এর আগে টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করেছেন এবং জর্জ স্টিফেনসন-এর আগে বাস্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছেন।’ ইতিহাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের আরো বহু দাবী আছে, যার উৎস উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুক্তিহীন রুশবন্দনা ছাড়া আর কিছু নয়।
ছোঁয়াচে জাতীয়তাবাদ মুসলিম জাহানে
পরম পরিতাপের বিষয় যে, জাতীয়তবাদের এ ভয়াবহ ব্যাধি কতিপয় মুসলিম দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে, অথচ প্রত্যাশা ছিলো, তারা হবে ইসলামের বিশ্বদাওয়াতের অগ্রদূত এবং পৃথিবীর জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তাবাহী। বরং তারাই হবে অভিশপ্ত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধের শক্তিশালী কেন্দ্র। বলাবাহুল্য যে, এটা হতে পেরেছে ঐসব দেশে দ্বীনের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়া এবং পাশ্চাত্যের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। তাই তুরস্কের উছমানি সালতানাতে দেখা যায় ‘তূরানবাদ’ নামে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ফেতনা, যার লক্ষ্য ছিলো প্রাচীন তুর্কী জাহিলিয়াত ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ। ইসলাম, যা আরবদের মাধ্যমে তুর্কীরা পেয়েছে, তার প্রতি তারা ছিলো চরম বৈরী, যেমন ছিলো নতুন জার্মানে অনার্য মাধ্যমে আগত ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি, যাকে তারা উপহাস করে বলতো, ‘সেমিটিক ধর্ম ও সভ্যতা’। একই ভাবে নবীন তুরস্কের কোন কোন চিন্তানায়ক ভাবতেন, ইসলাম হচ্ছে তুর্কীজাতির উপর চাপিয়ে দেয়া একটি বহিরাগত ধর্ম, যা কিছুতেই তাদের উপযোগী নয়। সুতরাং তাদের জাতীয় কর্তব্য হলো প্রাচীন প্রতিমাপূজায় ফিরে যাওয়া, যা ছিলো ইসলামপূর্ব যুগে তাদের নিজস্ব ধর্ম। নতুন তুরস্কের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান রূপকার বলে খ্যাত যিয়া কোক আলিব সম্পর্কে খালিদা এদীব খানম বলেন-
তিনি এমন এক নতুন তুরস্কের স্বপ্ন দেখছিলেন যা উছমানি তুর্কী এবং তাদের পূর্ববর্তী তূরানিদের মধ্যে যোগসূত্র হবে। তিনি ইসলামপূর্ব তুর্কীদের নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন যাতে এগুলোর উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাপক নাগরিক সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। তার স্থির বিশ্বাস ছিলো যে, , আরবদের হাতে প্রবর্তিত ইসলাম আমাদের অবস্থার উপযোগী নয়। সুতরাং যদি আমরা আমাদের জাহেলি যুগে ফিরে যেতে না চাই, তাহলে অন্তত এমন কোন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যা আমাদের পূর্ণ স্বভাব-উপযোগী।’
বলাবাহুল্য যে, এরূপ আত্মঘাতী ঝোঁক-প্রবণতা শেষদিকে যেমন তুর্কীদের মধ্যে দানা বেঁধেছিলো তেমনি বেঁধেছিলো ইরানীদের মধ্যেও।
মরহূম আমীর শাকীব আরসলান আরববিষয়ে যেমন তেমনি তুর্কী- বিষয়েও ছিলেন আস্থাযোগ্য বিশেষজ্ঞ পন্ডিত, কারণ ‘মজলিসুল উম্মাহ’-এর সদস্যরূপে দীর্ঘকাল তিনি তুরস্কে বাস করেছেন। তিনি বলেন-
‘ইসলামী উছমানি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে আরেকটি চিন্তাধারা ছিলো তূরানি জাতীয়তাবাদ। এর সামনের কাতারের প্রবক্তারা হলেন যিয়া কোক আলিব, আহমদ আগায়েফ, ইউসুফ আকশোর (এদু’জন রুশঅঞ্চল থেকে আগত), জালাল সাহির, ইয়াহয়া কামাল, হামদুল্লাহ ছাবহী, জাতীয় কবি মুহম্মদ আমীন বেক এবং আরো বহু সাহিত্যিক চিন্তাবিদ। ছাত্রসমাজ ও নতুন প্রজন্মের সিংহভাগ এ মতবাদে অনুরক্ত ছিলো। এদের দাবী হলো, সভ্যতার ক্ষেত্রে তুর্কীরা হচ্ছে অগ্রবর্তী প্রাচীনতম জাতি। তুর্কী ও মঙ্গোল হচ্ছে অভিন্ন নৃতাত্ত্বিক সত্তার অধিকারী। সুতরাং তাদেরকে ‘তূরানি সঙ্ঘ’ নামে আবার অভিন্ন সত্তায় ফিরে যেতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি শুধু সাইবেরিয়া, তুর্কিস্তান, চীন, ককেসাস ও বলকানের তুর্কীদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং এদিকে চীনের মঙ্গোল এবং ওদিকে ইউরোপের হাঙ্গেরি ও ফিনল্যান্ড পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো। কারণ তাদের মতে এরা সকলে তূরানী নৃ-মূল থেকে উৎসারিত। প্রথম চিন্তাধারার বিপরীতে এদের দাবী ছিলো, ‘আমরা প্রথমে তুর্কী, তারপর মুসলিম।’ বরং এরা ধর্মপরিচয় ও ইসলামী বন্ধন বর্জনের পক্ষপাতী ছিলো, তবে ‘তূরানবাদ’ বিস্তারে কোনভাবে সহায়ক হলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ ইসলামী পরিচয়টি উদ্দেশ্য না হয়ে শুধু মাধ্যম হতে পারে। কোন কোন তূরানবাদী এতটা বেড়েছিলো যে, তাদের উদ্ধত ঘোষণা ছিলো, ‘আমরা তুর্কী, সুতরাং আমাদের কা‘বা হলো তূরান।’
চেঙ্গিজ খান ছিলো তাদের জাতীয় বীর এবং মঙ্গোল বিজয়াভিযান ছিলো তাদের স্ত্ততি-বন্দনার বিষয়। এসম্পর্কে বহু গান, কবিতা ও সঙ্গীত রচিত হয়েছিলো, যাতে তরুণ প্রজন্ম চেঙ্গিজপূজা ও মঙ্গোলবন্দনার দীক্ষায় গড়ে ওঠে এবং ‘যেন তাদের সাহস ও মনোবল উৎকর্ষ লাভ করে’।’
তিনি আরো বলেন-
‘ইউরোপের অনুকরণে যেহেতু এ যুগটি ছিলো বিভিন্ন জাতীয়তা- বাদের যুগ সেহেতু পারসিক জাতীয়তাবাদও পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী শক্তি লাভ করেছিলো। বস্ত্তত এটা ছিলো তূরানবাদেরই পারসীয় সংস্করণ। তাই পারস্যের নতুন প্রজন্মকে দেখতে পাই পারস্যের প্রাচীন ধর্ম সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠতে যেমন তুর্কী নতুন প্রজন্ম তাদের প্রাচীন ধর্ম ও উপাস্য সাদা নেকড়ে সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলো। যার একটি প্রকাশ ঘটেছিলো এভাবে যে, আধুনিক বইপত্রে সাদা নেকড়ের চিত্র অঙ্কিত হতো।
এদের উদ্দেশ্যে শায়খুল ইসলাম মূসা কাযিম বলেছিলেন - তিনি নিজে আমাকে তা শুনিয়েছেন- ‘আরবদেরও ছিলো এমন সব পূজা -পদ্ধতি যা ভাবলেও গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু তারা ইসলামের মাধ্যমে সেগুলো নির্মূল করেছিলো। তাদের গর্ব ছিলো যে, আল্লাহ দয়া করে এরূপ নীচতা ও মূর্খতা থেকে তাদের উদ্ধার করেছেন। অথচ আজ তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করে নেকড়েপূজায় লিপ্ত হতে চাও! ধীক তোমাদের।
তো তুর্কীদের ঘটনা পারসিকদের বেলায়ও ঘটলো। তাদের নতুন প্রজন্ম পারসীয় প্রাচীন ধর্মগুলোর পুনরুজ্জীবনপ্রয়াসে মেতে উঠলো। যেমন ‘আলো ও অন্ধকার তত্ত্ব’ যা থেকে অগ্নিপূজার উদ্ভব ঘটেছে। তদ্রূপ যরথোস্ট্রো-চিন্তা, প্রথমে যিনি আল্লাহর একত্বের প্রচারক ছিলেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ হচ্ছেন আলো ও অন্ধকারের স্রষ্টা, আর এদু'য়ের সংমিশ্রণেই কল্যাণ ও অকল্যাণের অস্তিত্ব। এ সংমিশ্রণ ছাড়া বিশ্বজগতের অস্তিত্ব সম্ভবই হতো না। এধরনের বিভিন্ন সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস যা প্রাচীন পারস্যে প্রচলিত ছিলো, যেমন দ্বিত্ববাদ ও মানুবাদ। কেউ কেউ মাযদাক- বাদেরও প্রবক্তা ছিলো যার মূল কথা হলো নাস্তিকতা ও অবাধ স্বেচ্ছাচার।
আরবজাহানে জাতীয়তাবাদ
এর চেয়ে ভয়াবহ বিষয় ছিলো এই যে, খৃস্টীয় উনিশ শতকের শেষ দিকে জাতীয়তাবাদের সর্বনাশা ব্যাধি আরবদের মধ্যেও সংক্রমিত হলো; অথচ আরবরাই সুদীর্ঘ তের শতাব্দী মানবজাতিকে মানবভ্রাতৃত্ব ও মানবসাম্যের শিক্ষা দান করে এসেছে। কারণ তাদের জন্য আল্লাহর মনোনীত দ্বীনুল ইসলামের এটাই ছিলো শিক্ষা।
এই দুষ্ট জাতীয়তাবাদ একসময় তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিলো। অবশ্য এর যথোপযুক্ত কার্যকারণও ছিলো, কিছু অন্তর্গত এবং কিছু বহির্গত।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্গত কারণটি হচ্ছে জাতীয় অহঙ্কার, যা তুর্কী শাসক-প্রশাসক ও রাজকর্মচারীদের আচরণে প্রকাশ পেতো। বলাবাহুল্য যে, তুর্কীদের অহমিকা ও দম্ভ খুব অবমাননাকরভাবে আরবদের এধারণা দিতো যে, তারা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর জনগোষ্ঠী। বিশেষ যারা অতি সংবেদনশীল তাদের দৃষ্টিতে তুর্কীদের আচরণ-উচচরণ ছিলো চরম ঔপনিবেশিক। পরিস্থিতি আরো সঙ্গিন হয়ে গেলো এ কারণে যে, আরবীভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্ব দেয়া হয়নি, পক্ষান্তরে শাসকজাতির ভাষা তুর্কীকে করা হলো সরকারী ভাষা। তুর্কীদের এজাতীয় আরো কিছু রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতা আরবদের মধ্যে জাতীয় আক্রোশ ও আরবীয় অহমিকা উসকে দিয়েছিলো।
অবশ্য খৃস্টান আরব বুদ্ধিজীবীরাও এর পিছনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে, তুর্কীদের সঙ্গে যাদের না ছিলো দ্বীন ও আকীদার সম্পর্ক, না ছিলো ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। এরা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিমন্ডলে প্রতিপালিত হয়েছিলো, যার সাহিত্যে, সঙ্গীতে, কাব্যে ও দর্শনে ছিলো শুধু জাতি ও জাতীয়তাবাদের জয়গান।
এরপর উপস্থিত হলো বহির্গত কার্যরকারণটি। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক কর্ণধারগণ পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। উছমানি সাম্রাজ্যের পতন তো তাদের বহু কালের স্বপ্ন, যাতে প্রাচ্য থেকে তুর্কীদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব-প্রতিপত্তি পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারা যখন দেখলো যে, কিছু আরব যুবকের চিন্তাজগতে জাতীয়তাবাদী চেতনা অঙ্কুরিত হচ্ছে তখন তারা সুবর্ণ সুযোগ ভেবে মুখে-কলমে ও লেখায়-বক্তৃতায় ঐ চিন্তা-চেতনাকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি যোগাতে লাগলেন। এ উদ্দেশ্যে তারা আরব- জাহানের বড় বড় শহর ও রাজধানীতে নিয়মিত যাতায়ত শুরু করলেন এবং আরব লেখক, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং গোত্রপ্রধান ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হলেন। নিঃস্বার্থ আরবপ্রেম এবং আরব অধিকারের সংরক্ষণের মুখোশ পরে তারা এ চিন্তাটি ছড়িয়ে দিলেন যে, খেলাফাতের কেন্দ্র হবে, আস্তানা নয়, হারামাইন বা কোন আরব ইসলামী রাজধানী। কারণ হিজরী দশম শতাব্দীতে তুর্কীরা আরবদের হাত থেকে খেলাফাত ছিনিয়ে নিয়েছিলো, সুতরাং আরবরাই হচ্ছে খেলাফতের স্বাভাবিক, বৈধ ও শরীয়তসম্মত হকদার।
এ সর্বনাশা চিন্তা আরবদের মাথায় কীভাবে অনুপ্রবেশ করলো এবং ধীরে ধীরে তার বিষক্রিয়া শুরু হলো, সর্বোপরি পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ এ চিন্তার জন্মদান ও স্তন্যদানের পিছনে কী খেল খেলেছেন তা পরিষ্কার বুঝতে হলে আমাদের মিস্টার ওয়েলফার্ড বেলেন্টির ফিউচার অব ইসলাম বইটি অবশ্যই পড়তে হবে। আঠারো শ বিরাশিতে লেখা বইটি আরব ও ইসলামি বিশ্বে তখন বেশ চমক ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। আরবীসহ এর বিভিন্ন অনুবাদও বিপুল প্রচার পেয়েছিলো। বইটির ভূমিকায় মিস্টার বেলেন্টি বলেন,‘ খেলাফতবিষয়ে মিশরীয় নেতৃবৃন্দ ভারসাম্যপূর্ণ এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাদের পূর্ণ শক্তি ও মনোযোগ এখন নিবদ্ধ ‘স্বাধীনতা’-এর প্রতি, অন্যকিছুতে নয়। কখনো তারা প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি, বা ইসলামের দুর্গে কোনরূপ ফাটল ধরাননি। সে অভিপ্রায়ও তাদের ছিলো না। কেননা আমীরুল মুমিনীন হিসাবে সুলতান আব্দুল হামীদ খান সবার কাছেই স্বীকৃত ছিলেন এবং তুলনামূলক তিনিই ছিলেন এ মহান পদের যোগ্যতম ব্যক্তি। মোটকথা, খেলাফতের নবজাগরণ বা দ্বিতীয় উত্থানের বিষয়টি তুলে রাখা হয়েছিলো ঐ সময়ের জন্য যখন উছমানি খেলাফতের ‘নাকে শ্বাস নিয়ে’ স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। কোন সন্দেহ নেই যে, এটি ছিলো মিশরীয়দের ধীরস্থির ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং এটাই ছিলো তাদের জন্য উপযুক্ত।
একপর্যায়ে তিনি বলেন, ‘যদি আমরা আর কয়েকটি বছর ধৈর্য ধারণ করতে পারি তাহলে এ বিজয় যে আরো ব্যাপক ও চমকপ্রদ হবে তাতে খুব বেশী মানুষের সন্দেহ নেই। কারণ সুলতান আব্দুল হামীদ খানের মৃত্যু হোক বা অপসারণ, এর অবশ্যম্ভাবী ফল হবে কায়রোয় খেলাফতকেন্দ্রের স্থানান্তর, আর তা আরবদের সামনে সুবর্ণ সুযোগ এনে দেবে তাদের হারানো ধর্মীয় নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের।
তার বইয়ের একটি অধ্যায় হলো, ‘মক্কা- প্রকৃত রাজধানী’, তাতে তিনি বলেন, ‘মুসলিম জ্ঞানী- সমাজের সামনে এটা সুস্পষ্ট যে, যদি আমরা পিছনের দিকে যাত্রা শুরু করি (অর্থাৎ খেলাফতকেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল থেকে এশিয়ার অন্য কোন স্থানে নেয়া হয়) তাহলে আমরা এক সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে বাধ্য হবো। বস্ত্তত দ্বীনের কেন্দ্র ও রাজধানী হচ্ছে জাযীরাতুল আরবে। সেটাই হচ্ছে ইসলামের লালনক্ষেত্র এবং অহীর অবতরণ- ক্ষেত্র। সর্বোপরি সেটাই হচ্ছে ধর্মীয় শাসন ও নেতৃত্বের যাবতীয় গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী একমাত্র নিরাপদ শহর। ফলে তা এই শাসন ও নেতৃত্ব সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত বহন করতে পারবে। বাড়তি সুবিধা হলো, সেখানে ইহুদি-খৃস্টানদের উপস্থিতি নেই, ফলে বিবাদ-সঙ্ঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কাও নেই। আর তা পশ্চিমা দেশগুলোর লালা ঝরবে এমন উর্বর ও প্রাচুর্য- পূর্ণ ভূখন্ডও নয়। খলিফাকে সেখানে বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদূত বা অন্য কোন বিদেশী প্রতিনিধির ‘তম্বীহ’ শুনতে হবে না। ফলে তিনি সত্যিকার ‘নাইবে রাসূলের’ উপযুক্ত স্বাধীনতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন। আর ইসলাম ফিরে পাবে তার সর্বপ্রকার সকল আবিলতামুক্ত স্বচ্ছ নির্মল রূপ। এসব কারণে খুবই সম্ভব যে, খেলাফত মক্কায়, কিংবা মদিনায় তার যোগ্য অধিকারীদের কাছে ফিরে আসবে।’
ভদ্রলোক আরো বলেন, ‘মুসলিম জাতির আধ্যাত্মিক রাজধানী কুসতুনতুনিয়া থেকে মক্কায় স্থানান্তরের বিষয়টি খুব সহজ ও স্বাভাবিক একটি পদক্ষেপ, যা মানুষের বর্তমান চিন্তা-বিশ্বাসে তেমন কোন আলোড়ন বা পরিবর্তন সৃষ্টি করবে না, এমনকি তা আলেমসমাজের চিন্তাধারা ও মতামতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। বস্ত্তত উম্মাহর কর্ণধারদের জন্য মক্কা-মদিনাই হচ্ছে শরিয়তনির্দেশিত আধ্যাত্মিক নিরাপদ আশ্রয়স্থান এবং অতিসত্বর এদু’টি শহরই হবে আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্রভূমি। এ বিষয়ে যার সঙ্গেই আমি কথা বলেছি, তুর্কীদের বন্ধুরা ছাড়া সবাই পূর্ণ একমত প্রকাশ করেছেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, আলেমগণও এ চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থক। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, মক্কাই হওয়া উচিত খেলাফতের প্রধান কেন্দ্র। বহুদিন থেকে আমরা একটি জনপ্রিয় বাক্য শুনি, রোমই হচ্ছে রাজধানী। তো ‘মক্কাই হচ্ছে রাজধানী’ এ বাক্যটিও মানুষের চিন্তায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে। সঙ্গে যদি যোগ করা হয়, ‘খেলাফত কোরাইশের’ তাহলে নিঃসন্দেহ আরবরা তা সাদরে গ্রহণ করবে, আর আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আরবদের প্রভাববলয় মরোক্ক থেকে বুশেহর পর্যন্ত বিস্তৃ- ত। সুতরাং এ শ্লোগানে কমপক্ষে মরোক্ক থেকে বুশেহর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশুদ্ধ আরবজনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি আলোড়ন ও আন্দোলন অবশ্যই সৃষ্টি হবে। একইভাবে ভারত ও মালয়-এর মুসলিম জনগোষ্ঠীও ঐ প্রভাববলয়ের মধ্যে পড়ে, বরং যে কোন মুসলিম জনগোষ্ঠী যেখানে হোক তাদের অধিবাস, অভিন্ন কক্ষপথেই তাদের চিন্তা আবর্তিত হবে, শুধু তুর্কীদের বাদ দিয়ে, যারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি ও প্রভাব হারিয়েই চলেছে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো আর আরবদের সামনে উছমানি আনুগত্যের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলার সুযোগ অবারিত হলো, ওদিকে মিত্রশক্তিও সুযোগটি লুফে নিলো এবং আরবদের সামনে জাতীয়তাবাদের বাজনা বাজাতে শুরু করলো। ধুরন্ধর টমাস লরেন্স এ সময় মাঠে নামলেন এবং আরবভূখন্ডে জাতীয়তাবাদী চেতনার আগুন ছড়িয়ে দিলেন এবং বিশিষ্ট-সাধারণ প্রতিটি আরবকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললেন। হিজাযে শরীফ হোসায়ন বিদ্রোহ করলেন, শামে শামীরা এবং মিশরে মিশরীয়রা একই পথের পথিক হলো। মুসলিম তুর্কীরা, তখনো পর্যন্ত যারা ছিলো ইসলামের শক্তি ও প্রতাপের প্রতীক, এ দুঃসময়ে তাদের পাশে থাকার চেয়ে আরবরা মিত্রশক্তির পক্ষে ভিড়ে যাওয়াকেই লাভজনক মনে করলো। এ বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহর যত স্পষ্ট বাণী ও সতর্কবাণী ছিলো, সব ভুলে গিয়ে মিত্রশক্তির মিষ্টি মিষ্টি প্রতিশ্রুতির উপরই তারা ভরসা করলো, যাদের রাজনীতি ও কূটনীতি সতত পরিবর্তনশীল, সুবিধা ও স্বার্থ ছাড়া আর কিছু যারা জানে না এবং শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুর যারা পূজা করে না। সর্বোপরি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষই যাদের চলার মূল চালিকাশক্তি। সিরিয়ায় আরব হাশেমি শাসন প্রতিষ্ঠার পর মিত্রশক্তি কীভাবে সব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলো এবং হাশেমীদের দু’দিনের রাজত্ব তাশের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়েছিলো সে ইতিহাস তো সবারই জানা।
তারপর এলো আরবজাতীয়তাদের আদর্শিক চেতনার যুগ। বস্ত্তত এটা ছিলো আগাগোড়া এক পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ এক চিন্তাদর্শন। ধর্মের প্রতি যে পরিমাণ আবেগ-উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা এবং প্রশ্নাতীত পবিত্রতার অনুভূতি মানুষের অন্তরে থাকে জাতীয়তাবাদের পক্ষে সেগুলো পূর্ণমাত্রায়ই সক্রিয় ছিলো, বরং বলা চলে একটি নতুন ধর্মরূপেই যেন তা আত্মপ্রকাশ করেছিলো। ফলে শিক্ষিত আরব- জনগোষ্ঠী, বিশেষত যুবসমাজ, বহু কারণে ধর্মের সঙ্গে যাদের যোগসূত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিলো, দলে দলে জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত হলো। সম্ভাব্য কম সময়ে এবং সহজতম উপায়ে গৌরব ও মর্যাদা অর্জনের এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে স্বাধীন ও প্রাগ্রসর জাতিবর্গের সমকক্ষতা অর্জনের এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তাদের পেয়ে বসেছিলো। আর এজন্য তাদের
ধারণামতে আরবজাতীয়তাবাদের কোন বিকল্প ছিলো না। অন্যদিকে পশ্চিমা শক্তিগুলোর প্রতি তাদের মধ্যে বিরাট ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছিলো, যারা আরবদের বুকে বিষফোড়ার মত ইহুদিরাষ্ট্র ইসরাইলের জন্ম দিয়েছিলো এবং সর্বোতভাবে তাকে লালন-পালন করে যাচ্ছিলো। এ অপমানজনক পরিস্থিতিরই প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া ও চিন্তানৈতিক বিপ্লবরূপে আরবরা আরবজাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করলো। অতিউৎসাহীরা এক্ষেত্রে এতই সীমালঙ্ঘন করলো যে, আরবজাতীয়তাবাদ ছাড়া সবকিছু প্রত্যাখ্যান করার এবং প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যও তারা প্রস্ত্তত হয়ে গেলো, এমনকি ইসলাম ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধেও। তবে জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভাটার টান লাগতেও বেশী দেরী হলো না। কারণ শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র এবং হারানো আরবমর্যাদা পুনরুদ্ধারের সর্বোত্তম উপায়রূপে যে আরবজাতীয়তাবাদকে তারা অাঁকড়ে ধরেছিলো তা ষাতষট্টির আরব-ইসরাইল যুদ্ধে কোন অলৌকিক ফল বয়ে আনতে পারেনি, বরং বয়ে এনেছিলো নতুন জাতীয় লাঞ্ছনা ও যিল্লতি।
ইউরোপের জাতীয়তাবাদঃ উপকরণ ও প্রকৃতি
আগের আলোচনায় ফিরে আসি। ইউরোপে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার অনিবার্য ফল হলো এই যে, ছোট-বড় প্রতিটি জনপদ ও জনগোষ্ঠী নিজেদের ভিন্ন জগতের বাসিন্দা বলে ভাবতে শুরু করলো, যার বাইরে আর কোন জগত নেই। একদিকে প্রকৃতি তাদের নদী ও পর্বতের সীমারেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলো, অন্য দিকে তারা নিজেরাও রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থে সঙ্কীর্ণ একটি ‘আত্মবষ্টনী’ তৈরী করে নিয়েছিলো। ঐ সীমারেখা ও বেষ্টনীর বাইরে যে আরো কোন জগত আছে এবং সেখানে মানুষের অধিবাস আছে তা তারা ভাবতেই প্রস্ত্তত ছিলো না। নিজেদের অস্তিত্বের বাইরে অন্য কিছুর প্রতি তাদের না ছিলো আগ্রহ, না ছিলো শ্রদ্ধা। নিজেদের তারা উপাস্যের আসনে বসিয়ে আত্ম-উপাসনায় মেতে উঠেছিলো। উপাস্য ও উপাসিতের মধ্যে উপাসনা ও বন্দনার যত রকম সম্পর্ক হতে পারে সবই তারা গ্রহণ করেছিলো। তাদের যুদ্ধ ছিলো এই উপাস্যের সন্তুষ্টির জন্য; হত্যা ও লুণ্ঠন এবং জনপদের পর জনপদের ধ্বংসসাধন. সবই ছিলো ঐ উপাস্যের ক্ষুধা ও চাহিদা পূরণের জন্য। এককথায় আত্ম-উপাস্যের আত্মবন্দনার জন্যই ছিলো তাদের জীবন ও মরণ এবং তাদের যুদ্ধ ও লুণ্ঠন।
জাতীয়তাবাদ নামের এ নতুন ধর্মের প্রধান ও প্রথম বিশ্বাসই ছিলো এই যে, জাতি ও জাতীয়তা হচ্ছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে। আমার জাতির চেয়ে উত্তম এবং আমার দেশের চেয়ে সুন্দর কোন দেশ ও জাতি পৃথিবীতে নেই। স্রষ্টা বলে যদি কিছু থেকে থাকে, কিংবা এ শব্দটির ব্যবহার যদি জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হয় তাহলে বুদ্ধি, মেধা, গুণ ও প্রজ্ঞায় এবং বিশ্বকে শাসন করার যোগ্যতায় তিনিই আমার জাতিকে অন্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুতরাং পৃথিবীতে আমরাই স্রষ্টার নির্বাচিত শাসক ও অভিভাবক। শাসন করা আমাদের অধিকার, আর আনুগত্য ও দাসত্ব হলো সর্বজাতির কর্তব্য। এককথায় জাতীয়তাবাদের এই আগ্রাসী দানব অন্য কোন জাতি ও জনগোষ্ঠীকে পৃথিবীর কোন ভূখন্ডে বাস করার ও বেঁচে থাকার অধিকারই দিতে রাজি নয় যতক্ষণ না তারা দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে নেবে।
এই আগ্রাসী চিন্তার ক্ষেত্রে বর্তমান ইউরোপের জাতি ও রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। হিংস্রতায়, রক্তলোলুপতায়, সম্পদলুণ্ঠনের উন্মত্ততায় একই সমান্তরালে সবার অবস্থান। পার্থক্য শুধু কৌশলে ও কর্মপন্থায় এবং আবরণে ও আলখেল্লায়। কেউ যা বলে তাই করে এবং যা করে তাই বলে, আর কেউ যা করে, মুখে তা বলে না, অর্থাৎ পিঠে ছুরি বসায়, তবে মুখের হাসি থাকে অটুট। কারণ জাতীয়তাবাদের বীজ যে মাটিতে এবং যে জলবায়ুতেই বপন করা হোক তার বৃক্ষ হবে কণ্টকাকীর্ণ এবং ফল হবে তিক্ত ও বিষাক্ত। এটা সম্ভবই নয় যে, কোন জাতি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হবে আর তার মধ্যে লুণ্ঠন ও আগ্রাসনের মনোভাব থাকবে না, কিংবা অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্যের অনুভূতি থাকবে না। যেমন সম্ভব নয় যে, কেউ মদে চুর হবে, কিন্তু নেশাগ্রস্ত হবে না এবং প্রলাপ বকবে না। কবি ভাষায়-
‘হাত-পা বেঁধে ফেলে দিলো নদীতে, আর বলা হলো, সাবধান, ভিজে না যেন পানিতে।’
বিশেষ করে শিল্প ও সাহিত্য এবং ইতিহাস ও দর্শন, এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞানও যখন জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুঘটকরূপে কাজ করে এবং জাতির সর্বস্তরে রক্ত-বংশের অহঙ্কার এবং অতীত ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করার মানসিকতাকে সুড়সুড়ি দেয়, আর তাতে কোন ধর্মীয় ও নৈতিক বাধা-প্রতিবন্ধকও না থাকে সর্বোপরি জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যখন তাদের হাতে চলে যায়, জাতীয় অহঙ্কার ও আত্মগৌরবের প্রচার ছাড়া যাদের আর কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই তখন অবস্থা কত ভয়াবহ হতে পারে তা তো বলাই বাহুল্য।
যে দু’টি উপাদান ছাড়া জাতীয়তা- বাদ কখনো টিকে থাকতে পারে না, যাকে বলা যায় জাতীয়তা- বাদের মূল প্রাণ, তা হলো ভীতি ও ঘৃণা। জাতির সামনে যদি ঘৃণা ও ভয় করার মত কিছু তুলে ধরা না যায় তাহলে জাতীয়তাবাদের চেতনা সৃষ্টি হতে পারে না, হলেও স্থায়ী হতে পারে না। তাই জাতীয় নেতৃবর্গ ঘৃণা ও ভয়, এ দুই পথে জাতির আবেগ-অনুভূতিকে উসকে দেন এবং ‘ব্যথার শিরায়’ চাপ দিয়ে এমন তোলপাড় ও উন্মাদনা সৃষ্টি করেন যেন এক প্রলয়ঙ্করী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। এজন্য কখনো তারা তিলকে তাল বানান, তুচ্ছাতি -তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং বাস্তব-অবাস্তব শত্রুকে সামনে এনে জাতির ভিতরে ভয়-ভীতি ও ক্রোধ-ঘৃণার অনুভূতিকে চাঙ্গা রাখার প্রয়াস চালান। কারণ এরই মধ্যে রয়েছে অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এবং শাসন ও নেতৃত্বের নিরাপত্তা। বস্ত্তত এদু’টি অনুঘটক না থাকলে জাতীয়বাদের বেলুন বহু আগেই চুপসে যেতো এবং জাতীয়তাবাদের জোয়ারে কবেই ভাটার টান শুরু হয়ে যেতো। প্রফেসর জুড এর যে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পেশ করেছেন তা দেখুন-
‘কোন সম্প্রদায়ে যে চেতনাটি সম্মিলিতরূপে বিদ্যমান এবং যা খুব সহজেই জাগিয়ে ও চাগিয়ে তোলা যায় এবং যার মাধ্যমে গোটা সম্প্রদায়কে উদ্দীপ্ত করা যায় তা কিন্তু প্রেম ও ভালোবাসার অনুভূতি নয়, বরং ভয়-ভীতি ও ক্রোধ-ঘৃণার অনুভূতি। ভালো-মন্দ যে কোন উদ্দেশ্যে যারা কোন সম্প্রদায়ের উপর শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাতে তরা সফল হতে পারে না যতক্ষণ না ভয় বা ঘৃণা করার মত কিছু তারা তাদের সামনে তুলে ধরতে পারবে, হোক তা কোন বস্ত্ত বা ব্যক্তি, কিংবা কোন দল ও জনগোষ্ঠী। আমার কথাই ধরুন; আমি যদি (পরস্পর যুদ্ধরত) বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই তাহলে আমার কর্তব্য হবে চাঁদ-মঙ্গল যে কোন গ্রহ-উপগ্রহ থেকে কোন কাল্পনিক শত্রু তাদের সামনে খাড়া করা যাকে তারা ভয় বা ঘৃণা করবে (তারপর অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আত্মকলহ ভুলে গিয়ে ঐ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে)।
এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে আর অবাক হওয়ার কিছু থাকে না যখন আমরা দেখি, সে যুগের জাতীয় সরকারগুলো প্রতিবেশী জাতির সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে ভীতি ও ঘৃণার আবেগের উপর নির্ভরশীল ছিলো এবং শাসকশ্রেণীর কাছে এটাই ছিলো শাসন ও নেতৃত্বের রক্ষাকবচ এবং এটাই ছিলো জাতীয় ঐক্য-চেতনার বুনিয়াদ।
আজকের বিশ্বে এই যে জাতিগত হানাহানি ও সঙ্ঘর্ষ এবং অর্থ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত তা থেকে মানবজাতির উদ্ধারের জন্য প্রফেসর জুড যে সমাধান দিয়েছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ ও বোধগম্য। এটা অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত কখনো বন্ধ হবে না যদি না তা অন্যখাতে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা হয়। এজন্য কোন বহিঃশত্রুকে তাদের সামনে আনতে হবে যার প্রতি তাদের সবার থাকবে প্রচন্ড ভয়-ভীতি, ক্রোধ-আক্রোশ ও ঘৃণা-বিদ্বেষ, আর ঐ সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তারা পরস্পরের প্রতি বাড়িয়ে দেবে সহযোগিতার হাত এবং পোষণ করবে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। তবে এজন্য, মিস্টার জুড যেমন বলেছেন, কল্পনা ও উদ্ভাবনা শক্তির প্রয়োজন নেই এবং চাঁদ-মঙ্গল থেকে শত্রু খুঁজে আনার দরকার নেই। কারণ কোরআনের ভাষায়-
‘কীভাবে সম্ভব হবে তাদের জন্য অত দূর থেকে লড়াই করা।’
তাই আল্লাহর মনোনীত আসমানী ধর্ম ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়ে ঘোষণা করেছে যে, মানবজাতি ও আদমসন্তানের এই সাধারণ শত্রু অন্যখানে, অন্য কোন গ্রহে নয়, বরং এই পৃথিবীতেই রয়েছে। সুতরাং আদম- সন্তানের কর্তব্য হলো এই শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য ভাষা, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা। কোরআনের ভাষায়-
শয়তান তোমাদের জন্য শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রুরূপে গ্রহণ করো। নিঃসন্দেহে শয়তান তার দলকে ডাকে যাতে তারা জাহান্নামী হয়।
হে ঈমানদারগণ, তোমরা শান্তির ধর্মে প্রবেশ করো পরিপূর্ণরূপে, আর তোমরা শয়তানের পথে চলো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের ‘খোলা দুশমন’।’
এ কারণেই ইসলাম গোটা মানব- জাতিকে শুধু দু’ভাগে ভাগ করেছে; হক ও সত্যের অনুসারী এবং মিথ্যা ও বাতিলের পূজারী; এককথায় আল্লাহর দল ও শয়তানের দল। তারপর আল্লাহর দলের প্রতি ইসলামের উদাত্ত আহবনা হলো শয়তানি দলের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করা। কেননা তারা যমিনে শুধু ফিতনা-ফাসাদ, অনাচার-পাপাচার ছড়ায়, আর সত্য ও সুন্দর এবং ন্যায় ও কল্যাণকে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করতে চায়। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, দেশ ও জাতীয়তা এবং ভাষা ও গোত্রপরিচয় তাদের যাই হোক। ঘৃণা-বিদ্বেষ ও লড়াই-যুদ্ধের বুনিয়াদ ইসলামের দৃষ্টিতে ভূগোলের সীমারেখা যেমন নয় তেমনি নয় ভাষা ও বর্ণের ব্যবধান, বরং একমাত্র বুনিয়াদ হলো আকীদা ও বিশ্বাস, নীতি ও নৈতিকতা, মানবতার কল্যাণ-অকল্যাণ এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিদ্রোহ। কোরআনের ঘোষণা-
‘যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফুরি করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা শয়তানের দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল।’
হাঁ, আল্লাহর নবী আল্লাহর জন্য জিহাদ ও যুদ্ধ করেছেন, তবে তা আরব বা অনারব কোন জাতি ও জনগোষ্ঠীর স্বার্থের জন্য ছিলো না, বরং ছিলো মানবতার সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। এ সব যুদ্ধ একদিকে যেমন শয়তানের বন্ধু ও মানবতার শত্রুদের দমন করেছে তেমনি অন্যদিকে বয়ে এনেছে মানবতার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং পারলৌকিক মুক্তি ও সৌভাগ্য। অথচ সভ্যতার ইতিহাস এর চেয়ে কম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর কখনো দেখেনি। ছোট্ট একটি পরিসংখ্যান শুনুন। দ্বিতীয় থেকে নবম হিজরী পর্যন্ত সমস্ত গাযওয়া ও সারিয়ায় উভয় পক্ষে নিহতের সংখ্যা হচ্ছে একহাজার আঠারো। মুসলমান দু’শ ঊনষাট, আর কাফির হলো সাতশ ঊনষাট। পক্ষান্তরে ইতিহাসে এর আগে ও পরে যত যুদ্ধ হয়েছে তার যে কোন একটির রক্তপাতের পরিমাণ দেখুন, আপনি হতবাক হবেন; হিংস্রতা, বর্বরতা, পাশবিকতা ও অর্থসম্পদের ক্ষয়ক্ষতির কথা তো আলাদা।
ইসলামের ধর্মযুদ্ধ তো রক্তপাত বন্ধ করেছে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, সর্বোপরি তা মানবতার জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্য বয়ে এনেছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য যুদ্ধ মানবজাতিকে কী উপহার দিয়েছে? সঙ্ঘাতের পর সঙ্ঘাত, ধ্বংসের পর ধ্বংস ছাড়া আর কিছু? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী বীর মিস্টার লয়েড জর্জ, যিনি তখন বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রধান ছিলেন এবং ভার্সাই সন্ধিচুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তিনি কী বলছেন শুনুন-
‘প্রভু যিশু যদি ফিরে আসেন, খুব সামান্য সময়ই বেঁচে থাকতে পারবেন। কারণ তিনি দেখবেন, দু’হাজার বছর পরো মানুষ পাপাচারে ও খুনাখুনিতে লিপ্ত। মানুষই এখন মানুষের হিংস্রতায় বিপর্যস্ত। আমি তো বলতে চাই, ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধটি মানবজাতির রক্ত নিঃশেষ করে সেরেছে। ফসল ও গবাদিপশু ধ্বংস হওয়ার পর মানুষ এখন অনাহারে দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছে।
বলুন তো প্রভু যিশু পৃথিবীতে এসে কী দেখবেন? তিনি কি দেখবেন যে, মানুষ ভাই ও বন্ধুর মত পরস্পর করমর্দন করছে? নাকি দেখবেন, প্রথম যুদ্ধের চেয়ে আরো ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের আয়োজন শুরু হয়েছে, আর মানুষ পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে?
এই যে বিভিন্ন জাতি আজ হিংসা-হানাহানিতে লিপ্ত হচ্ছে এবং একের পর এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তা কেন? এই যে ভৌগলিকতার শ্লোগান এবং জাতীয়তাবাদের জয়গান, মানুষ তাতে কেন এমন বিভোর? কারণ শুধু এই যে, দেশ, অঞ্চল, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে মানুষ আজ তার প্রকৃত শত্রুকে ভুলে গিয়েছে। যা ছিলো মানবজাতির সম্মিলিত যুদ্ধক্ষেত্র তা থেকে সরে গিয়ে মানুষ নিজেই এখন বিভিন্ন দলে আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। কারণ আগুন যদি গ্রাস করার মত কিছু না পায় তখন নিজেই নিজেকে গ্রাস করে। তাই তো সেই কবে জাহেলি যুগের কবি বলে গিয়েছেন-
‘কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ি আমাদের গোত্র-ভাই বকরের উপর, যখন ভাই ছাড়া কাউকে খুঁজে না পাই।’
পক্ষান্তরে মানুষ যদি তার আসল শত্রুকে চিনতে পারে এবং অদৃশ্য এই শত্রু, শক্তিতে ও কূটকৌশলে কতটা ভয়ঙ্কর তা বুঝতে পারে তাহলে মুহূর্তের মধ্যে তারা সব কৃত্রিম শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও লড়াই-বিবাদ ভুলে যাবে। এত দিনের সব শত্রু তখন ভাই ও বন্ধুতে পরিণত হবে এবং শিসাঢালা প্রাচীরের মত ঐ শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। আরবের প্রাচীন প্রবাদ হলো-
‘আত্মরক্ষার লড়াই হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়ে দেয়।’
বিশ্বনবী মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নববী তারবিয়াতের মাধ্যমে এটাই করেছিলেন। মদীনায় আউস ও খাযরাজ গোত্রে যে দীর্ঘ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ চলছিলো এবং জাযীরাতুল আরবে কাহতান ও আদনান গোত্রে যে আত্মবিনাশী সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষ চলে আসছিলো তাদের তিনি কুফুর ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে এক উম্মত ও অভিন্ন শিবিরে পরিণত করেছিলেন। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও খুন-খারাবি ভুলে গিয়ে তারা হয়ে উঠেছিলো ভাই ভাই। ‘ইন্নামাল মু‘মিনূনা ইখওয়াহ’ এই বিশ্বাস ও চেতনায় তারা যেন এক নবজন্ম লাভ করেছিলেন। কারণ আল্লাহর নবী তাদের জন্য প্রবল শক্তিধর একটি বহিঃশত্রু চিহ্নত করেছিলেন, যাকে তারা ঘৃণা করবে এবং চিরশত্রুরূপে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর সে শত্রু হলো শয়তান ও তার অনুচর, কোরআনের ভাষায় যাদের বলা হয়েছে তাগুত এবং আউলিয়াউশ-শয়তান। ইরশাদ হয়েছে-
‘যারা ঈমান এনেছে তারা তো আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, আর যারা কুফুরি করেছে তারা তাগুতের পক্ষে লড়াই করে। সুতরাং তোমরা শয়তান ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।’
মুসলিম উম্মাহ যতদিন এই সাধারণ শত্রুর কথা মনে রেখেছিলো ততদিন তারা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও লড়াই-বিবাদ থেকে দূরে ছিলো। কিন্তু যখনই তারা এই সাধারণ শত্রুর কথা ভুলে গেলো এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করা ছেড়ে দিলো তখনই তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের শত্রুতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং তারা ভয়াবহ অন্তর্কলহ ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এভাবে এক ও অভিন্ন মুসলিম উম্মাহর ভিতরে সর্বগ্রাসী ফেতনার আগুন জ্বলে উঠলো, যা ইতিহাসের পাতায় আমাদের কলঙ্ক হিসাবে এখনো লেখা আছে।
মানব-ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চেতনা ও উন্মাদনা যখন যেখানে শিকড় গেড়েছে, পরস্পরের প্রতি ভয়ভীতি ও ঘৃণা-বিদ্বেষের মাধ্যমেই গেড়েছে। অতীত ও বর্তমানের প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী সরকার ও সম্রাজ্য ভয়-ভীতি ও ঘৃণা-বিদ্বেষ, এদু‘টি অশুভ শক্তির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এবং প্রাচীন ও আধুনিক যতগুলো ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে, যা মানবজাতির অস্তিত্বের প্রতি ছিলো অব্যাহত হুমকি, তা মূলত এ দুই জিঘাংসা ও উন্মাদনারই মর্মন্তুদ পরিণতি।
তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত এবং মানবতার ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের আহবান নিয়ে যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো তখন এই অভিশপ্ত জাতীয়তাবাদকে জাহিলিয়াত বলে ঘোষণা করলো এবং ঐসব যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-খারাবিকে হারাম ঘোষণা করলো যার ভিত্তি নিছক সম্প্রদায়প্রীতি ও জাত্যাভিমান। আল্লাহর নবী সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন-
যারা সাম্প্রদায়িকতার ডাক দেবে তারা আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যারা সাম্প্রদায়িকতার উপর লড়াই করবে তারা আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যারা সাম্প্রদায়িকতার উপর মারা যাবে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।
জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার যুদ্ধে মৃত্যুকে ইসলাম জাহিলিয়াতের মৃত্যু বলে ঘোষণা করেছে। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে, অন্ধ ও অন্ধকার পতাকার নীচে, সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনায় একত্র হয়ে, কিংবা সাম্প্রদায়িকতার ডাক দিতে গিয়ে, কিংবা সাম্প্রদায়িকতার সাহায্য করতে গিয়ে যে লড়াই করবে এবং নিহত হবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু (অন্য বর্ণনায় ‘সে আমার উম্মতভুক্তই নয়।’)
কিন্তু আফসোস, ইসলামি উম্মাহর নবী যে মহাফেতনা সম্পর্কে এত কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন তা ভুলে গিয়ে শত্রুর কূটচক্রান্তে উম্মাহ সেই তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লো। ফলে তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদা-বিশ্বাস এবং উখুওয়াত ও ভ্রাতৃত্বের জাযবা- চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত এক ও অভিন্ন মুসলিম উম্মাহ আজ শতধা বিভক্ত এবং প্রতিটি খন্ড শত্রুর একেকটি সহজ লোকমায় পরিণত, যেমন আল্লাহর নবী বলেছেন, বিভিন্ন জাতি একে অন্যকে ডেকে আনবে যেমন মানুষকে ডাকা হয় খানার দস্তরখানে।
জাতীয়তাবাদের পূজারীদের কর্মকৌশল
জাতীয়তাবাদের পূজারীরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে যে কৌশল গ্রহণ করে তা এই যে, প্রথমে তারা ক্ষুদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীগুলোর সামনে জাতীয়তাবাদের আলোঝলমল রূপ তুলে ধরে এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির গুণগানে এবং অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অতিবন্দনায় তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে। ফলে প্রতিটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদের নেশায় এমনই বুঁদ হয়ে থাকে এবং জাতীয় ঐতিহ্যের মিথ্যা অহমিকায় এতই আত্মহারা হয়ে পড়ে যে, তারাই যেন শ্রেষ্ঠ, তারাই যেন একমাত্র। ফলে বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা নিজেদের জাতীয় পরিচয়ের সঙ্কীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনগোষ্ঠী শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর আগ্রাসনের শিকার হয়। শক্তির অহমিকায় বিজয়ী জনগোষ্ঠী তখন এমনই বেশামাল হয়ে পড়ে যে, বড় শক্তির সাথেও সঙ্ঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, কিংবা বড় শক্তি কোন না কোন অজুহাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফল এই দাঁড়ায় যে, তারা বড় শক্তির সহজ ও নরম লোকমায় পরিণত হয়, আর যেহেতু তারা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী সেহেতু কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না, বরং দূর থেকে তামাশা দেখে, খুব বেশী হলে কিছু ‘ঠোঁট-সেবা’ প্রদান করে।
এমনকি একসময় যারা তাদেরকে জাতীয়তাবাদের ফানুস দেখিয়েছিলো তারাও তাদের পরিত্যাগ করে। কোরআনের ভাষায়-
শয়তানের মত, যে মানুষকে বলে কুফুরি করো। যখন মানুষ কুফুরি করে তখন সে বলে ওঠে, তোমার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আমি মুক্ত। দুর্বল জনগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদের প্রাচীর সৃষ্টি করে এবং সারা বিশ্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবে যে, তারা আরো শক্তিশালী ও নিরাপদ হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, এভাবে তারা বৃহৎ শক্তিবর্গের আগ্রাসন ডেকে আনে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে মধ্য ইউরোপের ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশগুলোর ভাগ্যে এটাই ঘটেছিলো। কিন্তু আফসোস, ইসলামী দেশগুলো, যাদের হাতে রয়েছে বিশ্ব-দাওয়াতের পতাকা এবং এমন অফুরন্ত শক্তি যে, যদি তা কাজে লাগানোর যোগ্যতা থাকে তাহলে গোটা ইউরোপ যাবতীয় বল ও লোকবলসহ তাদের পদানত হতে বাধ্য। কারণ তাদের শক্তি ইউরোপের জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দর্শনের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু ইসলামি ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে তাদেরও ঝোঁক এখন সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ। অথচ অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে ইউরোপীয় দেশগুলোর চেয়ে তারা যথেষ্ট পিছিয়ে। সুতরাং এ আশা করা বাতুলতা যে, জাতীয়বাদের দুর্গে বাস করে মুসলিম দেশগুলো খুব বেশী দিন কোন বিপদের মোকাবেলা করতে পারবে।
পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদের পূজারী বৃহৎ শক্তির দেশগুলো মনে করে, যে কোন মূল্যে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে বড় বড় ভূখন্ডের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে হবে এবং বিশাল-বিস্তৃত উপনিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে দুর্বল জাতি ও জনগোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব এবং তাদের সম্পদের উপর দখলস্বত্ব কায়েম করা যায়। প্রতিবেশী দেশ ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তারা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জন করে, তেমনি অন্যদিকে ভাষা, বর্ণ ও ভূগোলভিত্তিক জাতীয় অহমিকা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। জাতিকে তারা এ উন্মাদনায় বিভোর করে রাখে যে, তাদের ভাষা ও সাহিত্য এবং ইতিহাস ও সভ্যতাই হলো শ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী; পক্ষান্তরে দূর ও নিকটের অন্যান্য জাতি ও জনগোষ্ঠীর কাছে গর্ব করার মত কোন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও
ইতিহাস-ঐতিহ্য নেই। নিজেদের জাতীয় শক্তি, সংহতি ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য নির্দ্বিধায় হিংস্র থেকে হিংস্র এবং নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুর যে কোন কাজ তারা করতে পারে। তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ স্বার্থের জন্য অন্য জাতির অধিকার ও মর্যাদা ভূলণ্ঠিত করতে, এমনকি ব্যাপক গণহত্যা চালাতেও তাদের কোন দ্বিধা নেই। এর পেছনে কোন নৈতিক বা মানবিক উদ্দেশ্য থাকে না, থাকে শুধু তাদের ভাষায় ‘জাতীয় গৌরব’। নিকট অতীতে এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলো আমেরিকা ও ভিয়েতনাম, (আর চলমান উদাহরণ ও রক্তক্ষরণ তো মুসলিম উম্মাহর চোখের সামনেই রয়েছে!)
এধরনের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ যতই নিকৃষ্ট হোক, মানুষ ও মানবতার প্রতি তাদের অবজ্ঞা যত জঘন্যই হোক জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিতে সেই দেশ, জাতি ও তাদের কর্ণধাররাই হলো প্রশংসা ও বন্দনার যোগ্য। এই জাতীয় গৌরবের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রফেসর জুড বলেন-
‘জাতীয় মর্যাদা ও গৌরবের একমাত্র অর্থ হলো এমন শক্তির অধিকারী হওয়া যাতে প্রয়োজনে নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা অন্য জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া সম্ভব হয়। তথাকথিত এই জাতীয় গৌরবই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের পূজারীদের একমাত্র আরাধ্য।
এর অসারতা প্রমাণের জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এটা নৈতিক ও চারিত্রিক মহত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বার্থ ত্যাগ করে শুধু ন্যায় ও সত্য অনুসরণ করা, কথা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতির সঙ্গে মানবিক আচরণ করা, জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিতে মর্যাদা ও গৌরবের কোন বিষয় নয়। মিস্টার বোলডন-এর মতে মর্যাদা মানে এমন শক্তি যা দ্বারা জাতি গর্ব ও গৌরব ছিনিয়ে আনতে পারে এবং অন্যান্য জাতিকে তটস্থ রাখতে পারে। আর বলাবাহুল্য যে, এমন শক্তি নির্ভর করে গোলা ও বোমার উপর এবং সেই সাহসী ও দেশপ্রেমী সৈনিকের উপর যারা যে কোন জনপদে নির্দ্বিধায় গোলা ও বোমা নিক্ষেপ করতে পারে। মোটকথা, কোন জাতি ও জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ঐ সকল নীতি ও নৈতিকার সম্পূর্ণ বিপরীত যা কোন ব্যক্তির জন্য মর্যাদার বিষয়। সুতরাং আমার মতে কোন জাতি ও জাতীয় নেতা যত বেশী এ ধরনের মর্যাদার অধিকারী হবে, আসলে সে তত বেশী বর্বর ও অসভ্য হবে। ধোকা ও প্রতারণা এবং শোষণ ও নিপীড়ন দ্বারা অর্জিত মর্যাদা না ব্যক্তির জন্য গৌরবের, না জাতির জন্য।
সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা
জাতীয়তাবাদের পূজারী বিভিন্ন শক্তি যখন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে তখন মানবজাতির দুর্ভোগ আরো চরমে পৌঁছে যায়। কারণ একটি শক্তি যখন এগিয়ে যায় এবং বিস্তীর্ণ কোন জনপদে উপনিবেশ কায়েম করে, প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি তখন চুপচাপ বসে থাকে না, বরং অগ্রবর্তী শক্তিকে হটিয়ে পাল্টা দখল প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। কারণ সম্পদ লুণ্ঠন ও পণ্যসামগ্রীর বাজার সৃষ্টির জন্য তারও উপনিবেশের প্রয়োজন। তাকে তো যে কোন মূল্যে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরে জাতীয় গৌরবের পতাকা উড্ডীন করতে হবে। জাতীয়তাবাদ এক পৃথিবীতে দুই শক্তির অবস্থান মেনে নিতে প্রস্ত্তত নয়। অন্যদিকে দখলদার শক্তিও দখল ছাড়তে রাজি নয়। এভাবে দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের লড়াই শুরু হয়ে যায়। তাতে বিপুল সম্পদ ধ্বংস হয় এবং দু’পক্ষেই লোকক্ষয় ঘটে প্রচুর। তবে ধ্বংস- যজ্ঞের আসল ঝড় বয়ে যায় সেই জনপদ ও জনগোষ্ঠীর উপর, দুর্ভাগ্যক্রমে যাদের ভূগর্ভে লুকিয়ে আছে বিপুল সম্পদভান্ডার, কিন্তু নেই আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় শক্তি ও অস্ত্রসম্ভার। তবে পরিহাসের বিষয় এই যে, এ-সবই সঙ্ঘটিত হয় মানবতা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার নামে এবং দুর্বল জাতিকে সাহায্য করার নামে। উভয় পক্ষই দাবী করে, তাদের যুদ্ধ নিজেদের জন্য নয়, বরং দুর্বল জাতিকে শাসন ও শোষণ থেকে রক্ষা বা উদ্ধার করার জন্য। তবে ভিতরে- বাইরে অনেকেই আগ্রাসী শক্তিগুলোর সাধুচিন্তা ও সদিচ্ছা সম্পর্কে প্রবলভাবে সন্দিহান। প্রফেসর জুড বলেন-
ইংরেজ ভুলে যায়, বা ভুলে যাওয়ার ভান করে যে, সমস্যা ও সঙ্কটের মূল শিকড় কোথায়? কী কী কারণে সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষ এবং শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। ভুলে যায়, বা ভুলে যাওয়ার ভান করে যে, জাপান ও অন্যান্য জাতির ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের উৎস কী? তাদের বরং দাবী হলো, ইংরেজ খুবই শান্তিপ্রিয় জাতি, জাপানীরাই বরং পররাজ্যলোভী যুদ্ধোন্মাদ। তাদের দাবী হয়ত ঠিক, ইংরেজ নির্লোভ ও শান্তিপ্রিয় জাতি, তবে সে ঐ লুণ্ঠনকারীর মত যে এখন লুণ্ঠন-পেশা ছেড়ে সাধু সেজেছে। কারণ লুণ্ঠিত সম্পদ ইতিমধ্যেই তাকে নিরঙ্কুশ প্রভাব ও প্রতাপ এবং গৌরব ও মর্যাদায় ভূষিত করেছে। সুতরাং শান্তিরক্ষার তাগিদে নব্যলুণ্ঠকদের বিরুদ্ধে সে সংহারমূর্তি ধারণ করতেই পারে। অর্থাৎ সাবেক লুণ্ঠক ও বর্তমানের সাধু ব্যক্তিটি তাদেরকে যুদ্ধবাজ বলছে যারা শোষণে ও লুণ্ঠিত সম্পদে ভাগ বসাতে চায়।
আগ্রাসন ও রাজ্যদখলের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে পড়া, কিন্তু জাতীয়তা- বাদের উন্মাদনায় একই রকম উন্মাদ শক্তিগুলোর মধ্যে যত যুদ্ধ হয়েছে ও হচ্ছে তার বীভৎসতা ও ধ্বংসলীলা তো আমাদের সামনেই রয়েছে, সুতরাং তা তফসীল করে বলার প্রয়োজন নেই, শুধু বলতে চাই যে, এসব যুদ্ধকে কিছুতেই ঐ সকল যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয় যা সত্যিকার অর্থেই যালিমকে দমন এবং মযলূমকে রক্ষার মহান উদ্দেশ্যে ইসলামের ইতিহাসে সঙ্ঘটিত হয়েছে। যেমন আলকোরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন-
যদি মুমিনদের দু’টি দল পরস্পর সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের মধে সমঝোতা করে দাও। আর যদি একদল অপর দলের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে তাহলে যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যেন তারা আল্লাহর আদেশের কাছে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে তাহলে উভয়ের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে সমঝোতা করে দাও, আর সুবিচার করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলা সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।
(আলহুজুরাত, ৯)
কারণ জাতীয়তাবাদের যুদ্ধ হচ্ছে রাজ্যদখল, সম্পদ লুণ্ঠন এবং জাতীয় অহং ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে। এগুলো অবশ্যই বিলুপ্ত জাতিপুঞ্জ ও বর্তমান জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানেই ঘটে থাকে, তবে সেটা শুধু আগ্রাসন, লুণ্ঠন, শোষণ ও নিধনযজ্ঞকে আইনগত বৈধতা দেয়ার জন্য। বস্ত্তত জাতিপুঞ্জ বলুন, কিংবা জাতিসঙ্ঘ, তাদের নিষেধ-নির্দেশ ও প্রস্তাব-সুফারিশ অবনত মস্তকে মেনে নেয় শুধু অসহায় দুর্বল পক্ষ। আগ্রাসী শক্তির উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আগে যেমন ছিলো না, এখনো নেই, আর তা এমনই জ্বলন্ত সত্য যা কোন অন্ধকেও বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাচ্যের দার্শনিক, মুসলিম উম্মাহর দরদী কবি আল্লামা ইকবালের ভাষায় এগুলো হচ্ছে চোর ও কাফনচোরদের আখড়া যারা চুরির মাল ও কাফনের কাপড় ভাগভাগি করতে বসেছে।
জাতিতে ইংরেজ প্রফেসর জুড সত্যের দাবী রক্ষা করে তাই বলেছেন-
‘জাতিপুঞ্জ নামের বিশ্বপুলিশি সংস্থাটির তত্ত্বাবধানে যে যুদ্ধই হয় তা ন্যায়, সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, কিংবা অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীকে প্রতিহত করার জন্য নয়। এগুলো আসলে শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়। একদলের লক্ষ্য, যে কোন মূল্যে বিশ্বের সম্পদভান্ডারের সর্বোচ্চ পরিমাণের উপর দখল বজায় রাখা, আর অন্যপক্ষের উদ্দেশ্য হলো যে কোন উপায়ে তাতে ভাগ বসানো। এসকল যুদ্ধ অতীতের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির মধ্যকার যুদ্ধের চেয়ে, কিংবা জার্মান-প্রোশিয়া যুদ্ধ, সপ্তবর্ষী যুদ্ধ, নেপোলিয়ানের যুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিলো না, ছিলো শুধু নামের ভিন্নতা। পক্ষান্তরে এসকল যুদ্ধের পক্ষে সাফাই গেয়ে যা কিছু বলা হয়, যেমন গণতন্ত্র রক্ষা, ফ্যাসিবাদ প্রতিহত করা, বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করা, ইত্যাদি, এগুলো প্রকৃতপক্ষে মুখের মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়।
(চলবে, ইনশাআল্লাহ)