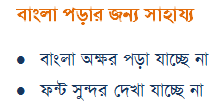দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন দু’টি যুগের মাঝে পার্থক্য-রেখা
জনৈক সাহিত্যিক বলেন, দু’টি ক্ষেত্রে নিখুঁত সূচনাকাল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; ব্যক্তিজীবনে নিদ্রা এবং জাতীয় জীবনে অধঃপতন।’ আসলেও তাই। কোন জাগ্রত ব্যক্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে একথা বলা সম্ভব নয় যে, ঠিক কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তদ্রপ কোন জাতি সম্পর্কেও একথা বলা সম্ভব নয় যে, ঠিক কোন্ সময়টাতে জাতির অধঃপতন শুরু হয়েছে। বস্তুত এদু’টি বিষয় তখনই পূর্ণ উপলদ্ধিতে আসে যখন তা ভালোভাবে জেঁকে বসে। তবে অধিকাংশ জাতির ইতিহাসে এটা সত্য হলেও মুসলিম উম্মাহর জীবনে অবক্ষয় ও অধঃপতনের সূচনা ছিলো বেশ স্পষ্ট। এমনকি যদি উন্নতি ও অবনতির এই মধ্যবর্তী পার্থক্য-রেখাটির উপর অঙ্গুলিনির্দেশ করতে বলা হয় তাহলে অতি সহজেই আমরা সেই ঐতিহাসিক রেখাটি চি?হ্িনত করতে পারবো যা খিলাফাতে রাশেদা ও আরব-মুসলিম শাসনকে পৃথক করে রেখেছে।
আমরা যদি একনজরে মুসলিম উম্মাহর উত্থানের কারণসমূহ পর্যালোচনা করতে চাই তাহলে দেখতে পাবো যে, সূচনাকালে প্রতক্ষভাবে মুসলিম শাসন এবং পরোক্ষভাবে বিশ্বশাসনের দায়িত্বভার এমন একদল মানুষের হাতে ছিলো যারা প্রত্যেকে ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং জীবন ও চরিত্র, নীতি ও নৈতিকতা, মহত্ত্ব ও মহানুভবতা, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা এবং পূর্ণতা ও ভারসাম্যপূর্ণতার ক্ষেত্রে মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন্ত মু‘জিযা ছিলেন।
ইসলামের ছাঁচে তাঁদেরকে তিনি এমন পরিপূর্ণরূপে গড়ে তুলেছিলেন যে, দেহসত্তা ছাড়া অন্যকোন ক্ষেত্রে অতীতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিলো না; না চিন্তা-চেতনায়, না ভাবে ও স্বভাবে এবং না চাওয়া ও চাহিদার ক্ষেত্রে। সূক্ষ্ম বিচারকের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেও তাঁদের জীবন ও চরিত্রে ইসলামের প্রাণ ও চেতনার পরিপন্থী জাহিলিয়াতের সামান্য কোন চি?হ্নও খুঁজে পাওয়া যেতো না। বরং নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলামকে একজন মানবরূপে উপস্থিত করা হলে তা হুবহু তাঁদেরই যে কোন একজনের মতই হতো। আগেও যেমন বলেছি, তাঁরা ছিলেন দ্বীন ও দুনিয়ার একত্রসমাবেশের যিন্দা নমুনা ও আদর্শ উদাহরণ। একদিকে তাঁরা ছিলেন মসজিদের মাননীয় ইমাম, অন্যদিকে আদালতের মহামান্য বিচারক। মসজিদে তাঁরা দ্বীন ও ইলম শিক্ষা দিতেন এবং আদালতে বিচারকের আসনে ইনছাফ কায়েম করতেন। একদিকে তাঁরা ছিলেন বাইতুল মালের আমানতদার ও পাহারাদার, অন্যদিকে রণাঙ্গনের যোগ্য সেনাপতি ও কুশলী যুদ্ধ- পরিচালক। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে যেমন তাঁদের কোন তুলনা ছিলো না, তেমনি ইকামাতে দ্বীন ও আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায়ও তাঁরা ছিলেন তুলনাহীন। এককথায় তাঁদের প্রত্যেকে একই সঙ্গে ছিলেন মুত্তাকী, পরহেযগার ও আল্লহভীরু ধার্মিক এবং সাহসী মুজাহিদ, ফকীহ মুজতাহীদ, বিজ্ঞ বিচারক, সুদক্ষ শাসক ও কুশলী রাজনীতিক। তাঁদের একই ব্যক্তি ছিলেন দ্বীন ও দুনিয়া এবং ধর্ম ও রাজনীতির ধারক, আর তিনি হলেন খলীফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মুমিনীন। তাঁর চারপাশে ছিলো এমন এক জামা‘আত, যারা মসজিদে নববীতে এবং নববী শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। অভিন্ন ছাঁচে তারা গড়ে উঠেছিলেন এবং অভিন্ন চিন্তা-চেতনা এবং আত্মা ও আত্মিকতার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের শিক্ষা, দীক্ষা ও তারবিয়াত ছিলো এক ও অভিন্ন। শাসনকার্যে ও অন্যান্য বিষয়ে খলীফা তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের সাহায্য নিতেন। তাঁদের উপস্থিতি ও পরামর্শ ছাড়া উম্মাহর কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। ফলে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা ও প্রাণ-চেতনা সমাজে ও প্রশাসনে এবং মানুষের জীবন ও চরিত্রে গভীরভাবে প্রতিফলিত হতো এবং তাঁদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা-প্রবণতা সর্বত্র পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হতো। তাই মানুষের আত্মা ও জড়সত্তা, ইহ জীবন ও পরজীবন এবং ধর্ম ও রাজনীতির মাঝে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিলো না। তদ্রূপ নীতি ও প্রবৃত্তি এবং উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার মাঝে ছিলো না কোন রেষারেষি, এমনকি বিভিন্ন সমাজশ্রেণীর মাঝেও ছিলো না কোন সংঘর্ষ। এককথায় ইসলামী সালতানাত ও মুসলিম সমাজ ছিলো তার পুরোধাপুরুষদের আখলাক ও চরিত্র, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ণতা ও ভারসাম্যপূর্ণতার আদর্শ প্রতিচ্ছবি।
জিহাদ ও ইজতিহাদ থেকে বিচ্যুতি
বস্তুত বিশ্বের বুকে ইসলামী ইমামাত ও নেতৃত্ব এবং শাসন ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কিছু সংবেদনশীল ও সুবিস্তৃত গুণ ও যোগ্যতার অনিবার্য প্রয়োজন। সংক্ষেপে সেগুলোকে আমরা জিহাদ ও ইজতিহাদ, এদু’টি শব্দে প্রকাশ করতে পারি। যে কোন ব্যক্তি বা দল ইসলামী ইমামাতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার অভিলাষী হবে তাদেরকে অবশ্যই সততা, সত্যবাদিতা এবং তাকওয়া ও ন্যায়পরতার পাশাপাশি জিহাদ ও ইজতিহাদেরও পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। বাহ্যত শব্দদু’টি খুব সহজ-সরল, কিন্তু কার্যকত তা অত্যন্ত ব্যাপক ও মর্মসমৃদ্ধ। জিহাদ অর্থ জীবনের প্রিয়তম ও মূল্যবানতম উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ও সর্বশক্তি ব্যয় করা। মুসলিম জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জন এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও বিধানের সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আর সেজন্য প্রয়োজন এক সুদীর্ঘ জিহাদ ও সুকঠিন সংগ্রামের। এই জিহাদ ও সংগ্রাম হবে ঐসব চিন্তা -বিশ্বাস, চাহিদা ও প্রবৃত্তি এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শের বিরুদ্ধে যা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়; তদ্রূপ ভিতরের ও বাইরের ঐ সব মিথ্যা উপাস্যের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগীর ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের এ মহৎ গুণ অর্জনের পর একজন মুসলিমের অবশ্যকর্তব্য হবে আপন সমাজে, চারপাশের জনপদে এবং পর্যায়ক্রমে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর আদেশ, বিধান ও শাসন প্রতিষ্ঠার জিহাদে আত্মনিয়োগ করা এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া। এটা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে তার উপর অর্পিত অপরিহার্য দায়িত্ব, তদুপরি মানবজাতির প্রতি দয়া ও সহৃদয়তারও এটাই দাবী। কেননা মানবতা ও সভ্যতাকে রক্ষা করার এটাই একমাত্র পথ, এমনকি তার আত্মকল্যাণের জন্যও এটা অপরিহার্য। কারণ এই জিহাদ ও মুজাহাদা ছাড়া ব্যক্তিজীবনের ইবাদত ও আনুগত্যও দুসাধ্য, বরং অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোরআনী পরিভাষায় এটাকেই বলা হয়েছে ‘ফিতনা’।
বলাবাহুল্য যে, মানুষ ও পশু-প্রাণী এবং উদ্ভিদ ও জড়বস্তুসহ সমগ্র বিশ্বজগত আল্লাহর ইচ্ছার অধীন এবং তাঁর জাগতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক বিধানের পূর্ণ অনুগত। ইরশাদ হয়েছে-
তাঁরই আনুগত্য গ্রহণ করেছে যা কিছু রয়েছে আকাশমণ্ডলীতে এবং পৃথিবীতে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, আর তারা তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে।’
তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহর সামনেই সিজদাবনত রয়েছে যারা আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং পৃথিবীতে এবং (সিজদাবনত) সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পাহাড়পর্বত ও পশু-প্রাণী এবং বহু মানুষ; আর অনেকের উপর অবধারিত হয়ে গেছে আযাব।’
এটা হলো প্রাকৃতিক ও বিশ্বজাগতিক বিধান, যাতে মানুষের প্রয়াস-প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা নেই। সৃষ্টিজগতে জীবন-মৃত্যু এবং উন্মেষ- বিকাশের যে বিধান আল্লাহ নির্বাচন করেছেন এবং প্রত্যেক শরীর ও স্বভাবের জন্য যে ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন সেই নিয়ম ও বিধানের বৃত্তেই সকলে বিচরণ করছে এবং করতেই থাকবে; তা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়ার ক্ষমতা ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন সৃষ্টিরই নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে মানুষের চেষ্টা-মেহনতের না প্রয়োজন আছে, না অবকাশ। মুসলিম উম্মাহকে যে জিহাদ ও মুজাহাদার আদেশ করা হয়েছে তা হলো আল্লাহর বিধান ও শারী‘আত প্রতিষ্ঠার জিহাদ এবং ইকামাতে দ্বীন ও ই‘লায়ে কালিমাতুল্লাহ-এর মুজাহাদা, যা নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন। যেহেতু ঐশী বিধান ও আসমানী শারী‘আতের বিপক্ষ শক্তি ও তার আন্দোলন পৃথিবীতে সবসময় আছে এবং থাকবে সেহেতু জিহাদ ও মুজাহাদাও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অবশ্য জিহাদ ও মুজাহাদার অসংখ্য শ্রেণী ও প্রকার রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো যুদ্ধ ও লড়াই এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কখনো তা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলেও গণ্য হয়, যার উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী কোন শক্তির অস্তিত্ব যেন পৃথিবীতে না থাকে, যা মানুষকে খাহেশাত ও কুপ্রবৃত্তি এবং শিরক ও কুফুরির দিকে টেনে নিতে পারে।
তাই ইরশাদ হয়েছে-‘আর লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে, যাতে কোন ফিতনার অস্তিত্ব না থাকে এবং পূর্ণ আনুগত্য যেন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।’
এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অন্যতম দাবী এই যে, মানুষ ইসলামের পূর্ণ পরিচয় ও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবে, যার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের জন্য সে জিহাদ করতে চায়, তদ্রূপ কুফর ও জাহিলিয়াত সম্পর্কেও তার পূর্ণ অবগতি থাকবে, যার মূলোৎপাটনের জন্য সে লড়াই করতে চায়। ইসলাম সম্পর্কে তার জ্ঞান হবে সঠিক ও নির্ভুল এবং কুফুর সম্পর্কেও তার অবগতি হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ, যাতে বাহ্যিকতার বর্ণচ্ছটা দ্বারা কখনো সে প্রতারিত না হয়। হক-বাতিল এবং সত্য-মিথ্যা যখন যেরূপেই তার সামনে আসুক, সে যেন তা চিনতে পারে। এজন্যই হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, ‘আমার আশংকা হয় যে, যার জন্ম ও প্রতিপালন হয়েছে ইসলামের পরিমণ্ডলে, অথচ জাহিলিয়াতের পূর্ণ অবগতি অর্জন করেনি, সে একটি একটি করে ইসলামের অঙ্গচ্ছেদন করে ফেলবে।’
এটা অবশ্য ঠিক যে, কুফুর ও জাহিলিয়াতের যাবতীয় প্রকার ও প্রকৃতি এবং প্রকাশ ও অভিপ্রকাশ সম্পর্কে সূক্ষ্ম-নিখুঁত ও পরিপূর্ণ অবগতি প্রত্যেক সাধারণ মুসলমানের জন্য জরুরি নয় এবং সম্ভবও নয়, তবে কুফুর ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদে যারা নেতৃত্ব দেবে এবং সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে তাদের জ্ঞান ও অবগতি অবশ্যই সাধারণ ও মধ্যস্তরের মানুষের চেয়ে বেশী হতে হবে এবং ইসলাম ও কুফুর উভয় সম্পর্কেই তাদের জ্ঞান হতে হবে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ।
তদ্রূফ কুফুর ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদ ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের সর্বপ্রকার শক্তি ও প্রস্তুতিও থাকতে হবে এবং তা হতে হবে সাধ্যের ভিতরে চূড়ান্ত স্তরে, যাতে তারা লোহার মুকাবেলায় লোহা হয়ে, এমনকি সম্ভব হলে ইস্পাত হয়ে এবং বাতাসের বিরুদ্ধে ঝড় হয়ে ময়দানে আসতে পারে এবং যুগের বাতিল শক্তির বিরুদ্ধেসর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে পারে। সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ যেন তারা অর্জন করে এবং মানুষের জ্ঞান-প্রযুক্তি যত অস্ত্র ও যন্ত্র এবং কল ও কৌশল উদ্ভাবন করেছে সবই যেন তারা আয়ত্ত করে।
কারণ আল্লাহ তা‘আলার সুস্পষ্ট আদেশ হলো-‘আর তোমরা প্রস্তুত করো তাদের মুকাবেলার জন্য তোমাদের সাধ্যের সকল শক্তি এবং অশ্বদল। তা দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে তোমরা আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তাদেরকে ছাড়া আরো কিছু লোককে, যাদের তোমরা চেনো না, আল্লাহ তাদের চেনেন। আর আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের প্রস্তুতিতে) যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে তার প্রতিদান তোমাদের পূর্ণরূপে দান করা হবে, আর তোমাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।’
আর ইজতিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, মুসলিম উম্মাহর ইমামাত ও নেতৃত্ব এমন সুযোগ্য মানুষের হাতে থাকবে যারা উম্মাহর জীবনে, বিশ্বের অঙ্গনে এবং মুসলিম শাসিত অঞ্চলে নব-উদ্ভূত সকল সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পারেন, যেগুলোর উত্তর বিধিবদ্ধ মাযহাব ও সংকলিত ফিকাহগ্রন্থে পাওয়া যায় না। শারী‘আতের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং ইসলামী আইনের মূলনীতিমালা সম্পর্কে তাদের থাকতে হবে পূর্ণ জ্ঞান এবং থাকতে হবে- একক বা সমষ্টিগত- এমন উদ্ভাবনী ও ইজতিহাদী যোগ্যতা, যাতে নতুন যে কোন সমস্যার যথার্থ ইসলামী সমাধান তারা নির্ধারণ করতে পারেন এবং সংকটকালে মুসলিম উম্মাহকে নির্ভুলভাবে পথপ্রদর্শন করতে পারেন।
তারা হবেন এমন মেধা ও উদ্যম এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী যাতে তারা আল্লাহর সৃষ্ট সকল প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাতে পারেন এবং ঐ সকল সম্পদ ব্যবহার করতে পারেন যেগুলো আল্লাহ ভূমিতে ও ভূগর্ভে লুকিয়ে রেখেছেন। তাদেরকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন সকল শক্তি ও সম্পদ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সেবায় নিয়োজিত হয়; শয়তান ও তাগুতি শক্তি যেন নিজেদের অশুভ উদ্দেশ্যে এবং পৃথিবীতে অনাচার ও পাপাচার সৃষ্টির কাজে সেগুলো ব্যবহার করতে না পারে।
যোগ্য হাত থেকে অযোগ্য হাতে উম্মাহর ইমামাত
কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্য এই যে, খিলাফাতে রাশেদার পর ইসলামী উম্মাহর ইমামাতের মহাগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার এমন লোকদের দখলে চলে গেলো যারা কোনভাবেই এর যোগ্য ছিলো না এবং এজন্য তাদের যথাযথ প্রস্তুতিও ছিলো না। তাদের পূর্ববর্তীগণ, এমনকি তাদের সমকালীন অনেকে যে দ্বীনী তারবিয়াত ও আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে তারা বঞ্চিত ছিলো, বরং আরবদের প্রাচীন গোত্রীয় চিন্তা-চেতনা ও ঝোঁক-প্রবণতা থেকেও তাদের মন-মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলো না। ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও ভাবধারায় তারা এতটা আত্মস্থ ছিলো না, ইসলামী উম্মাহর নেতৃত্ব -দানের জন্য যা ছিলো অপরিহার্য। জিহাদী চেতনা ও ইজতিহাদী যোগ্যতা কোনটাই তাদের ছিলো না, যা ইসলামী খিলাফাতের গুরু- দায়িত্ব বহন এবং বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য যা ছিলো জরুরী। আর এটা উমাইয়া ও আব্বাসী উভয় খিলাফাতের ক্ষেত্রেই ছিলো সমান সত্য। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু আদর্শ খলীফা হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)।
উম্মাহর জীবনে রাজতন্ত্রের অশুভ প্রভাব
এর ফলে ইসলামের মযবূত দেয়ালে এমন এমন ফাটল দেখা দিলো, যা আর বন্ধ করা সম্ভব হয়নি এবং ইসলামী উম্মাহর জীবনে এমন বিচ্যুতি ও বিকৃতি ঘটলো এবং একের পর এক এমন সব ফিতনা ও দুর্যোগ ধেয়ে আসতে লাগলো যা রোধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এখানে আমরা খুব সংক্ষেপে তার বিবরণ তুলে ধরছি।
রাজনীতি থেকে ধর্মের নির্বাসনইসলাম তো সাধারণ অর্থে একটি ধর্মমাত্র ছিলো না; ইসলাম তো ছিলো মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন, সবকিছুকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামের দ্ব্যর্থহীন দাবী হলো, সবকিছুতে শুধু আল্লাহর আদেশ নিষেধ কার্যকর হবে, অন্যকারো নির্দেশ নয়। সুতরাং রাজনীতি ও দেশশাসনের ক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের নিজস্ব আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধান। খিলাফতে রাশিদার দায়িত্ব ছিলো ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাজ্যশাসন পর্যন্ত সর্বত্র আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং খোলাফায়ে রাশিদীন পূর্ণ আমানতদারির সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বীন ও সিয়াসাত তথা ধর্ম ও রাজনীতির মাঝে কার্যত বিভাজন দেখা দিলো। শাসনক্ষমতা এমন লোকদের হাতে এসে গেলো যাদের না দ্বীন ও শারী‘আতের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছিলো, না তারা ওলামায়ে উম্মতের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেছিলো। রাজনীতি ও রাজ্যশাসনে তাদের ছিলো একচ্ছত্র ক্ষমতা। খেয়াল-খুশিতে, বা স্বার্থ-সুবিধার তাগাদায় তারা বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা হিসাবে ওলামায়ে উম্মত ও ফোকাহায়ে দ্বীন-এর সাহায্য নিতো এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থে নিজেদের মত করে তাঁদের ব্যবহার করতো, অর্থাৎ ওলামায়ে উম্মতের পরামর্শ যতটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করতো, যতটুকু ইচ্ছে বর্জন করতো। আবার সুযোগ হলে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিতো। এমনকি অনেক সময় তাঁদের উপর নির্মম নিপীড়ন নেমে আসতো। এভাবে রাজনীতি ও রাজ্যশাসন দ্বীনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে গেলো এবং ইসলামী খিলাফত হয়ে গেলো রোম ও পারস্যের মত নিছক স্বেচ্ছারী রাজতন্ত্র। খলীফা ও তার খিলাফত হয়ে গেলো, যেন লাগামহীন অবাধ্য উট। পরিস্থিতি যখন এমন গুরুতর, তখন ওলামায়ে ওম্মতের অবস্থা ছিলো এই যে, কেউ হুকুমতের প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হতেন এবং কখনো কখনো বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন। কেউ সংশোধনের চেষ্টায় কখনো কঠোর, কখনো কোমল ভাষায় তিরস্কার করতেন এবং উপদেশ দিতেন। তারা সব দেখতেন, শোনতেন, আর নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন; কার্যত তাদের করার কিছুই ছিলো না। আরেকদল সংশোধনে হতাশ হয়ে সবকিছু থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন। রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে গিয়ে তারা আত্মশোধন ও ব্যক্তিসংশোধন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। হয়ত তারা ভাবতেন, এভাবে যদি নিজেকে ও অল্পসংখ্যক অনুসারীকে দুনিয়ার ফিতনা থেকে বাঁচানো যায় তাহলে সেটাও অনেক বড় কামিয়াবি।
কেউ দ্বীনের কল্যাণ ভেবে শাসক ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। একদল এমনও ছিলো যারা শুধু হালুয়া-রুটির জন্য শাহী দরবারে হাজিরা দিতো। সব মিলিয়ে ফলাফল এই ছিলো যে, তত্ত্বে ও বিশ্বাসে না হলেও কার্যত দ্বীন ও সিয়াসাত এবং ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। আরো সরল ভাষায় যদি বলি, খিলাফতে রাশেদা-পূর্ব দুনিয়ার শাসনব্যবস্থার মত নামসর্বস্ব খিলাফতও তেমনি ধর্মহীন ও চরিত্রহীন অবয়ব লাভ করেছিলো। দ্বীন ও শরী‘আত যেন ছিলো ডানাকাটা পাখী, কিংবা শেকলপরা বন্দী, আর রাজনীতি ছিলো অবাধ ও মুক্ত-স্বাধীন। ধর্মের বাঁধন ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতেই থাকলো, আর রাজনীতির ভ্রষ্টাচার ও স্বেচ্ছাচার বেড়েই চললো। শেষ পর্যন্ত আহলে ইলম ও আহলে সিয়াসাত দু’টি বিপরীত শ্রেণীরূপে আত্মপ্রকাশ করলো, যাদের অপরিচয় ও দূরত্ব কখনো কখনো বিরোধ ও বিদ্বেষের রূপ গ্রহণ করতো।
শাসকদের মাঝে জাহিলিয়াতের ভাবধারাশাসকবর্গ, এমনকি খিলাফাতের ‘আমানতদার’ ব্যক্তিটিও দ্বীন ও আখলাক এবং ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শ ছিলেন না, বরং অনেকেই জাহেলিয়াতের চিন্তা-চেতনা ও রোগজীবাণু বহন করতো। ফলে স্বভাবতই জীবন ও সমাজের সর্বত্র তা সংক্রমিত হয়ে পড়েছিলো এবং মানুষ তাদের স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতাকেই অনুসরণ করতে শুরু করেছিলো। এটাই মানুষের স্বভাব ও ফিতরাত। তাই বলা হয়, ‘আন্নাসু আলা দ্বীনি মুলূকিহিম’- রাজার চালে রাজ্য চলে। দ্বীনের নিয়ন্ত্রণ, নৈতিকতার শাসন এবং বিবেকের অনুশাসন একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছিলো। ‘আমর বিল মা‘রূফ ও নাহী আনিল মুনকার’ হয়ে পড়েছিলো নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফল। কারণ তার পিছনে ছিলো না সরকারি ব্যক্তি ও শক্তি। দ্বীনদার শ্রেণীর স্ব-উদ্যোগের আদেশ-নিষেধের কেউ পরোয়া করতো না। কেননা তাদের না ছিলো তিরস্কারের ক্ষমতা, না পুরস্কারের সামার্থ্য। অথচ খাহেশাত ও প্রবৃত্তির উপকরণ ছিলো প্রচুর এবং অনাচার ও পাপাচারের হাতছানি ছিলো প্রবল। ফলে ইসলামী সমাজ ও মুসলিম জীবনে জাহিলিয়াত আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং দ্রুত শক্তি বিস্তার করতে লাগলো। আর দ্বীন ও দ্বীনিয়াত ভুলে মানুষ ডুবে গেলো ভোগ-বিলাস, খেল-বিনোদন ও শাহওয়ত-খাহেশাতের গান্দেগিতে। চিরস্থায়ী আখেরাতের পরিবর্তে মানুষের তখন লক্ষ্য ছিলো দুনিয়ার ধনদৌলত এবং ক্ষণস্থায়ী যিন্দেগির শানশৌকত। নফস ও নফসানিয়াতের বাজার ছিলো গরম। নাচ-গান এবং সুর ও সুরার মায়ফিল ছিলো জমজমাট। একথায় সমাজের প্রায় সবমানুষ সবকিছু ভুলে সবকিছুতে ডুবে গিয়েছিলো। ইছফাহানীর কিতাবুল আগানী এবং জাহিযের কিতাবুল হায়াওয়ান খুলুন; এদু'টোই আপনাকে খুলে খুলে বলে দেবে, মানুষ তখন কতটা ভোগবাদী ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হয়ে পড়েছিলো! কেমন সর্বগ্রাসী ছিলো দুনিয়ার লোভ-লালসা এবং পাপসর্বস্ব জীবনের আসক্তি! জীবন ও চরিত্রের এত দূর অধঃপতনের পর এবং অনাচার, পাপাচার ও ভোগ-বিলাসের এমন অতলে ডুবে যাওয়ার পর কোন জাতির পক্ষে আর যাই হোক, ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা, দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করা এবং নবুয়তের স্থলবর্তী হয়ে আল্লাহ ও আখেরাতের পথে ডাকা এবং তাকওয়া ও তাহারাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবন ও চরিত্রে মানুষের জন্য আদর্শ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, এমনকি দীর্ঘকাল স্বাধীন জীবনের স্বাদ গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যিল্লতি ও বরবাদি এবং লাঞ্ছনা ও অপদস্থতাই শুধু হতে পারে তাদের ভাগ্যলিপি। আলাকোরআনের ভাষায়- ‘এটাই ছিলো আল্লাহর শাশ্বত বিধান ঐসকল জাতির ক্ষেত্রে যারা বিগত হয়েছে, আর কিছুতেই পাবে না তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন।’
ইসলামের মন্দ প্রতিনিধিত্বএই অপদার্থ শাসকবর্গ তাদের যাবতীয় আচরণে-উচ্চারণে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা এবং ভ্রষ্ট রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থারই শুধু প্রতিনিধিত্ব করছিলো; ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ, ইসলামের রাজনীতি ও সমরনীতি এবং ইসলামের সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থার খুব কম প্রতিফলনই ছিলো তাদের জীবনে। ফলে অমুসলিদের সামনে ইসলামের বাণী ও বার্তা এবং দাওয়াত ও আহ্বান তার সব আবেদন হারিয়ে ফেলেছিলো, বরং ইসলামের প্রতি তাদের আস্থা ও আশ্বস্তিই দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। জনৈক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের ভাষায়- ‘ইসলামের অবনতি শুরু হয়েছিলো এজন্য যে, মানবজাতি তাদের সততা ও সত্যতায় সন্দিহান হয়ে পড়েছিলো যারা এই নতুন ধর্মটির প্রতিনিধিত্ব করছিলো।’
জ্ঞানচর্চার মৌলিক ভ্রান্তিআরেকটি বড় বেদনাদায়ক বিষয় ছিলো এই যে, অবনতি ও অবক্ষয়ের ঐ যুগে মুসলিম জ্ঞানী- মনীষিগণ যে গভীর অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞান ও গ্রীক ঈশ্বরতত্ত্ব চর্চা করেছেন, প্রাকৃতিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের চর্চা-গবেষণা তারা সেই পরিমাণ করেননি, অথচ জীবন ও জগতের নেতৃত্বের জন্য সেগুলোই ছিলো কার্যকর ও ফলপ্রসূ জ্ঞান। পক্ষান্তরে গ্রীক ঈশ্বরতত্ত্ব ছিলো শুধু গ্রীকদের জাতীয় প্রতিমাতত্ত্ব, যা তারা দর্শনিক পরিভাষা ও শাস্ত্রীয় পোশাকে উপস্থাপন করেছিলো- মাত্র। তাতে তত্ত্ব ও সত্য এবং সার ও সর বলতে কিছুই ছিলো না, ছিলো শুধু ধারণা ও অনুমান এবং শব্দজৌলুস ও বাক্য-ঝিলিক। অথচ মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে এসবের না ছিলো প্রয়োজনীয়তা, না ছিলো কোন সার্থকতা। কেননা নবী ও নবুয়তের মাধ্যমে উম্মাহকে আল্লাহ তা‘আলা যাত ও ছিফাত এবং ইলাহিয়্যাত সম্পর্কে সুসংহত ও সুনিশ্চিত জ্ঞান দান করেছিলেন, যার পর ঈশ্বরতত্ত্বীয় এসব চুলচেরা দার্শনিক আলোচনা ও ‘রাসায়নিক’ বিশ্লেষণে যাওয়া ছিলো নিরর্থক, বরং ধ্বংসাত্মক। আল্লাহ তো তাদের দান করেছিলেন ‘আল- ফোরকান’ নামে সুস্পষ্ট হিদায়াত ও নূর। কিন্তু মুসলিম চিন্তানায়করা এ মহান নিয়ামতের ‘শায়ানে শান’ শোকর এবং যথাযোগ্য কদর করেনি, বরং দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী তারা গ্রীক-চিন্তাপ্রসূত এসকল জ্ঞান ও শাস্ত্র নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে এবং দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রীয় এসকল অর্থহীন ও নিষ্ফল জটিলতায় মেধা ও বুদ্ধির অপচয় ঘটিয়েছে। এককথায় জিহাদের প্রকৃত ক্ষেত্র ত্যাগ করে বীরবিক্রমের তারা ‘বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ’ করেছে এবং নিজেদের হাতে নিজেদের বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এই নির্বোধ বুদ্ধিবিলাস তাদেরকে ঐসকল প্রায়োগকি জ্ঞান-গবেষণা ও শাস্ত্রচর্চা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যা দ্বারা প্রকৃতির যাবতীয় শক্তি ও সম্ভাবনা করায়ত্ত করে সেগুলোকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে নিয়োজিত করা যায় এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ইসলামের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়। একই ভাবে তারা রূহ ও আত্মা, ফালসাফাতুল ইশরাক ও নবপ্লেটো দর্শন এবং ওয়াহদাতুল ওজূদ ও এককসত্তাবাদ-এর জটিল আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছে এবং সময়, শ্রম, মেধা ও প্রতিভার বিপুল অংশ তাতেই ব্যয় করেছে।
একথা অবশ্য সত্য যে, মুসলিম মনীষিগণ প্রায়োগিক জ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন এবং তাদের কীর্তি ও কর্ম, গবেষণা ও উদ্ভাবনা পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেক বেশী ছিলো; কিন্তু সত্য এই যে, জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তাদের সুবিস্তৃত অবদানের সাথে তা মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না। তদ্রূপ ইতিহাসের যে সুদীর্ঘ সময়কাল তারা ভোগ করেছে সে তুলনায় তা সন্তোষজনক ছিলো না। এসময় প্রকৃতি বিজ্ঞানের শাখায় ঐ পরিমাণ প্রতিভা ও মনীষার আবির্ভাব ঘটেনি, জ্ঞান ও শাস্ত্রের অন্যান শাখায় যেমন ঘটেছে।
পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগের সাথে যদি তুলনা করি তাহলেও বলতে হবে যে, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও মহাজাগতিক বিজ্ঞানের উপর যে পরিমাণ গবেষণা ও গ্রন্থনা তারা রেখে গেছেন যদিও উত্থানকালের ইউরোপ সেগুলো থেকে বিরাটভাবে উপকৃত হয়েছে এবং মোটামুটি মূল্যায়নও করেছে; কিন্তু মাত্র সতের ও আঠারো শতকের সময়সীমায় ইউরোপের জ্ঞানী-বিজ্ঞানিগণ যে বিশাল ও সুসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার তৈরী করেছেন তার তুলনায় সেগুলো একেবারেই নগণ্য। স্পেন ও প্রাচ্যের মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও গবেষণাকর্ম নিয়ে আমরা যতই গর্ব করি পাশ্চাত্যের কীর্তি ও কর্মের পাশে তা উল্লেখযোগ্যই নয়। মানে ও পরিমাণেও নয়, নতুনত্ব ও সৃজনশীলতায়ও নয় এবং বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা ও শাস্ত্রীয় উৎকর্ষেও নয়। প্রাকৃতিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় আধ্যাত্মিক বিষয়াদির প্রতি ইসলামী প্রাচ্য কত বেশী যত্নবান ছিলো তা যদি বুঝতে চান তাহলে উদাহরণস্বরূপ শায়খ ইবনুল আরাবী-এর আলফুতূহাতুল মাক্কিয়্যাহ এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের শ্রেষ্ট গ্রন্থটির মাঝে তুলনা করে দেখুন; প্রথমটির তত্ত্ব ও তথ্যের বিপুলতায় এবং বিষয়বস্তুর প্রতি সযত্ন প্রয়াস ও আত্মনিবেদনের গভীরতায় আপনি হতবাক হয়ে যাবেন এবং তা থেকেই বুঝে যাবেন, প্রাচ্যের রুচি, ঝোঁক ও প্রবণতা মূলত কী ছিলো!
শিরক ও বিদ‘আতের ছড়াছড়িমুসলিম উম্মাহর অবক্ষয় ও অধঃপতনের এ চরম সময়কালে বিভিন্ন প্রকার শিরক ও বিদ‘আত এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, আকল হতবাক হয়ে যায়! বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয়, এ উম্মাহ হযরত ইবরাহীমের অনুসারী তাওহীদবাদী উম্মাহ, যার নাম তিনি রেখেছেন মুসলিম উম্মাহ। শিরক ও বিদ‘আত এবং মূর্খতা ও গোমরাহীর ঘোর অন্ধকারে ইসলামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাওহীদ প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো এবং জাহিলিয়াতের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি, চিন্তা-চেতনা ও কুসংস্কার মুসলিম জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছিলো এবং শিকড় গেড়ে বসেছিলো। এভাবে বলা যায়, সমাজজীবন ও ধর্মীয় জীবনের এক বিরাট অংশ জাহিলিয়াতের কবলে চলে গিয়েছিলো এবং মুসলিম জাতি সঠিক দ্বীন থেকে যেমন বিচ্যুত ছিলো তেমনি বাস্তব দুনিয়া থেকেও পড়েছিলো। অথচ বিশ্বের জাতিবর্গের মাঝে মুসলিম উম্মাহর যা কিছু বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব তার মূল হচ্ছে এই আসমানী দ্বীন যা আল্লাহর নবী মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন এবং উম্মাহর কাছে আমানত রেখে গেছেন। আর মৌলিকতা, নির্ভুলতা, নির্ভেজালতা ও সংরক্ষণীয়তাই হলো এই দ্বীনের একক বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিকত্ব। এই দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর অহী, যা চিরসংরাক্ষিত-
‘আমিই নাযিল করেছি এই যিকির এবং অবশ্যই আমিই তার হিফাযাতকারী।’