বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
শিশু-কিশোর ও নবীনদের পত্রিকা
মাসিক আল-কলম-পুষ্প
সম্পাদক: আবু তাহের মিসবাহ
( এবং পুষ্পের লেখকবন্ধুরা )
[ একটি দারুল কলম প্রকাশনা ]
(মা যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমীন- ধারাবাহিক অনুবাদ)
মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হল?
পূর্বপ্রকাশিতের পর...
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: জাহেলিয়াতের কাঁচামাল থেকে মানবতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ
এই সুব্যাপ্ত ও সুগভীর ঈমান, এই মহাপ্রজ্ঞাপূর্ণ নববী শিক্ষা ও দীক্ষা এবং এই অলৌকিক গ্রন্থ আলকোরআন- যা চিরসজীব, যার বিস্ময় অনিঃশেষ- এবং অতুলনীয় ছোহবত ও সাহচর্য, এগুলোর মাধ্যমে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু মানবতাকে নতুন প্রাণ ও নতুন জীবন দান করলেন। মানবতার যে বিপুল অব্যবহৃত কাঁচা সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছিলো এবং কারোই জানা ছিলো না, এগুলোর গুণ কী এবং সঠিক ব্যবহারক্ষেত্র কোনটি, বরং জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশায় সব হারিয়ে যাচ্ছিলো, তিনি সেই কাঁচা মানবসম্পদে নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন; সুপ্ত সকল প্রতিভা জাগ্রত করলেন এবং চাপা পড়া যোগ্যতার বিকাশ ঘটালেন। প্রতিটি প্রতিভা ও যোগ্যতাকে তিনি যথাস্থানে নিয়োজিত করলেন। তখন মনে হলো জীবনের শূন্য ক্ষেত্রগুলো এত দিন এই সব প্রতিভা ও যোগ্যতারই অপেক্ষায় ছিলো। সব যেন প্রস্তর- মূর্তির মত নিষ্প্রাণ ছিলো, আর তিনি সেগুলোকে জীবন্ত মানবে রূপান্তরিত করলেন, কিংবা সব যেন মৃতদেহ ছিলো, আর তাঁর প্রাণস্পর্শে সেগুলো প্রাণ লাভ করলো এবং সমাজকে জীবনের বার্তা শোনতে লাগলো। যারা নিজেরাই ছিলো অন্ধ এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত, এখন তারাই মনবতাকে আলো দিয়ে পথ দেখাতে লাগলো। কোরআনের ভাষায়- ‘যারা মৃত ছিলো, অনন্তর তাদেরকে আমি জীবন দান করলাম এবং তাদেরকে নূর দান করলাম, যার দ্বারা তারা মানব- সমাজে পথ চলতে লাগলো, তারা কি হতে পারে ঐ ব্যক্তির মত যে হারিয়ে গেছে বিভিন্ন অন্ধকারে, আর তা থেকে বের হতেই পারছে না!’
তাঁর নূরানী ছোহবত ও জ্যোতির্ময় সাহচর্য এবং হাকীমানা তারবিয়াত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার গুণে ধ্বংসের কিনারায় উপনীত জাতির মাঝে এমন এক বিপ্লব সৃষ্টি হলো যে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এমন সব ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হলো যারা সত্যিকার অর্থেই ছিলেন মানবতার বিস্ময় এবং ইতিহাসের অনন্য সম্পদ।
ওমর (রা), যিনি পিতা খাত্তাবের বকরি চরাতেন, আর তিনি তাঁকে অকর্মন্য বলে তিরস্কার করতেন, শক্তি ও সম্মন এবং মর্যাদা ও আভিজাত্যে যিনি কোরায়শের মধ্যম মানের ছিলেন, সমাজে ও সমবয়সীদের মাঝে যার আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য ছিলো না, সেই সাধারণ একজন ওমর হঠাৎ সারা বিশ্বকে আপন প্রতিভা, যোগ্যতা, গুণ ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন, কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্য তছনছ করে তাদের রাজমুকুট ছিনিয়ে আনছেন এবং এমন এক ইসলামী সালতানাত গড়ে তুলছেন যা যুগপৎ উভয় সাম্রাজ্যের উপর বিস্তৃত, অথচ সুশাসনে ও সুব্যবস্থায় উভয় সাম্রাজ্যের উর্ধ্বে যার অবস্থান। পক্ষান্তরে তাকওয়া ও ধার্মিকতা এবং ইনছাফ ও সুবিচারের ক্ষেত্রে তো তুলনার কোন প্রশ্নই আসে না; এমনকি ছাহাবা কেরামের মাঝেও এসব বিষয়ে তিনি ছিলেন অনন্য।
খালিদ বিন ওলীদের কথা ধরুন; তিনি কী ছিলেন?! খুব বেশী হলে কোরায়শের উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের একজন, স্থানীয় ও গোত্রীয় যুদ্ধে তার খ্যাতি ছিলো। সেই সুবাদে গোত্রপতিদের কাছে ছিলো তার আলাদা কদর, কিন্তু গোত্রীয় গণ্ডি পেরিয়ে আরব উপদ্বীপেও তার বিশেষ কোন পরিচিতি ছিলো না, সেই সাধারণ এক যোদ্ধা খালেদ বিন ওয়ালীদ ‘আসমানি তলোয়ার’ হয়ে এমন ঝলসে উঠলেন যে, যা সামনে আসে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই খোদায়ি তলোয়ার রোম সাম্রাজ্যের উপর বিজলী হয়ে এমন চমকালো যে, ইতিহাসের দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ছড়িয়ে থাকলো শুধু তারই খ্যাতি ও সুখ্যাতি ।
আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, যার সততা, বিশ্বস্ততা ও কোমলতার প্রসংশা ছিলো, ছিলো ক্ষুদ্র কিছু বাহিনী পরিচালনার অভিজ্ঞতা, হঠাৎ তিনি হয়ে গেলেন আমীনুল উম্মাহ! উম্মতের বিশ্বস্ততম ব্যক্তি! মুসলমানদের বৃহত্তম বাহিনী পরিচালনার গুরু দায়িত্ব অর্পিত হলো তার উপর, আর তিনি এমন বিস্ময়কর যোগ্যতার সাথে বাহিনী পরিচালনা করলেন যে, রোমকবাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো! এমনকি সমগ্র সিরিয়ায় রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো, আর বিদায়কালে রোম- সম্রাট সিরিয়ার উপর অসহায় দৃষ্টি বুলিয়ে বলে উঠেন, হে সিরিয়া, তোমাকে বিদায় সালাম, এমন বিদায় যার পর নেই কোন মিলন।
আমর ইবনুল আছ, যিনি ছিলেন কোরায়শের বুদ্ধিমানদের একজন। কিন্তু তার কীর্তি ছিলো শুধু এই, কোরায়শ তাকে হাবশার রাজদরবারে দূতরূপে পাঠিয়েছিলো হিজরতকারী মুসলমানদের ফেরত আনাতে, কিন্তু তাকে ফিরে আসতে হয়েছিলো ব্যর্থ হয়ে; সেই তিনি ইসলাম গ্রহণের পর হলেন ফাতিহে মিছর- মিশরবিজয়ী এবং অখণ্ড ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী।
সা‘আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ, ইসলামপূর্ব জীবনে যার বড় কোন যুদ্ধের খবর কেউ জানে না, তিনি হলেন কাদেসিয়ার বিজয়ী বীর। মাদায়েনের চাবি অর্পিত হলো তার হাতে। ইরাক ও ইরানকে ইসলামী সালতানাতের সবুজ মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করে পেলেন ‘ফাতিহে আজম’- এই অমর ও অনন্য উপাধি।
সালমান ফারসী, যিনি ছিলেন পারস্যের কোন ব্যস্তির ধর্মীয় নেতার পুত্র। নিজের এলাকার বাইরে যার কোন পরিচিতি ছিলো না। তিনি পারস্য থেকে বের হলেন। দাসত্বের পর দাসত্ব এবং বিপদের পর বিপদ বরণ করে অবশেষে মদীনায় উপনীত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন, আর স্বদেশভূমি পারস্যের রাজধানী মাদায়েনের আমীর ও প্রশাসক হলেন! কালকের সাধারণ এক প্রজা, আজ হলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী শাসক! তার চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এমন শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়েও তার তাকওয়া ও ধার্মিকতায় এবং নির্মোহতা ও অনাড়ম্বরতায় আসেনি সামান্যতম পরিবর্তন! পারস্যের বিমুগ্ধ মানুষ অবাক হয়ে দেখে, তাদের শাসক ঝুপড়িতে বাস করেন এবং বোঝা মাথায় বাজারে যান।
হাবশী দাস বেলাল, যার কোন মূল্য ছিলো না এমনকি বেচাকেনার বাজারেও, গুণ ও যোগ্যতায় এবং সততা ও ধার্মিকতায় তিনি এমন উচ্চ স্তরে উপনীত হলেন যে, আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব পর্যন্ত তাঁকে বলতেন, সাইয়িদুনা বিলাল!
আবু হোযায়ফা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম, আরব জাহিলিয়াতে যার আলাদা কোন পরিচয় ছিলো না, ইসলাম তাকে এমনই অত্যুচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলো যে, খলীফা ওমর (রা) তাকে খেলাফতের গুরু দায়িত্ব বহনেরও উপযুক্ত মনে করেছেন। তিনি বলেছিলেন, আবু হোযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম যদি বেঁচে থাকতো, তাকে আমার স্থলবর্তী করে যেতাম।
যায়দ ইবনে হারিছা, যিনি লুণ্ঠিত কাফেলা থেকে দাসবাজারে গিয়ে বিক্রি হয়েছিলেন, মুতার যুদ্ধে তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি, যে বাহিনীতে ছিলেন জা‘ফর বিন আবু তালিব এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদের মত অভিজাত কোরায়শবীর; আর তাঁর পুত্র উসামা ছিলেন সেই বাহিনীর প্রধান যাতে ছিলেন আবু বকর ও ওমর (রা)-এর মত ছাহাবী।
আবু যর, আলমিকদাদ, আবুদ্-দারদা, আম্মার বিন ইয়াসির, মু‘আয বিন জাবাল ও উবাই ইবনে কা‘আব- জাহেলী যুগের এই সাধারণ মানুষগুলোর উপর দিয়ে যখন ইসলামের সুরভিত বায়ু প্রবাহিত হলো, তারা হয়ে গেলেন যুহদ ও তাকওয়ার আদর্শ এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।
আলী ইবনে আবু তালিব, আয়েশা বিনতে আবু বকর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, যায়দ ইবেন ছাবিত ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস- উম্মী নবীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়ে এাঁরা প্রত্যেকে হয়ে গেলেন মুসলিম উম্মাহর এমন জ্ঞানপ্রদীপ যার আলোতে উদ্ভাসিত হলো সারা বিশ্ব। তাঁদের কলব থেকে প্রবাহিত হলো ইলমের এমন ঝর্ণাধারা এবং তাদের যবান থেকে নিঃসৃত হলো হিকমত ও প্রজ্ঞার এমন অমীয় বাণী, যার তুলনা হতে পারে শুধু যমযমের ঝর্ণধারা।
তারা এবং অন্যসকল ছাহাবা- এককথায় তাদের পরিচয় হলো, হৃদয়ের দিক থেকে মানবসমাজে পবিত্রম, ইলম ও প্রজ্ঞার দিক থেকে গভীরতম এবং লৌকিকতার দিক থেকে সহজতম। তারা যখন কথা বলতেন, যামানা নিশ্চুপ হয়ে তাদের কথা শুনতো এবং ইতিহাসের কলম তা লিখে রাখতো।
ভারসাম্যপূর্ণ মানবগোষ্ঠী
দেখতে দেখতে সবকিছু বিস্ময়কর ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেলো! জাহেলিয়াতের এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই যে ‘মানবকাঁচাপণ্য’, সমসাময়িক জাতি যাদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতো এবং প্রতিবেশী দেশ যাদের অবজ্ঞা করতো হঠাৎ করেই তারা দেখতে পেলো সেই তুচ্ছ কাঁচা পণ্য থেকে তৈরী হয়ে গেছে এমন মহামূল্যবান মানব- সম্পদ যার চেয়ে উত্তম কিছু সভ্যতার ইতিহাসে কখনো ছিলো না, কখনো হবে না। যেমন সুষম ও সুসংহত তেমনি সুবিন্যস্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ, যেন গোল আঙটা, যার প্রান্ত বোঝা যায় না, কিংবা যেন একপশলা বৃষ্টি, যার শুরুতে বেশী কল্যাণ না শেষে, বলা যায় না। এমন এক মানবগোষ্ঠী, যা মানবীয় প্রয়োজনের সকল দিকে পরিপূর্ণ ও সুসম্পূর্ণ। কোথাও কোন খুঁত নেই এবং কমবেশী করার সুযোগ নেই। বিশ্বের কাছে তাদের নেই কোন প্রয়োজন, অথচ তাদের কাছে বিশ্বের আছে প্রয়োজন এবং তা সর্ববিষয়ে।
এই নতুন মানবগোষ্ঠী পৃথিবীতে এক নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করলো এবং নতুন রাষ্ট্র ও শাসন- ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করলো, অথচ আধুনিক সভ্যতা ও রাষ্ট্র- ব্যবস্থার সাথে তাদের কোন পরিচয়ই ছিলো না। তবু কোন জাতির কাছ তাদের মানুষ ধার করতে হয়নি এবং কোন রাজ্য ও সরকার থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে হয়নি। সম্পূর্ণ আত্মশক্তি ও আত্মযোগ্যতায় তারা এমন এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন যা বিস্তৃত ছিলো দুই মহাদেশের বিশাল এলাকায়। প্রতিটি স্থান ও অবস্থান এবং প্রতিটি আসন ও উপবেশন এমন সব মানুষ দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছিলো যারা যোগ্যতা ও ধার্মিকতা এবং শক্তি ও সততার মাঝে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছিলেন।
এই বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর স্বভাবতই তা রক্ষা ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিলো সর্বোচ্চ যোগ্যতার অসংখ্য মানুষের। অথচ উম্মাহর তখন মাত্র আবির্ভাবকাল; কয়েকটি দশক মাত্র তার বয়স এবং সেটাও পার হয়েছে শুধু প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা এবং জিহাদ ও সংগ্রামের মাঝে। কিন্তু বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলো নবআবির্ভূত উম্মাহ কীভাবে সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি স্তরে কেমন যোগ্যতম মানুষ সরবরাহ করেছে! যেমন আদর্শ শাসক ও প্রশাসক, তেমনি সুদক্ষ পরিচালক ও ব্যবস্থাপক; যেমন বিশ্বস্ত কোষাগার ও হিসাব রক্ষক তেমনি ন্যায়পরায়ন বিচারক, সুদক্ষ সেনাপতি ও একনিষ্ঠ সৈনিক। সর্বোপরি ধার্মিকতা ও সাধুতায় এবং সরলতা ও উদারতায় অতুলনীয়। সর্ববিষয়ে অন্তরে তাদের আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর কাছে জবাবদেহির চিন্তা।
যেহেতু দ্বীনী তারবিয়াত ও ইসলামী দাওয়াতের ধারা অব্যাহত ছিলো সেহেতু সদাপ্রবাহমান ঝর্ণার মত উম্মাহ তার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনযন্ত্রকে যোগ্য, দক্ষ, দায়িত্ববান ও নিবেদিতপ্রাণ এবং মুত্তাকী ও ধর্মাপ্রাণ কর্মী ও কর্মকর্তা সরবরাহ করে যেতে পেরেছে। কখনোই উম্মাহ যোগ্যতা, দক্ষতা, মেধা, প্রতিভা, সততা ও ধার্মিকতার সংকটে পড়েনি। শাসনক্ষমতা সবসময় তাদেরই হাতে ছিলো যারা বিশ্বাস করতেন যে, এ ক্ষমতা কর ও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নয়, বরং মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথে হিদায়াত করার জন্য। ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে সবসময় যারা সততা ও যোগ্যতার একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ফলে ইসলামী সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে এবং সমাজ ও মানুষের ধর্মীয় জীবন ঐ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ উদ্ভাসিত হতে পেরেছে যা মানব জাতির ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে ঘটেনি।
বস্তুত এত অল্প সময়ে এমন অসাধ্য সাধন হতে পেরেছে শুধু এজন্য যে, আল্লাহর নবী মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবস্বভাবের বদ্ধ তালা খোলার জন্য সঠিক চাবিটি ব্যবহার করেছিলেন। ফলে প্রথম প্রচেষ্টাতেই তা খুলে গিয়েছিলো এবং মানবস্বভাবের লুকায়িত সকল সম্পদ ও শক্তি, গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিভা ও সম্ভাবনা দুনিয়ার সামনে চলে এসেছিলো। জাহেলিয়াতের মর্মমূলে তিনি সঠিকভাবে আঘাত হেনেছিলেন এবং প্রথম আঘাতেই তা ধরাশায়ী হয়েছিলো। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিতে তিনি অবাধ্য বিশ্বকে নতুন দিকে এবং সহজ সরল পথে চলতে বাধ্য করেছিলেন, যাতে মানব- জাতি তার সৌভাগ্যের নতুন যুগের শুভ উদ্বোধন করতে পারে, আর তা হলো ইসলামী সভ্যতার সেই স্বর্ণালী যুগ, যা মানবতার ললাটে একমাত্র শুভ্র তিলকরূপে এখনো জ্বলজ্বল করছে।
তৃতীয় অধ্যায়: মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের যুগ
প্রথম পরিচ্ছেদ: মুসলিম শাসকদের বৈশিষ্ট্য
উপরে বর্ণিত সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে মুসলিম উম্মাহ যখন আত্মপ্রকাশ করলো তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের শাসন ও নেতৃত্বের ভার তাদেরই হাতে অর্পিত হলো এবং জরাগ্রস্ত জাতিসমূহ নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত হলো। কারণ তারা শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলো এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে যুলুম-অত্যাচার এবং অনাচার ও স্বেচ্ছাচারের বাহন বানিয়েছিলো। আর জাতি ও সভ্যতার ইতিহাসের শুরু থেকেই আসমানের বিধান হলো, জরাগ্রস্ত জাতিকে নেতৃত্বের আসন থেকে ছুঁড়ে ফেলা এবং উদিয়মান জাতিকে তাদের স্থলবর্তী করা। তো আসমানী বিধানের অমোঘ পরিণতিরূপে মুসলিম উম্মাহ যখন বিশ্বনেতৃত্বের আসনে সমাসীন হলো তখন মানবজাতিকে সে ন্যায় ও সত্যের পথে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ গতিতে পরিচালিত করলো। ঐ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত ছিলো যা একটি জাতিকে বিশ্বজাতির নেতৃত্বের যোগ্যতা দান করে এবং যাদের পরিচালনা ও ছত্রচ্ছায়ায় বিশ্বের সুখ-শান্তি, সফলতা ও সৌভাগ্য সুনিশ্চিত হয়। কী ছিলো সেই গুণ ও যোগ্যতা?
প্রথমত তারা ছিলো আসমানী কিতাব ও আসমানী শরীয়াতের অধিকারী। তাই তাদের নিজেদের আইন ও বিধান তৈরী করার প্রশ্ন ছিলো না। ফলে চলমান অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতির তাগিদে আইন ও বিধানের অব্যাহত রদবদল এবং অনিবার্য ভ্রান্তি, বিচ্যূতি ও বিপর্যয় থেকে তারা নিরাপদ ছিলো, যা মানবরচিত যে কোন আইনের ক্ষেত্রে অবধারিত হয়ে থাকে। তারা তাদের আচরণ ও বিচরণ এবং শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্ধকারে অন্ধ পথিকের মত ছিলো না। তাদের কাছে ছিলো আল্লাহপ্রদত্ত সেই চিরসমুজ্জ্বল আলো, যা জীবনের সকল পথ ও পথের বাঁক আলোকিত করে রেখেছিলো। ফলে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিলো আলোর সাহায্যে আলোরই মাঝে। তাদের চলার পথ যেমন ছিলো উদ্ভাসিত তেমনি তাদের গন্তব্য ছিলো সুস্পষ্ট। আলকোরআনের ভাষায়-
‘যারা মৃত ছিলো, অনন্তর আমি তাদের জীবন দান করেছি এবং তাদের জন্য নির্ধারণ করেছি নূর, যার সাহায্যে তারা চলে মানুষের মাঝে, তারা কি হতে পারে ঐ ব্যক্তির মত যে নিমজ্জিত বিভিন্ন অন্ধকারে, যা থেকে সে বের হতে পারে না!’
মানুষকে শাসন এবং মানুষের মাঝে সুবিচার করার জন্য তাদের কাছে ছিলো আসমানী শরীয়াত ও জীবনবিধান। আল্লাহ তাদেরকে বানিয়েছিলেন হক ও ইনছাফের ধারক এবং ন্যায় ও সত্যের বাহক। তাই চরম ক্রোধ ও অসন্তোষের মুহূর্তে এবং শত্রুতা ও বিদ্বেষের চূড়ান্ত মানবীয় দুর্বলতার সময়ও ন্যায় ও সুবিচার থেকে তারা তিলপরিমাণ বিচ্যুত হতো না এবং প্রতিশোধের পাশবিকতায় গা ভাসিয়ে দিতো না। তাদের প্রতি আল্লাহ নির্দেশ ছিলো এবং সে নির্দেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালনও করতো-
‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি অবিচল থাকো (এবং) ন্যয়পরতার সাথে সাক্ষ্যদানকারী হও। আর কোন দলের প্রতি শত্রুতা যেন ইনছাফ না করার অপরাধে তোমাদের লিপ্ত না করে। (বরং) তোমরা ইনছাফ করো। (কারণ) সেটাই হলো তাকওয়া (ও আল্লাহভীতির) অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।
দ্বিতীয়ত তারা শাসন ও নেতৃত্বের গুরুভার গ্রহণ করেছিলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তারবিয়াত ও সংশোধনের মাধ্যমে যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করার পর। পক্ষান্তরে অন্যান্য জাতি শাসন- ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলো নৈতিক ও চারিত্রিক এবং আত্মিক ও আধ্যাত্মিক কোন রকম তারবিয়াত ও সংশোধন ছাড়া। ফলে ন্যয় ও কল্যাণের উৎস হওয়ার পরিবর্তে পৃথিবীর জন্য তারা হয়ে পড়েছিলো মন্দ ও অকল্যাণ এবং দুষকৃতি ও ফাসাদের প্রজননক্ষেত্র। এটা অতীতের সমাজপতি, সেনাপতি, ‘রাষ্ট্রপতি’ ও শাসক-প্রশাসকদের ক্ষেত্রে যেমন সত্য ছিলো, তেমনি সত্য বর্তমানের ক্ষেত্রেও। কিন্তু ছাহাবা কেরামের বিষয়টি ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর দীর্ঘ একটা সময় আল্লাহর নবী মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাকীমানা তারবিয়াত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের নাফসের তাযকিয়া এবং হৃদয় ও আত্মার সংশোধন করেছেন এবং নির্মোহতা, ধার্মিকতা, নৈতিক পবিত্রতা, সততা, সত্যবাদিতা, আত্মত্যাগ ও আল্লাহভীতির উপর তাদের গড়ে তুলেছেন। শাসনক্ষমতার লোভ ও নেতৃত্বের মোহ তাদের অন্তর থেকে বিলুপ্ত করেছেন। তিনি বলতেন-
আল্লাহর কসম, এই শাসনক্ষমতা আমি তাকে দেবো না যে দাবী করে, বা লোভ করে।
তাছাড়া এই আয়াত বারবার তাদের কানে পড়েছে এবং হৃদয়ের গভীরে এর মর্মবাণী বদ্ধমূল হয়েছে-
ঐ আখেরাত আমি তাদেরই জন্য নির্ধারণ করবো যারা যমিনে বড়ত্ব অর্জন করতে চায় না এবং ছড়াতে চায় না ফাসাদ। আর সুপরিণতি রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।
এই নববী তারবিয়াতের ফল হলো এই যে, পদ ও সম্পদ এবং ক্ষমতা ও নেতৃত্বের মোহ তাদের অন্তরে আর বাকি ছিলো না, মানুষ যেমন এগুলোর মোহে ছুটে যায় আগুনের দিকে পতঙ্গের ছুটে যাওয়ার মত। বরং অন্যকে ঠেলে দিয়ে তারা নিজেরা পিছিয়ে থাকতেন এবং সভয়ে তা এড়িয়ে যেতে চাইতেন, নিজে প্রার্থী হওয়া এবং দৌড়ঝাঁপ ও চেষ্টা-তদ্বীর করা তো দূরের কথা। অনন্যোপায় হয়ে কখনো কোন পদ বা ক্ষমতা গ্রহণ করলে সেটাকে তারা দুধেল গাভী ও গাছপাকা ফল ভাবতেন না, বরং অর্পিত কঠিন আমানত এবং আল্লাহর পক্ষ হতে বিরাট পরীক্ষা মনে করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন, এজন্য একদিন আল্লাহর সামনে তাদের দাঁড়াতে হবে এবং ছোট-বড় সব বিষয়ের পুঙ্খানুপঙ্খ হিসাব দিতে হবে। এ আয়াত তারা সবসময় স্মরণ করতেন-
অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন যেন তোমরা আমানতসমূহ সেগুলোর হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করো, যেন ইনছাফের সাথে বিচার করো।
তারা স্মরণ করতেন এই আয়াত-
তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলবর্তী বানিয়েছেন এবং তোমাদের কাউকে কারো উপর বিভিন্ন মর্যাদা দান করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন ঐ সকল বিষয়ে যা তিনি তোমাদের দান করেছেন।
তৃতীয়ত তারা বিশেষ কোন শ্রেণী ও গোষ্ঠী এবং বিশেষ কোন দেশ ও অঞ্চলের সেবক বা প্রতিনিধি ছিলেন না, যারা শুধু ঐ শ্রেণী ও গোষ্ঠীর কল্যাণচিন্তা করবে এবং শুধু ঐ দেশ বা অঞ্চলের স্বার্থ রক্ষা করবে; কিংবা বিশেষ কোন সমপ্রদায় বা দেশের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করবে। তারা কখনো এমন ধারণা দ্বারা আক্রান্ত হননি যে, শাসক হওয়ার জন্য তাদের সৃষ্টি, আর
অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি শাষিত বা শোষিত হওয়ার জন্য। তারা জানতেন, বিশ্বমঞ্চে তাদের আবির্ভাব এজন্য নয় যে, তারা আরবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তার ছত্রচ্ছায়ায় ভোগ-উপভোগ ও স্বেচ্ছাচার করে বেড়াবেন, আর পৃথিবীতে আরব- রক্তের গর্ব ও দম্ভ প্রচার করে বেড়াবেন। ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে তাদের অভিযান এজন্য নয় যে, মানবসমপ্রদায়কে রোম ও পারস্যের দাসত্ব থেকে বের করে আরবদের গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করবেন। তাদের অভিযান তো ছিলো মানবকে মানবের দাসত্ব থেকে বের করে এক আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত করার জন্য। যেমন ইরানের রাজদরবারে মুসলিম দূত হযরত রাবঈ বিন আমির বলেছিলেন-
‘আল্লাহ আমাদের প্রেরণ করেছেন যেন মানুষকে আমরা মুক্ত করি বান্দার ‘ইবাদত’ থেকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং সকল ধর্মের যুলুম-অনাচার থেকে ইসলামের সত্য ও ন্যয়ের দিকে।’
তাদের দৃষ্টিতে দেশ-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবসমপ্রদায় ছিলো অভিন্ন এক জাতি। মানুষে মানুষে কোন কোন ভেদ নেই, সকলে সমান, সকলে আদম-
সন্তান, আর আদম হলেন মাটির তৈরী। আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আজমের উপর এবং আজমের কোন কৌলীন্য নেই আরবের উপর, তবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। আলকোরআনের এ আয়াতের উপর ছিলো তাদের অবিচল বিশ্বাস - (তরজমা)
হে লোকসকল! নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী হতে এবং তোমাদের ভাগ করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ সম্মানী সে-ই যে তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ মোত্তাকী।
সেই সোনালী যুগের একটি অনন্য ঘটনা ইতিহাস আজো সংরক্ষণ করে রেখেছে। মিসরের শাসক হযরত আমর ইবনুল আছ (রা)-এর এক পুত্র কোন এক ঘটনায় জনৈক মিসরীয় কিবতীকে চাবুক মেরেছিলো বংশকোলীন্যের গর্ব করে একথা বলে- নাও, কুলীন ও অভিজাতবর্গের সন্তানের পক্ষ হতে চাবুকের স্বাদ গ্রহণ করো।
অভিযোগ নিয়ে সেই কিবতী মিসর থেকে সোজা মদীনায় খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)এর দরবারে হাযির হলো, আর তিনি কিছাছের হুকুম দিয়ে বললেন- কখন থেকে মানুষকে তোমরা গোলাম বানাতে শুরু করলে, অথচ মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন অবস্থায় জন্ম দিয়েছিলো।
তো এই মহান ব্যক্তিগণ, তাদের নিকট দ্বীন ও ইলমের যে সম্পদ ছিলো তা বিতরণের ক্ষেত্রে কোন কৃপণতা করেননি এবং দেশ, ভাষা, বর্ণ ও বংশের কোন পার্থক্য করেননি, তেমনি শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও মানুষে মানুষে তাদের কাছে কোন ফরক-তমিয ছিলো না। মানবজাতির জন্য তারা যেন ছিলেন সেই ‘করুণবৃষ্টি’ যা সর্বত্র বর্ষিত হয় এবং সর্বজনে সিক্ত করে। যে মেঘ-বৃষ্টিকে পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ড স্বাগত জানায় এবং স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে তা থেকে কল্যাণ ও উর্বরতা গ্রহণ করে। এই সকল ‘মেঘমানবের’ শীতল ছায়ায় এবং তাদের কল্যাণশাসনের ছত্রচ্ছায়ায় পৃথিবীর সকল জাতি ও মানবগোষ্ঠী, এমনকি প্রাচীন কাল থেকে যারা শুধু যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে এসেছে, তারা সকলে নিজেদেরকে এবং বিশ্বকে গড়ার মহান কর্মযজ্ঞে শরীকদার হতে পেরেছিলো। ইলমচর্চা ও জ্ঞান- সাধনা এবং ধর্ম-কর্ম ও শাসন- পরিচালনা, সবকিছুতে তারা আরবদের সমান অংশীদার হতে পেরেছিলো, বরং কোন কোন গুণ ও বৈশিষ্ট্যে এবং প্রতিভা ও যোগ্যতায় অনেকে আরবদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো এবং আরবরা তাদের সাদরে বরণ করে নিয়েছিলো। তাদের মধ্য এমন এমন ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও মুফাস্সির আত্মপ্রকাশ করেছিলেন যারা ছিলেন আরবদেরও মাথার মুকুট এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ গর্ব ও গৌরবের পাত্র। এমনকি ইবনে খালদূনের ভাষায়-
‘বিস্ময়কর বাস্তবতা এই যে, ইসলামী উম্মাহর ইলমের ধারক ও জ্ঞানসাধকদের অধিকাংশই হলেন আজমী, অনারব; আর তা দ্বীন ও শরীয়াতের ইলম এবং যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই। এর ব্যতিক্রম খুবই বিরল। এমনকি কেউ কেউ নসব ও বংশপরিচয়ে আরব হলেও ভাষায় অনারব, অন্তত শিক্ষাদীক্ষায় এবং শিক্ষকসূত্রে অনারব। (অর্থাৎ আরব হয়েও জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা তারা গ্রহণ করেছেন অনারব শায়খ থেকে।) অথচ মিল্লাত ও মাযহাব ছিলো আরবীয় এবং শরীয়তের বাহক ছিলেন আরব।)
পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও অনারব মুসলিম জনগোষ্ঠীতে এমন এমন শাসক ও প্রশাসক, সিপাহি ও সিপাহসালার, উযির ও নাযিম, জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধজন এবং আলিম-ওলামা ও আইম্মা-মাশায়েখের আবির্ভাব ঘটেছে, সত্যিকার অর্থেই যারা ছিলেন মানবতার অলংকার এবং মানবজাতির ভূষণ। জ্ঞানে-গুণে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যে, ধার্মিকতা ও নৈতিকতায় এবং যোগ্যতা ও প্রতিভায় তারা ছিলেন উজ্জ্বলতম একেকটি নক্ষত্র এবং তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।
চতুর্থত মানুষ হচ্ছে দেহ ও আত্মা এবং হৃদয় ও বুদ্ধি এবং আবেগ ও রক্তের সমন্বিত অস্তিত্ব। সুতরাং মানুষ প্রকৃত সুখ-শান্তি ও সৌভাগ্য এবং জীবনের সফলতা ও সার্থকতা ততক্ষণ অর্জন করতে পারে না এবং মানবজাতি ও মানবতা ততক্ষণ ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না মানুষের এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি ও যোগ্যতা সুসমন্বিতরূপে এবং যথাযথভাবে বিকশিত ও প্রতিপালিত না হবে। পৃথিবীতে একটি আদর্শ ও কল্যাণকর সভ্যতার অস্তিত্ব ততক্ষণ কল্পনা করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না এমন একটি ধর্মীয়, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈষয়িক পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে যেখানে সহজে ও স্বতঃস্ফূর্ত- ভাবে যে কারো পক্ষে মানবীয় পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করা সম্ভব হয়। আর সভ্যতার পথে মানবজাতির সুদীর্ঘ প্রয়াস-প্রচেষ্টা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা এটা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করেছে যে, আদর্শ সভ্যতার এ সুন্দর স্বপ্নের বাস্তিবায়ন কখনোই সম্ভব নয়, যদি না জীবনের নিয়ন্ত্রণভার এবং সভ্যতার গতিনির্ধারণের ক্ষমতা এমন লোকদের হাতে থাকে যারা আত্মা ও জড়তা এবং হৃদয় ও বুদ্ধির অবিচ্ছেদ্যতায় বিশ্বাস রাখে, যারা ধর্মীয়, নৈতিক ও জাগতিক জীবনের আদর্শ উদাহরণ হতে পারে এবং যারা সুস্থ বুদ্ধি, জাগ্রত বিবেক এবং কল্যাণকর জ্ঞানের অধিকারী হবে। সুতরাং যদি তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় ও আকীদা-বিশ্বাসে এবং তারবিয়াত ও প্রতিপালনে কোন ত্রুটি থেকে যায় তাহলে অবধারিত ভাবে সেই ত্রুটি তাদের হাতে গড়ে ওঠা সভ্যতায়ও সংক্রমিত হবে, হতে বাধ্য এবং তার প্রতিক্রিয়া বিভিন্নরূপে ও বিচিত্র অভিপ্রকাশ ক্ষেত্রে প্রকটভাবে দেখা দেবে।
এভাবে যদি সভ্যতার পথযাত্রায় এমন মানবগোষ্ঠীর আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যারা শুধু জড়তার পূজায় বিশ্বাসী এবং শুধু স্থূল ভোগা-বিলাস ও জাগতিক লাভলোকসানের চিন্তায় বিভোর, যারা দৃশ্যমান জীবন ও জগত ছাড়া ঊর্ধ্বজাগতিক অন্য কিছুতে বিশ্বাসী নয়, যারা মনে করে, ভোগ-উপভোগের এই জড়জীবনের পর মানুষ মাটির সাথে মিশে যাবে এবং সবকিছু অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে, তো তাদের স্বভাব, মন-মানস ও চিন্তা-চেতনার প্রভাব অবধারিতভাবেই সভ্যতার আকৃতি ও প্রকৃতিতে পড়বে এবং সেই ছাঁচেই তা গড়ে ওঠবে ও বিকশিত হবে। ফলে মানবতার কিছু কিছু দিক যেমন পূর্ণতা লাভ করবে তেমনি কিছু কিছু দিক বিনষ্ট হবে। এই সভ্যতা হয়ত ইট-পাথরে, লোহা-তামায়, কাগজে-বস্ত্রে ও সোনায়-মুদ্রায় উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাবে এবং বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, সমর- কৌশলে ও যুদ্ধাস্ত্রে সময় থেকেও এগিয়ে যাবে এবং আনন্দবিনোদন ও পাপাচারের রূপবৈচিত্রে মানুষের কল্পনাকেও হার মানাবে, কিন্তু হৃদয় ও আত্মার জগত পরিণত হবে ঊষরমরুতে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা হয়ে পড়বে বিপর্যস্ত। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তান এবং ভাই-বোন ও বন্ধুর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে সুবিধা ও স্বার্থের টানে। এককথায় সেই সভ্যতা পরিণত হবে এমন ফোলা-ফাঁপা দেহে যা দেখতে হবে আকর্ষণীয়, কিন্তু স্বাস্থ্য ও সুস্থতা থেকে বঞ্চিত এবং তার হৃদয় হবে ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত।
পক্ষান্তরে সভ্যতার চালকের আসনে বসা সেই মানবগোষ্ঠী যদি জড় ও বস্তুকে অস্বীকার বা অবহেলা করে এবং শুধু হৃদয়, আত্মা ও ঊর্ধ্বজাগতিক বিষয়কেই গুরুত্ব প্রদান করে এবং জীবন ও জীবনের স্বাভাবিক চাহিদার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় তাহলে পরিণাম কী হবে? সভ্যতার বৃক্ষ সজীবতা হারিয়ে শুকিয়ে যাবে। মানুষের ভিতরের স্বভাবশক্তি ও সহজাত যাগ্যতা দুর্বল হয়ে ঝিমিয়ে পড়বে এবং এই স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক এই নেতৃত্বের প্রভাবে মানুষ জীবনের আলোকিত মঞ্চ থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেবে অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্বতে ও গুহার অন্ধকার নির্জনতায়। বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের পরিবর্তে তারা বরণ করবে কৌমার্যের ব্রত ও সাধনা এবং সেটাকেই মনে করবে মোক্ষ লাভের স্বর্ণদ্বার। আত্মাকে পবিত্র করার জন্য দেহের উপর তারা চালাবে এমন আত্মনির্যাতন যে, দেহের সকল ক্ষমতা ও সক্ষমতা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। এককথায় জীবনকে হরণ করে তারা মৃত্যুকে বরণ করে নেবে, যাতে তারা পৌঁছে যেতে পারে নোংরা জড়জগত থেকে আত্মার পুতপবিত্র জগতে, যেখানে ঘটবে তাদের প্রকৃত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। কারণ তাদের তো বিশ্বাস, জড়জগতের স্থূলতায় মানবশক্তির পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়। এই আত্মঘাতী চিন্তা- চেতনার ফল এছাড়া আর কী হতে পারে যে, সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটবে, নগর-শহর বিপর্যস্ত হবে এবং পুরো জীবনব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে!
যেহেতু এটা মানবের স্বভাব ও ফিতরতের সাথে সঙ্ঘর্ষপূর্ণ চিন্তা- ধারা সেহেতু তা গ্রহণযোগ্য হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উত্থান হবে অবশ্যম্ভাবী। মানুষের বাইরের জড়সত্তা ও ভিতরের পাশবিকতা এমনই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠবে যে, নীতি ও নৈতিকতা এবং আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি কোন দয়া-মায়া ও কোমলতার অবকাশ থাকবে না। এককথায় মানবতার ঘটবে অপমৃত্যু এবং পাশবিকতা ও হিংস্রতার হবে জয়জয়কার। কিংবা খুব কম করে যদি হয় তাহলে সন্ন্যাসপ্রবণ এই গোষ্ঠীর উপর জড়বাদী একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যে, প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণেই তারা তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হবে এবং পরাজয় শিকার করে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করবে। অথবা জীবন ও জগতের সমস্যার প্রতিকার করতে গিয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার কারণে সে নিজেই এগিয়ে গিয়ে জড়বাদী শক্তির সাথে সমঝোতা করতে চাইবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির দায়দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের তারা গুটিয়ে নেবে প্রথাগত ধর্মকর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষুদ্র বৃত্তে। এভাবে জীবন ও ধর্ম এবং দ্বীন ও যিন্দেগির বিচ্ছিন্নতা সামনে আসবে। নৈতিকতা ও আধ্যত্মিকতা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং জীবন থেকে তার ছায়া ক্রমে সংকোচিত হতে থাকবে, আর মানবসমাজে ও ব্যবহারিক জীবনে তার নিয়ন্ত্রণ একেবারে শিথিল হয়ে পড়বে এবং একসময় এগুলো হয়ে যাবে ভাবনা ও কল্পনার বিষয়, যা জীবনের অঙ্গন থেকে নির্বাসিত হয়ে আশ্রয় নেবে দর্শন ও মতবাদ হিসাবে বুদ্ধিজীবীদের গবেষণা- পত্রে। পৃথিবীর যে সকল জাতি ও জনগোষ্ঠী মানবজাতির ও মানব- সভ্যতার নেতৃত্ব দান করেছে তাদের মধ্যে খুব কমই এমন ছিলো যারা প্রান্তিকতার এই ভয়ানক দোষ ও বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ছিলো। হয় তারা ছিলো ভোগবিলাসে মত্ত আগাগোড়া জড়বাদের পূজারী, কিংবা জীবন ও তার চাহিদার প্রতি বীতশ্রদ্ধ নিছক আত্মার পূজারী ও সন্ন্যাসবাদী। একারণেই জীবন ও সভ্যতার তরী সবসময় ছিলো দোলায়মান। কখনো তা কাত হয়ে পড়তো জড়বাদিতার দিকে, কখনো সন্ন্যাসবাদের দিকে। সর্বাঙ্গীণতা ও ভারসাম্যপূর্ণতা বলতে গেলে ছিলো না।
পক্ষান্তরে ছাহাবা কেরামের বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তাঁরা ধার্মিকতা ও নৈতিকতা, নির্মোহতা ও জীবনবাদিতা, বস্তুশক্তি ও আত্মিক শক্তি এবং নীতি ও রাজনীতির মাঝে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছিলেন। সভ্যতার জন্য অপরিহার্য সকল দিক তাঁদের মাঝে বিদ্যমান ছিলো এবং মানবতার যে সকল গুণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো, কিংবা বিক্ষিপ্ত- ভাবে বিশ্বের নেতৃত্বদানকারী জাতিসমূহের মাঝে ছিলো সেগুলোর একত্র সমাবেশ ঘটেছিলো তাঁদের মাঝে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তারাই ছিলেন একমাত্র জনগোষ্ঠী যারা তাদের সুউন্নত নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক দীক্ষা এবং এ বিস্ময়কর ভারসাম্য যা কোন জাতির মাঝে কমই দেখা যায় এবং দেহ ও আত্মার স্বাভাবিক চাহিদার মাঝে এ অপূর্ব সমন্বয়, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কমই পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে পরিপূর্ণ জাগতিক ও বস্তুগত প্রস্তুতি এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির অনন্যসাধারণ ব্যাপ্তি- এই সবের কল্যাণে একমাত্র ছাহাবা কেরামের পক্ষেই সম্ভব ছিলো মানবজাতি ও মানবসভ্যতাকে সঙ্গে করে সফলতা ও সার্থকতা এবং সুখ ও সৌভাগ্যের পথে যাত্রা করা এবং আত্মিক, নৈতিক ও জড়জাগতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দেয়া। (ক্রমশ)
বাংলা ইউনিকোডে টাইপ করুন। যেমন: কুরআন, তাওহীদ ইত্যাদি
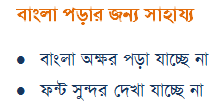
অন্যান্য লেখা
-
রবিউছ ছানী ১৪৪৫ হিঃ
ডাক দিয়ে যায় মুসাফির!- ৮ -
রবিউছ ছানী ১৪৪৫ হিঃ
কাশ্মীরে আলী মিয়াঁর বয়ান -
মুহাররম ১৪৪৫ হিঃ
ডাক দিয়ে যায় মুসাফির!- ৭ -
মুহাররম ১৪৪৫ হিঃ
পাকিস্তানে আলী মিয়াঁর বয়ান -
কাশ্মীরসংখ্যা
ডাক দিয়ে যায় মুসাফির! -
কাশ্মীরসংখ্যা
কাশ্মীরে হযরত আলী মিয়াঁর বয়ান -
কাশ্মীরসংখ্যা
মুসলিম উম্মাহর আজকের করণীয়১-২ -
জিলহজ্ব ১৪৪০ হিঃ (৩/৮)
ডাক দিয়ে যায় মুসাফির! -
জিলহজ্ব ১৪৪০ হিঃ (৩/৮)
আমাদের জন্য অনুকরণীয় -১-২-৩ -
জিলহজ্ব ১৪৪০ হিঃ (৩/৮)
পাকিস্তানে আলী মিয়াঁর বয়ান কোন স্বাধীন ভূখণ্ডে আলিম সমাজের দায়িত্ব ও যোগ্যতা -
রবিউল আউয়াল ১৪৪০হিঃ (৩/৭)
ডাক দিয়ে যায় মুসাফির! -
মুহররম.১৪৪০হিঃ (৩/৬)
ডাক দিয়ে যায় মুসাফির! -
মুহররম.১৪৪০হিঃ (৩/৬)
আমাদের জন্য অনুকরণীয় -
মুহররম.১৪৪০হিঃ (৩/৬)
মুসলিম উম্মাহর আজকের করণীয় -
মুহররম.১৪৪০হিঃ (৩/৬)
উম্মতে মুহাম্মাদিয়্যার সঠিক অবস্থান