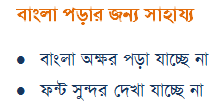হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী (রহ) রচিত মাযা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমীন-এর ধারাবাহিক অনুবাদ -১৪-
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ওছমানী খেলাফতের উত্থান
অষ্টম শতাব্দীর ঐ সঙ্কট- সন্ধিক্ষণে ইতিহাসের মঞ্চে একটি অপ্রতিহত শক্তিরূপে ওছমানিদের আবির্ভাব ঘটলো এবং তারা ইতিহাসের গতিধারার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলো। সাতশ তেপ্পান্ন হিজরীতে (১৪৫৩ খৃঃ) খলীফা মুহম্মদ ছানী বিশাল বাইজা- ন্টাইন সাম্রাজ্যের অপরাজেয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপল পদানত করলেন। তখন তার বয়স মাত্র চবিবশ বছর। এই অভাবিতপূর্ব বিজয়ের ফলে মুসলিম উম্মাহর নির্জীব দেহে নতুন করে আশা-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ইসলামও যেন নতুন গতি ও শক্তি লাভ করলো। মুসলিম উম্মাহর অন্তরে আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হলো যে, ওছমানী খেলাফাতের নেতৃত্বে তুর্কী জাতি বিশ্বের বুকে মুসলিম উম্মাহর হারানো শক্তি ও গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে, আর মুসলিম উম্মাহ বিশ্বনেতৃত্বের আসনে পুনঃসমাসীম হবে। সাহসে ও শৌর্যবীর্যে তুর্কীরা যেমন ছিলো অতুলনীয় তেমনি যুদ্ধাস্ত্র ও সমরকুশলতায় তাদের উদ্ভাবনী প্রতিভা ছিলো ঈর্ষণীয়। বস্ত্তত বাইজান্টাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল, যা সুদীর্ঘ আটশ বছর মুসলিমশক্তির সামনে ছিলো অপরাজেয়, তুর্কীরা তা পদানত করে তাদের যোগ্যতা ও শক্তিমত্তার বাস্তব প্রমাণও রেখেছিলো। ফলে সমকালীন বিশ্ব সর্বক্ষেত্রে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলো। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে জ্ঞান ও কর্মশক্তিকে তারা সর্বোচ্চরূপেই ব্যবহার করেছিলো, যা বিশ্বে কোন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের অপরিহার্য শর্ত।
সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ড্রপার মুহম্মদ আলফাতিহ-এর সমরকুশলতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন, ‘ গণিতশাস্ত্র (ও অন্যান্য জ্ঞানে) তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং যুদ্ধবিদ্যায় সেগুলোর সুপ্রয়োগ জানতেন। বস্ত্তত এ বিজয়ের জন্য তাঁর পূর্ণ প্রস্ত্ততি ছিলো এবং যুদ্ধের সকল আধুনিক সরঞ্জাম তিনি পূর্ণরূপে ব্যবহার করেছিলেন।
পশ্চিমা লখক নধৎড়হ পধৎৎধ ফবাধীঁ তার সুবিখ্যাত রংষধসরপঃযরহশবৎং গ্রন্থে বলেন, ‘মুহম্মদ আলফাতিহ-এর এ বিজয় নিছক ভাগ্যের উপহার ছিলো না, কিংবা ছিলো না শুধু প্রতিপক্ষ শক্তির দুর্বলতার ফল, বরং এজন্য দীর্ঘকাল তিনি প্রয়োজনীয় প্রস্ত্ততি গ্রহণ করেছিলেন এবং সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল শক্তি ব্যবহার করেছিলেন। কামান ছিলো তখন সদ্যউদ্ভাবিত যুদ্ধাস্ত্র। আর তিনি জনৈক হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলীর সাহায্যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ কামান তৈরী করে- ছিলেন, যাতে তিনশ কিলোগ্রাম ওজনের গোলা এক মাইলের বেশী দূরে নিক্ষেপ করা যেতো। বলা হয়, ঐ কামান চালাতো সাতশ লোক, আর তা বারুদবোঝাই হতো দু’ঘণ্টায়।
কনস্টান্টিনোপল অভিযানকালে মুহম্মদ আলফাতিহ-এর অধীনে ছিলো তিন লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী এবং অতি শক্তিশালী কামানবহর। আর সমুদ্রের দিক থেকে শহর অবরোধকারী নৌ- বহরে যুদ্ধজাহায ছিলো একশ বিশটি। তিনিই সেই মহান সমরকুশলী যিনি আপন উদ্ভাবনী প্রতিভাবলে স্থলপথে নৌজাহায চালিয়ে উপসাগরে নামানোর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন, শত্রু- পক্ষের কাছে যা ছিলো অকল্পনীয়। বহুকাষ্ঠখন্ড চর্বিত করে তার উপর দিয়ে সত্তরটি জাহায টেনে নিয়ে তিনি ‘কাসিমপাশা’র সাগরজলে নামিয়েছিলেন।
তুর্কীজাতির বৈশিষ্ট্য
সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মাঝে তুর্কীজনগোষ্ঠী তখন এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলো, যাতে সঙ্গত কারণেই তারা হয়ে উঠেছিলো মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব লাভের যোগ্য হকদার।
প্রথমত তারা ছিলো উদীয়মান, উচ্চাভিলাষী ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ একটি জাতি। তাদের মধ্যে ছিলো সত্যিকার জিহাদী চেতনা। তাছাড়া জীবনযাপনে স্বভাব ও প্রকৃতির নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তারা ঐ সকল নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিলো, যাতে প্রাচ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলো ছিলো আক্রান্ত।
দ্বিতীয়ত তাদের সামরিক শক্তি ছিলো এমন পর্যাপ্ত যার সাহায্যে তারা ইসলামের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিস্তার ঘটাতে এবং যে কোন শত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে সক্ষম ছিলো। এককথায় মুসলিম উম্মাহর পক্ষ হতে সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তারা ছিলো যোগ্যতম এক জনগোষ্ঠী। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ওছমানীরা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, বিশেষত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার প্রতি মনোযোগী ছিলো। তাদের কামানগুলো ছিলো অধিকতর দূরপাল্লার। আর অস্ত্রাগারে ছিলো সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। সামরিক প্রশিক্ষণ, যুদ্ধকৌশল উদ্ভাবন, সেনা-বাহিনীর আধুনিক বিন্যাস ইত্যাদি সকল বিষয়ে তারা পূর্ণ যত্নবান ছিলো। ফলে যুদ্ধবিদ্যা ও সমরবিজ্ঞানে তারাই ছিলো শ্রেষ্ঠ এবং ইউরোপের আদর্শ। তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার সাধ্য ছিলো না কারো।
তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিলো ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা- এই তিন মহাদেশে। ইসলামী প্রাচ্যের পারস্য থেকে মরক্কো পর্যন্ত ছিলো তাদের শাসন এবং এশিয়া মাইনর ছিলো তাদের অধিকারে। অন্যদিকে ইউরোপে তাদের অগ্রাভিযান ভিয়েনার প্রাচীরে আঘাত হেনেছিলো। সমগ্র ভূমধ্যসাগরে তারাই ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৌশক্তি; অন্য কোন নৌশক্তির সেখানে প্রবেশাধিকার ছিলো না। তুর্কী খলীফার দরবার ‘আলবাবুল আলী’তে নিযুক্ত পিটার দ্যা গ্রেট-এর প্রতিনিধি এক পত্রে বলেন, ‘সুলতান কৃষ্ণসাগরকে মনে করেন তার নিজস্ব অধিকার, যেখানে নেই অন্য কারো প্রবেশাধিকার।’
তাদের নৌবহর ছিলো এত বিশাল, যা ইউরোপের সম্মিলিত শক্তির কাছেও ছিলো না। ৯৪৫ (১৫৪৭ খৃঃ) হিজরীতে পোপের আহবানে ভেনিস, স্পেন, পুর্তগাল ও মাল্টার সম্মিলিত নৌশক্তি তুর্কী নৌবহরকে পরাস্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়ে উল্টো তারাই পর্যদুস্ত হয়েছিলো।
খলীফা সোলায়মান আলকানূনী-এর শাসনকালে তুর্কিদের যেমন জলভাগ ও স্থলভাগে ছিলো নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, তেমনি ছিলো অখন্ড রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব-প্রতিপত্তি।
ওছমানী সালতানাত তখন উত্তরে সাভা নদী, দক্ষিণে নীলনদের উৎসমুখ ও ভারতসাগর, পূর্বে ককেসাস পর্বতশ্রেণী এবং পশ্চিমে আটলাস পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তুর্কী নৌবহরে জঙ্গিজাহাযের সংখ্যা ছিলো তিন হাজারের বেশী। একমাত্র রোম ছাড়া প্রাচীন বিশ্বের সমস্ত প্রসিদ্ধ শহর ছিলো ‘আলবাবুল আলী’র অধীন।
তুর্কিদের ভয়ে সমগ্র ইউরোপ এমনই কম্পমান ছিলো যে, বড় বড় প্রতাপশালী শাসক তুর্কী সুলতানের ছত্রচ্ছায়ায় থাকাই নিরাপদ মনে করতো। তুর্কী সুলতানদের সম্মানে এমনকি গীর্জার ঘণ্টাধ্বনিও বন্ধ রাখা হতো। মুহম্মদ আলফাতিহ-এর মৃত্যুসংবাদে পোপ তিনদিনব্যাপী জাতীয় আনন্দ ঘোষণা করেছিলেন এবং কৃতজ্ঞতার প্রার্থনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন।
তৃতীয়ত ভৌগলিক ও কৌশলগত বিচারে তাদের অবস্থান ছিলো তদানিন্তন বিশ্বমানচিত্রের সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে, যা বিশ্বকে শাসনের জন্য ছিলো অতি উপযোগী। কেননা তাতে বলকান উপসাগর থেকে যুগপৎ এশিয়া ও ইউরোপের উপর নজরদারি করা সম্ভব ছিলো। তাদের রাজধানী ইস্তাম্বুল (কনস্টান্টিনোপল) ছিলো ইউরোপ ও এশিয়ার সঙ্গমস্থলে, যেখান থেকে একই সঙ্গে তারা তিন মহাদেশের উপর সহজে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারতো। তাই নেপোলিয়ান বলেছিলেন, ‘কনস্টান্টিনোপলই হচ্ছে কল্পিত ‘বিশ্বসাম্রাজ্যের’ আদর্শ রাজধানী।’
ইউরোপে তুর্কিদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো, আর নিকট ভবিষ্যতে ইউরোপ হতে যাচ্ছিলো ‘নবসম্ভাবনা’র অধিকারী। ইউরোপের বুকে তখন নতুন জীবনীশক্তি টগবগ করছিলো এবং উন্নতি-অগ্রগতির যাবতীয় উপকরণ ও কার্যকারণ বিকাশ লাভ করছিলো। তাকদীর যদি চাইতো তাহলে তুর্কিদের জন্য সহজেই সম্ভব ছিলো জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গনে অগ্রসর হওয়া এবং খৃস্টীয় ইউরোপকে ছাড়িয়ে যাওয়া। এমনকি সম্ভব ছিলো বিশ্বনেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং বিশ্বকে ইউরোপীয় ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা করে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করা, যার বার্তা তারা ইসলামের কল্যাণে আগেই লাভ করেছে।
তুর্কীদের অধঃপতন
কিন্তু ইতিহাসের গতি ছিলো অন্যদিকে। এটা শুধু তুর্কীজাতিরই দুর্ভাগ্য ছিলো না, বরং গোটা মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য ছিলো যে, উত্থান ও উন্নতির মধ্যকালেই তুর্কীরা অধঃপতনের শিকার হলো এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের রোগ-ব্যাধি তাদেরও মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও বিবাদ-কোন্দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। শাসকদের মধ্যে দেখা দিলো দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং স্বেচ্ছাচার ও ভোগের অনাচার। যুবরাজদের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে পড়লো। চরিত্র ও নৈতিকতায় মারাত্মক অবক্ষয় দেখা দিলো। শাসক, সেনানায়ক ও রাজকর্মচারী, সবার মধ্যে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়লো। দেশ ও জাতি এবং রাজ্য ও সাম্রাজ্যের প্রতি বিশ্বাস- ঘাতকতাই হলো তাদের নীতি। এমনকি গোটা জাতি বিলাসিতা ও ভোগবাদিতার মানসিকতায় আক্রান্ত হলো। এভাবে একটি পতনশীল জাতির যাবতীয় দোষ-ব্যাধি ও স্বভাবনষ্টতা তুর্কিদের মধ্যেও দেখা দিলো, যার বিশদ বিবরণ রয়েছে তুর্কীজাতির ইতিহাসগ্রন্থে। এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই।
সবচে’ ভয়ঙ্কর যে ব্যাধি তুর্কীজাতির গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিলো তা হলো নির্জীবতা ও স্থবিরতা। এটা যেমন ছিলো জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমনি ছিলো যুদ্ধবিদ্যা, সামরিক প্রশিক্ষণ এবং সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের ক্ষেত্রেও। তারা যেন ভুলেই গিয়েছিলো আসমানের এই অমোঘ নির্দেশ- ‘তোমরা প্রস্ত্তত করো তাদের জন্য যতটুকু পারো, শক্তি ও অশ্বদল, তা দ্বারা সন্ত্রস্ত করবে তোমরা আল্লাহর শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ....।
এবং ভুলে গিয়েছিলো নবুওয়তের সেই চিরন্তন বাণী- ‘জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই সে তা পাবে, সেই হবে তার অধিক হকদার।
আর যেহেতু তাদের রাজনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থান ছিলো খুবই নাযুক এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত সেহেতু সবসময় তাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য ছিলো মিশরবিজয়ী ছাহাবী হযরত আমর ইবনুল আছ (রা)-এর সেই শাশ্বত উপদেশ, যা তিনি মিশরে মুসলিম গাজীদর উদ্দেশ্যে প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- ‘মনে রেখো, কেয়ামত পর্যন্ত তোমরা বিপদ ও ঝুঁকির মুখে রয়েছো। তোমাদের অবস্থান হচ্ছে নাযুক এক মোর্চায় সতর্ক প্রহরার অবস্থায়। তোমাদের থাকতে হবে সদাসশস্ত্র। কেননা চারপাশে তোমাদের বিপুল শত্রু, আর তাদের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে তোমাদের উপর এবং তোমাদের ভূখন্ডের উপর।’
কিন্তু আফসোস, তুর্কীজাতি বসে থাকলো, আর সময় এগিয়ে গেলো। তারা পিছিয়ে পড়লো, আর ইউরোপ তাদের ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেলো। তুরস্কের বিদুষী লেখিকা খালিদা এদীব খানম তার জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতার যে চিত্র এঁকেছেন এখানে তা তুলে ধরা বেশ উপযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ‘তুরস্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাত’ গ্রন্থে তিনি বলেন-
‘জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে যত দিন কালামশাস্ত্রীয় দর্শনের কর্তৃত্ব ছিলো তত দিন ওলামা ও জ্ঞানী সমাজ তুরস্কে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপেই পালন করে যাচ্ছিলেন। সোলায়মানিয়া মাদরাসা ও মাদরাসাতুল ফাতিহ ছিলো সমকালীন যাবতীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রের কেন্দ্র। কিন্তু পাশ্চাত্য যখন ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের বৃত্ত ভেঙ্গে বের হয়ে এলো এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও নতুন দর্শনের ভিত্তি নির্মাণ করলো, যার ফলে বিশ্বে এক নতুন বিপ্লব সৃষ্টি হলো তখন মুসলিম ওলামা ও জ্ঞানী সমাজ আধুনিক শিক্ষার দায়িত্ব এবং আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য পালনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলেন। তারা ভাবতেন, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি এখনো সেখানেই নিশ্চল আছে যেখানে ছিলো খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। এই মারাত্মক ভ্রান্তিকর চিন্তা খৃস্টীয় উনিশ শতক পর্যন্ত তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে ছিলো।’
তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলিম দেশের বিদ্বানসমাজের এ চিন্তাধারার সাথে ইসলাম ও ইসলামী চেতনার কোন সম্পর্ক ছিলো না। কারণ খৃস্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব বা মুসলিম ইলমুল কালাম, মূলত এর ভিত্তি ছিলো গ্রীক দর্শনের উপর, যাতে এরিস্টটলীয় দর্শনেরই ছাপ ছিলো প্রধান, আর এরিস্টটল ছিলেন পৌত্তলিক দার্শনিক। এখানে সংক্ষেপে আমরা খৃস্টান পন্ডিত ও মুসলিম ওলামা সমাজের চিন্তা- ধারার একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরবো।
কোরআনুল কারীম কখনো প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের সৃষ্টিপ্রসঙ্গকে বিশদ আলোচনায় আনেনি। কারণ কোরআনী শিক্ষার আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নৈতিক ও সামাজিক জীবন। কোরআনের মূল উদ্দেশ্যই হলো ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং কল্যাণ- অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়া। কারণ কোরআন মানুষের জন্য একটি জীবনবিধান নিয়ে এসেছিলো। কোরআন যখনই কোন আধ্যাত্মিক বা অতিপ্রাকৃতিক বিষয় আলোচনা করেছে সেখানে বলতে গেলে কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতাই আমাদের চোখে পড়ে না। কোরআনী শিক্ষার ভিত্তিই হলো তাওহীদ বা একত্ববাদ। তাই (বিশ্বাসগত দিক থেকেও) ইসলাম একটি সহজ-সরল, নির্জটিল ও উদার ধর্মরূপে পরিচিত হয়েছে। বিশ্বজগত সম্পর্কে নতুন নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের চেয়ে অনেক উদার ছিলো। কিন্তু এই সরলতা ও উদারতা, যা নতুন জ্ঞান-গবেষণার জন্য সহায়ক হতে পারতো মুসলিমদের জীবনে তা দীর্ঘ সময় বহাল ছিলো না। হিজরী নবম শতকে মুসলিম ওলামা ও কালামবিদগণ ফিকাহ তো বটেই, এমনকি ঈশ্বরতত্ত্বীয় আলোচনাকেও বিচিত্র নিয়ম-নীতি ও বিধি-বন্ধনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। ফলে ইজতিহাদ ও গবেষণার দুয়ার বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আর ঐ সময়কালেই ইসলামী দর্শনের গভীরে এরিস্টেটলীয় ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো।
পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা ছিলো ঈসায়ী ধর্মের, যাকে সেন্ট পোল-এর ধর্ম বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। সেখানে ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টিপর্বে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে। খৃস্টানদের কাছে যেহেতু এটা ছিলো আল্লাহর কালাম সেহেতু তাদের বিশ্বাসগত অপরিহার্য কর্তব্য ছিলো তার সত্যতা সাব্যস্ত করা। কিন্তু বাস্তব পর্যবেক্ষণ যেহেতু তাদের ব্যাখ্যা- ও বক্তব্যের সমর্থনে ছিলো না সেহেতু তারা তাত্ত্বিক প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলো। আর এক্ষেত্রে তারা এরিস্টেটলের অাঁচল ধরেছিলো এজন্য যে, তার দর্শনে তখন ছিলো আশ্চর্যরকম জাদুশক্তি।
এর মধ্যে পাশ্চাত্যজগত যখন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে বিশ্বজগতের নতুন অধ্যয়ন শুরু করলো তখন গীর্জার ধর্মনেতারা দিশেহারা হয়ে পড়লো। এদিকে বাস্তব প্রমাণের ভিত্তিতে জ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব ও সত্য আবিষ্কৃত হতে লাগলো, ওদিকে খৃস্টান ধর্মপন্ডিতগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, গীর্জার প্রভাব-প্রতিপত্তির বুঝি ‘ঘণ্টা বেজে গেলো’। এভাবে শুরু হয়ে গেলো বিজ্ঞান ও ধর্মের ভয়াবহ সংঘাত। বহু বিজ্ঞানী, যারা জ্ঞান-গবেষণা ও বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিত ছিলেন, তারা হলেন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বস্ততার বলি। কিন্তু বহু রক্ত ঝরিয়ে শেষ পর্যন্ত গীর্জার কর্ণধারগণ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে বাধ্য হলেন এবং গীর্জার বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্য- সূচীতে বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করলেন। ফলে তাদের বিদ্যালয়গুলো, যা নিকট অতীতেও মুসলিম বিদ্যালয়গুলোর প্রতিবিম্ব ছিলো, হঠাৎ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হলো। তবে তারা তাদের ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মদর্শন ত্যাগ করেনি। ফল এই দাঁড়ালো যে, আধুনিক সমাজের অন্তত কিছু অংশের উপর গীর্জার প্রভাব রয়ে গেলো। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট পাদ্রিগণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও পারদর্শী হলেন এবং সর্ববিষয়ে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করলেন।
পক্ষান্তরে তুরস্কে মুসলিম ওলামা-সমাজের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা মনোযোগী হবেন কি, বরং তাদের এলাকায় নতুন চিন্তার প্রবেশও নিষিদ্ধ করে দিলেন। আর যেহেতু মুসলিম উম্মাহর শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ছিলো তাদেরই হাতে সেহেতু একই স্থবিরতা শিক্ষাব্যবস্থায়ও চেপে বসলো। তদুপরি অবক্ষয় যুগে আলিমদের রাজনৈতিক তৎপরতা দ্রুত বর্ধমান। ফলে গবেষণা ও পরীক্ষা -নিরীক্ষার গুরুভার বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিলো না। তাই সহজ নোসখা হিসাবে বাধ্য হয়েই তারা এরিস্টেটলের দর্শন অাঁকড়ে ধরলেন এবং তাত্ত্বিক প্রমাণকেই জ্ঞানের ভিত্তিরূপে বহাল রাখলেন। ফলে তের শতকে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার যে হাল ছিলো, উনিশ শতকে এসেও তা বহাল ছিলো।
মুসলিমবিশ্বব্যাপী স্থবিরতা
জ্ঞান ও চিন্তার এ স্থবিরতা ও বান্ধ্যাত্ব শুধু তুরস্কে এবং ধর্মীয় শিক্ষার মহলেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং পূর্ব থেকে পশ্চিম গোটা মুসলিমবিশ্বই এর শিকার ছিলো। মস্তিষ্ক যেন নিশ্চল, চিন্তা যেন নির্জীব এবং শরীর যেন অবশ। অষ্টম শতকের কথা নাও যদি বলি, কোন সন্দেহ নেই যে, নবম শতকই ছিলো শেষ যুগ, যেখানে দ্বীন ও ইলম এবং জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও গবেষণার এবং কবিতা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার কিছু না কিছু স্বাক্ষর ছিলো। এ শতকেই ইবনে খালদূনের আলমুকাদ্দিমার মত চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থ মুসলিম বিশ্বের গ্রন্থাগারে সংযোজিত হয়েছিলো। পক্ষান্তরে দশম শতাব্দী ছিলো নিশ্চলতা, স্থবিরতা ও অনুকরণের সূচনাযুগ। এবং এটা যেমন ছিলো ধর্মীয় জ্ঞানের সকল শাখার চিত্র, তেমনি ছিলো জ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস,দর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থার ছবি।
তখনকার জ্ঞান-গবেষণার ইতিহাস দেখুন, এমন একটি নামও আপনি খুঁজে পাবেন না যাকে বলা যায় ‘প্রতিভা’, কিংবা অন্তত ‘মনীষা’, যিনি জ্ঞান ও শাস্ত্রের কোন শাখায় সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রশংসা করার মত নতুন কোন মাত্রা যোগ করেছেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু কয়েকটি নাম, যারা তাদের যুগের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্তর থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন, যারা দ্বীনী ও ইলমী পরিমন্ডলে কোন ‘কারনামা’ বা বুদ্ধিবৃত্তিক কীর্তি উপহার দিয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রায় সব ব্যতিক্রমই ছিলো ভারতবর্ষে। যেমন শায়খ আহমদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ, মৃঃ ১০৩৪ হিঃ), যার ‘মাকতূবাত’ দ্বীনী ও ইলমী খাজানায় একটি মূল্যবান সংযোজন বলে সর্বস্বীকৃত।
এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ, মৃঃ ১১৭৬ হিঃ), যার গ্রন্থত্রয় হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ইযালাতুল খাফা ও রিসালাতুল ইনছাফ হচ্ছে স্ব-স্ব বিষয়ে সত্যি অনন্য কীর্তি!
তদ্রূপ শাহ ছাহেবের সুযোগ্য পুত্র শাহ রফীউদ্দীন দেহলবী (রহ, মৃঃ ১২৩৩ হিঃ), যিনি ‘তাকমীলুল আযহান’ ও ‘রিসালাতুল মাহাববাহ’ কিতাবে কিছু নতুন ও চমকপ্রদ চিন্তা উপস্থাপন করেছেন।
তদ্রূপ শাহ ইসমাঈল শহীদ দেহলবী (রহ, শাহাদাত, ১২৪৬ হিঃ) যার ‘মানছিবে ইমামত ও আকাবাত’ গ্রন্থদু’টি বিস্ময়কর ইজতিহাদি শানের অধিকারী এবং স্ব-স্ব বিষয়ে অতুলনীয়।
একই ভাবে বলা যায় ওলামায়ে ফিরিঙ্গি মহল-এর কথা এবং পূর্বাঞ্চলের কতিপয় শিক্ষাঙ্গন ও চিন্তাকেন্দ্রের কথা। মেধায়, মননে ও সৃজনশীলতায় তারা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিলেন এবং আপন আপন সময়কালের শিক্ষাধারায় সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন; তবে তাদের মেধা ও প্রতিভা এবং চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির কীর্তি-কর্ম পাঠ্যবিষয়ের গন্ডি খুব কমই অতিক্রম করেছে।
শুধু দ্বীনী ইলমের কথা বলি কেন, কবিতা ও সাহিত্যের অঙ্গনও ছিলো একই রকম বান্ধ্যাত্বের শিকার। কাব্যকর্ম পরিমাণে প্রচুর হলেও তাতে জীবন ও সজীবতার ছাপ ছিলো না, ছিলো শুধু গতানু- কগতিকতা, স্থূলতা ও অনুকরণ- সর্বস্বতা। সাধারণভাবে কবিতার বিষয়বস্ত্ত ছিলো রাজতোষামোদ, সস্তা চাটুকারিতা ও আত্মপ্রশস্তি।
গদ্যসাহিত্যও ছিলো আড়ম্বর, কৃত্রিমতা, ছান্দিকতা ও অন্তসার- শূন্য শব্দজৌলুসে আকীর্ণ। এমনকি ইতিহাসগ্রন্থ, দাপ্তরিক লেখা, প্রশাসনিক ফরমান এবং বন্ধুমহলীয় পত্রাবলীও এ দোষ থেকে মুক্ত ছিলো না। বিচ্ছিন্ন দু’একটি সাহিত্যকর্মে অবশ্য এমন কিছু নমুনা পাওয়া যায়, যা তখনকার সাধারণ রুচি ও প্রবণতা থেকে কিছুটা উপরে এবং পতিত স্তর থেকে কিছুটা ঊর্ধ্বে।
মাদরাসা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলোও চরম স্থবিরতা, নির্জীবতা ও বান্ধ্যাত্বের শিকার হয়ে পড়েছিলো। সেখানেও ছিলো জ্ঞানদৈন্য ও চিন্তানৈতিক অবক্ষয়ের ছাপ। পূর্ববর্তিদের সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী, যা জ্ঞান, শিক্ষা ও রুচিপ্রদ ছিলো, সেগুলোকে ক্রমান্বয়ে পাঠ্যসূচী থেকে সরিয়ে পরবর্তিদের রচনাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছিলো, নিজ নিজ বিষয়ে যাদের ইজতিহাদি যোগ্যতা ছিলো না। তারা শুধু পূর্ববর্তিদের ব্যাখ্যাকারী ও ভাষ্যকার ছিলেন। সমগ্র পাঠ্যসূচী ব্যাখ্যা, টীকা, সারসংকলন ও ‘মতন’-এ পূর্ণ ছিলো, যেখানে বিজ্ঞ লেখকগণ কাগজ-কালিতে কৃচ্ছতা করে বোধগম্য সরল ও বিশদ ভাষার পরিবর্তের ‘সংকেতভাষা’ ব্যবহার করেছেন, যা বোঝার জন্য আবার বিশদ ব্যখ্যার প্রয়োজন হতো। এভাবে ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা, তার উপর আবার টীকা-এর সিলসিলা জারি থাকতো।
উপরের চিত্র থেকে মোটামুটি বোঝা যায়, মুসলিম বিশ্বের উপর তখন জ্ঞান-বান্ধ্যাত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা কেমন কঠিনভাবে চেপে বসেছিলো, যা থেকে জীবনের কোন অঙ্গন মুক্ত ছিলো না।
তুর্কী সালতানাতের সমকালীন পূর্বাঞ্চল
তুর্কী সালতানাতের সমকালে পূর্বাঞ্চলে দু’টি শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য ছিলো। প্রথমটি হলো তৈমূর বংশীয় যহীরুদ্দীন বাবর (৯৩৩ হিঃ ১৫৪৬ খৃঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোঘল সাম্রাজ্য। বাবর ছিলেন সুলতান সেলীম প্রথম-এর সমসাময়িক। শুরুতে যারা মোঘল সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছেন, সাহস ও প্রতাপে এবং সামরিক শক্তি ও সাম্রাজ্যের বিস্তারে তারা মুসলিম বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আওরঙ্গযেব। তিনিই ছিলেন প্রতাপশালী শেষ মোঘলসম্রাট। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব যেমন ছিলো বিজয়া-ভিযানে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে তিনি তেমনি ছিলো কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানে এবং নৈতিকতা ও ধার্মিকতায়। তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সাম্রাজ্য শাসন করেছেন এবং নববই বছরেরও বেশী বয়সে ১১১৮ হিজরীতে (খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে) ইন্তিকাল করেছেন। আর সেটা ছিলো ইউরোপের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। ইউরোপ তখন আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠেছে এবং চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, খোদ আওরঙ্গযেব বা তাঁর পূর্বসূরী কারোই ইউরোপ সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিলো না। সেখানে তখন কী বিরাট পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং নবজাগরণের কার্যকারণগুলো কত দ্রুত শক্তি অর্জন করছে সে সম্পর্কে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। তাই ইউরোপ থেকে যে সামান্যসংখ্যক বণিক, চিকিৎসক ও পর্যটক মোঘল দরবারে এসেছে, তাদের তারা দয়া ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখেছেন। ভাবতে অবাক লাগে, এত বিশাল-বিস্তৃত এবং এমন জটিল জনগোষ্ঠীঅধ্যুষিত সাম্রাজ্যের শাসনভার যাদের হাতে তারা সমকাল সম্পর্কে এতটা বেখবর কীভাবে থাকতে পারেন! কিন্তু এটাই ছিলো বাস্তবতা । আরো দুর্ভাগ্য যে, আওরঙ্গযেবের উত্তরসূরীরা ছিলো ভীরু, দুর্বল, অযোগ্য ও আরামপ্রিয় শাসক। ইউরোপ থেকে ধেয়ে আসা বিপদ-দুর্যোগের মোকাবেলায় ইসলামী উম্মাহকে রক্ষা করা দূরের কথা, তাদের তো পৈতৃক রাজত্ব ও সিংহাসন রক্ষা করারও যোগ্যতা ছিলো না। শেষ ফল এই দাঁড়ালো যে, তাদের অনৈক্য ও অন্তর্কলহ, ভীরুতা ও দুর্বলতা এবং অন্তহীন অযোগ্যতার কারণে বিশাল ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হয়ে গেলো, যা ছিলো গ্রেট বৃটেনের সুসমৃদ্ধি ও সফল শিল্প- বিপ্লবের বুনিয়াদ,১
১। এ প্রসঙ্গে নৎড়ড়শং ধফধসং বলেন, ১৭৫৭ সালে পলাশী-যুদ্ধের পর বাংলার সম্পদ লন্ডনে আসা শুরু হয় এবং তার সুফলও খুব দ্রুত দেখা দেয়। এই যে এত বড় শিল্পবিপ্লব, যার প্রভাব এখন পৃথিবীর সর্বত্র দৃশ্যমান, হয়ত তার অস্তিত্বই হতো না যদি পলাশীর যুদ্ধ না হতো। বস্ত্তত ভারতবর্ষের অঢেল সম্পদই ছিলো শিল্পবিপ্লবের সহায়ক ও চালিকাশক্তি।
ভারতবর্ষ থেকে সম্পদের ঢল যখন লন্ডনে এসে আছড়ে পড়তে শরু করলো এবং বিশাল পুঁজি তৈরী হলো তখন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও বিরাট প্রতিযোগিতা শুরু হলো। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সম্পদ দ্বারা এত অধিক মুনাফা অর্জিত হয়নি, যতটা হয়েছে ভারত থেকে লদ্ধ (লুণ্ঠিত) সম্পদ দ্বারা। কেননা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে ইংলেন্ডের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না। (ঃযব ষধড়িভ পরারষমুধঃরড়হ ধহফ ফবপধু, ষড়হফড়হ, ১৮৮৯, ঢ়. ৩১৩-১৭)
একই প্রসঙ্গে ংরৎ রিষষরধস ফরমনু বলেন, ইংলেন্ডের শিল্পসমৃদ্ধি মূলত বাংলা ও কর্নাটকের সম্পদভান্ডারের কারণেই সম্ভব হয়েছে। পলাশীর পূর্বে যখন ভারতবর্ষের সম্পদ ইংলেন্ডে আসা শুরু হয়নি তখন আমাদের দেশে শিল্প বলতে কিছুই ছিলো না। (ঢ়ৎড়ংঢ়বৎড়ঁং রহফরধ: ধ ৎবাড়ষঁঃরড়হ. ঢ়.৩০)
এমনকি এটাই ছিলো মুসলিম বিশ্বের পরাধীনতা ও দাসত্ব- শৃঙ্খলের পরোক্ষ কারণ।
প্রাচ্যের দ্বিতীয় বৃহৎ সাম্রাজ্য ছিলো ইরানের ছাফাভী সালতানাত। এটি ছিলো সত্যিকার অর্থেই একটি সুউন্নত ও সুসমৃদ্ধ দেশ। কিন্তু শাসকবর্গ শিয়াবাদ ও উগ্রসাম্প্রদায়িকতায় এতই মেতে ছিলো এবং ওছমানী সালতানাতের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষে এমনই ব্যতিব্যস্ত ছিলো যে, অন্য বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার ফুরসতই তাদের ছিলো না। ফলে ইউরোপ যখন উন্নতির পথে শনৈঃশনৈঃ এগিয়ে চলেছে, সেই সুবর্ণ সময়কালটি তারা অপচয় করেছে কখনো তুর্কী সীমান্তে হামলা চালিয়ে, কখনো আত্মরক্ষার যুদ্ধে জড়িয়ে।
বস্ত্তত প্রাচ্যের এদু’টি বৃহৎ সাম্রাজ্য নিজ নিজ সমস্যায় এমনই নাজেহাল ছিলো এবং বাইরের দুনিয়া থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন ছিলো যে, ইউরোপের মত দূর-দূরাঞ্চল তো অনেক পরে, নিকটবর্তী মুসলিম দেশগুলোর পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কেও তাদের কোন ‘জানাজান্তি’ ছিলো না। আর ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, বা আন্ত-মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা, এগুলো তো সম্ভবত শাসকবর্গের চিন্তায়ও কখনো আসেনি। এমনকি ইউরোপের শিক্ষা-জাগরণ ও বিজ্ঞানসাধনা এবং শিল্পবিপ্লব ও সামরিক অগ্রগতি সম্পর্কে নিকট পর্যবেক্ষণ এবং তা থেকে যথাসাধ্য উপকৃত হওয়ার প্রচেষ্টাটুকুও তাদের মধ্যে ছিলো না; ছিলো শুধু অন্তর্কলহে মেতে থাকা, আর ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দেয়া। এককথায়, ইউরোপে যখন জাগরণের শোর, মুসলিম জাহানে তখন ঘুমের ঘোর!
হেমন্তেও বসন্তের কিছু আভাস
একথা সত্য যে, মুসলিম উম্মাহর সবুজ-সজীব উদ্যান, যেখানে নিরন্তর প্রস্ফুটিত হতো প্রতিভার অসংখ্য ফুল, তা তখন উজাড় হয়ে গিয়েছিলো এবং বসন্ত-বাহার বিদায় নিয়েছিলো। তবে একথাও সত্য যে, ঐ অবস্থায়ও মাঝে মধ্যে এখানে সেখানে ইসলামবৃক্ষে কিছু সবুজ কিশলয়ের উন্মেষ ঘটেছে এবং হেমন্তকালেও তা এমন কিছু ফুল ও ফল উপহার দিয়েছে, যার তুলনা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ইতিহাসের বসন্তকালেও খুব বেশী পাওয়া যায় না। সোজা ভাষায় আমরা বলতে পারি, যুগটা ছিলো জাতীয় অবক্ষয় ও অধঃপতনের, তবে ব্যক্তিপর্যায়ে কিছু অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কর্মের। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন উচ্চ মনোবল, উদ্দীপ্ত চেতনা ও জাগ্রত মস্তিষ্কের অধিকারী এমন কতিপয় ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিলো, যারা কিছু সময়ের জন্য হলেও পতনোন্মুখ জাতি ও জনগোষ্ঠীর মাঝে নবজীবনের সঞ্চার করেছিলেন। ভারতবর্ষে সুলতান ফতহে আলী খান টিপুর মত সাহসী, দূরদর্শী ও সিংহহৃদয় শাসক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, হিন্দুস্তানকে যিনি নতুন আযাদীর ও নয়া যিন্দেগির প্রায় দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছিলেন। অন্যদিকে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ)-এর মত জাদুকরী ব্যক্তিত্বের অধিকারী দাঈ ও মুজাহিদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন যিনি খেলাফতে রাশেদার আলোকে ইসলামী হুকুমত কায়েমের জিহাদ শুরু করেছিলেন, যার সীমানা বিস্তৃত হবে হিন্দুস্তান থেকে বোখারা পর্যন্ত; তাঁর দাওয়াত ও তারবিয়াতের ফলে উন্নতচরিত্র অসংখ্য মুজাহিদ এবং নিবেদিত প্রাণ দাঈ ও সিপাহী তৈরী হয়েছিলো, যাদের ঈমান ও ইয়াকীন, ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াত এবং জোশ ও জাযবা সেই ‘কুরূনে উলা’র ঝলক দেখিয়েছিলো। বলতে গেলে ঐ পতনমুখী যুগে তিনি এক অসাধ্যই সাধন করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক অরাজকতা, চারিত্রিক অধঃপতন এবং জাতীয় তন্দ্রাচ্ছন্নতা এমনই চূড়ান্ত ছিলো যে, বিশাল বটবৃক্ষের মত এসকল ব্যক্তিত্বও মুসলমানদের পতন ও অধঃপতনের গতিমাত্রায় বিশেষ কোন ‘রোকথাম’ আনতে পারেননি এবং উম্মাহ সামগ্রিকভাবে তাঁদের জিহাদ ও মুজাহাদা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং তাজদীদী প্রয়াস-প্রচেষ্টা থেকে তেমন কোন সুফল অর্জন করতে পারেনি।
শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপের উত্থান
ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই তুর্কীরা নীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে অবক্ষয় এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে পশ্চাদ্পদতার শিকার হয়ে পড়েছিলো। মানবজাতির ইতিহাসে এটা ছিলো এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ, যার ছাপ ও প্রভাব পড়েছে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে। ইউরোপ তখন দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছে এবং বিপুল এক উদ্দীপনা ও উন্মাদনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, যাতে দ্রুততম সময়ে পিছনের অজ্ঞতা ও মূর্খতার ক্ষতিপূরণ হতে পারে। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তাদের উন্নতির গতি ছিলো বিস্ময়কর। আপন লক্ষ্যের পথে তারা শুধু দৌড়ে যাচ্ছিলো না, বরং ডানা মেলে উড়ে চলেছিলো। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে তারা বশীভূত করছিলো এবং সৃষ্টিজগতের রহস্যরাজি উন্মোচিত করছিলো। অজানা দেশ-মহাদেশ ও সাগর-পথ আবিষ্কৃত হচ্ছিলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাদের অগ্রযাত্রা এবং জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তাদের শোভাযাত্রা অব্যাহত ছিলো। এই সংক্ষিপ্ত সময়কালে সেখানে অনন্যসাধারণ বহু বিজ্ঞান-প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছিলো। সংক্ষিপ্ত উদাহরণে যাদের নাম উল্লেখ করা যায় তারা হলেন কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন ও অন্যান্য। বস্ত্তত এই মহাবিজ্ঞানি- গণ জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের জগতে প্রাচীন ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন এবং জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। অভিযাত্রী ও নাবিকদের মধ্যে ছিলেন কলোম্বাস, ভাসকো ডি গামা ও ম্যাগলিন-এর মত সাহসী, উদ্যমী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি, যারা অজানা দেশ-মহাদেশ এবং নতুন সাগর-পথ আবিষ্কার করেছেন।
উপরোক্ত সময়কালে ইতিহাসের পাতায় বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর স্থান ও অবস্থান নতুনভাবে বিন্যস্ত হচ্ছিলো। কারো ভাগ্যতারকা ছিলো উদয়ের পথে, কারো ভাগ্যতারকা ছিলো অস্তাচলে। তখনকার একটি মুহূর্ত ছিলো কয়েক দিন এবং একটি দিন ছিলো কয়েক বছরের সমান। সুতরাং এ যুগসন্ধিক্ষণে সামান্য সময়ও নষ্ট করার অর্থ ছিলো বহু দীর্ঘকাল নষ্ট করা। কিন্তু হায় আফসোস, মুসলিম উম্মাহ তখন শুধু দিন, মাস ও বছর নয়, বরং বহু যুগ ও বহু প্রজন্মের অপচয় করেছে। ইউরোপের জাতিবর্গ যেখানে প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করেছে এবং জ্ঞান-গবেষণা ও বিজ্ঞানসাধনার সকল অঙ্গনে বছরে যুগের পথ অতিক্রম করেছে।
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে তুর্কিদের পশ্চাদ্পদতার একটা সাধারণ ধারণা পেতে হলে এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, ষোড়শ শতাব্দীর আগে সেখানে জাহাজ- নির্মাণ শিল্পের কোন অস্তিত্বই ছিলো না। পক্ষান্তরে ছাপাখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ইউরোপীয় পদ্ধতির সামরিক একাডেমির সাথে পরিচয় ঘটেছে মাত্র অষ্টাদশ শতকে। এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তুরস্ক শিল্প, প্রযুক্তি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার জগত থেকে এত দূরে ছিলো যে, রাজধানীর আকাশে উড়ন্ত বেলুন দেখে মানুষ ভেবেছিলো, জাদুমন্ত্র! ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলোও এক্ষেত্রে তুরস্ককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এমনকি মিশরও তুরস্কের চার বছর আগে রেলযোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলো, আর ডাকটিকেট চালু হয়েছিলো কয়েক মাস আগে।
এই যখন ছিলো মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বদানকারী তুরস্কের অবস্থা তখন তার শাসনাধীন বা প্রভাবাধীন আরব-অনারব দেশগুলোর অবস্থা কী হতে পারে তা তো সহজেই বোঝা যায়। মাঝারি তো নয়ই, এমনকি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পেরও প্রচলন সেসব দেশে ছিলো না। ফরাসী পর্যটক মঁসিয়ে ভলনে -যিনি অষ্টাদশ শতকে মিশর ভ্রমণ করেন এবং চার বছর সিরিয়ায় অবস্থান করেন- তার সফরনামায় লিখেছেন, ‘শিল্পে এদেশ (সিরিয়া) এতই অনগ্রসর যে, তোমার ঘড়ি নষ্ট হলে মেরামতের জন্য বিদেশী কারিগরের কাছে যেতে হবে।’
তদুপরি মুসলমানদের এই পিছিয়ে পড়া শুধু বিজ্ঞান-দর্শন, তত্ত্বীয় জ্ঞান, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রেই ছিলো না, বরং ছিলো সর্বব্যাপী। এমনকি যুদ্ধবিদ্যা ও সমরশিল্পেও তারা ইউরোপ থেকে পিছিয়ে পড়েছিলো। অথচ শেষ দিকেও এক্ষেত্রে তুরস্কের শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো সর্বস্বীকৃত। কিন্তু ইউরোপ অস্ত্রনির্মাণ, যুদ্ধকৌশল উদ্ভাবন এবং উন্নত সামরিক ব্যবস্থাপনায় তুরস্ককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। ফলে ১৭৭৪ সালে তুরস্ক ইউরোপীয় বাহিনীর হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এভাবে যুদ্ধের মাঠেও যখন ইউ- রোপের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত হলো। তখন ওছমানী সালতানাতের টনক কিছুটা নড়লো এবং খলীফার আদেশে সামরিক প্রশিক্ষণ ও বাহিনী পুনর্গঠনের জন্য কতিপয় ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ডেকে আনা হলো। সুলতান তৃতীয় সেলিম উনিশ শতকের শুরুর দিকে আরো ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি যেমন বাস্তববাদী ও দূরদর্শী ছিলেন তেমনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও কুশলী। শাহী ঐতিহ্যের বিপরীতে তার শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছিলো রাজপ্রাসাদের বাইরে রুক্ষ-কঠিন পরিবেশে। তিনি আধুনিক ধারার নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে তিনি নিজে শিক্ষা দান করতেন। এছাড়া তিনি আধুনিক পদ্ধতির একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও বেশ কিছু সংস্কার সাধন করেন। কিন্তু তুর্কীজাতি ও তার সমাজব্যবস্থা এতটাই স্থবির ও রক্ষণশীল ছিলো যে, কোন প্রকার আধুনিকায়ন ও সংস্কার প্রচেষ্টা গ্রহণ করার যোগ্যতা তাদের ছিলো না। ফলে সেনাবাহিনীর পুরোনো অংশ বিদ্রোহ করে বসে এবং তিনি মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। পরে সুলতান দ্বিতীয় মাহমূদ তার স্থলাভিষিক্ত হন, যার শাসকাল ছিলো ১৮০৭ থেকে ৩৯ সাল পর্যন্ত। তার পর সিংহাসনে আসেন সুলতান প্রথম আব্দুল মজীদ, যার শাসনকাল ছিলো ৩৯ থেকে ৫১ সাল পর্যন্ত। তারা উভয়ে শহীদ সুলতান তৃতীয় সেলিমের মিশন অব্যাহত রাখেন। ফলে তুরস্ক কিছুটা উন্নতি-অগ্রগতি লাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তিক্ত সত্য এই যে, আলোচ্য সময়কালে মুসলিম তুরস্কের উন্নতি-অগ্রগতির সঙ্গে ইউরোপীয় জাতিবর্গের তুলনা করলে হতবাক হতে হয়। ইউরো-তুরস্কের প্রতিযোগিতা যেন ছিলো গল্পের খরগোশ ও কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতা, তবে পার্থক্য এই যে, ক্ষিপ্রগতির খরগোশ এখানে জাগ্রত, আর ধীরকচ্ছপ এই জাগে এই ঘুমিয়ে পড়ে।
আঠারো ও উনিশ শতকে মরক্কো, আলজিরিয়া, মিসর, হিন্দুস্তান, তুর্কিস্তান ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রাচ্যের মুসলিম জাতি ও জনগোষ্ঠীর মাঝে এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতি ও শক্তির মাঝে যে ভয়াবহ সংঘাত-সংঘর্ষ সঙ্ঘটিত হয়েছিলো তাতে জয়-পরাজয়ের ফায়ছালা আসলে ষোল ও সতের শতকেই হয়ে গিয়েছিলো এবং সাধারণ ‘সমঝ-বুঝ’ আছে এমন যে কারো পক্ষে তখনই এর ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিলো। অর্থাৎ যা ঘটেছে ইতিহাসের গতিধারায় তা ঘটা অনিবার্য ছিলো।
চতুর্থ অধ্যায়ঃ ইউরোপীয় যুগ
প্রথম পরিচ্ছেদঃ জড়বাদী ইউরোপ
পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বভাব-প্রকৃতি ও ইতিহাস
তুর্কী সালতানাতের পতনের পর ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিশ্বের শাসনক্ষমতা এবং চিন্তানৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব মুসলিম জাতির হাত থেকে ইউরোপের অমুসলিম জাতিবর্গের হাতে চলে গিয়েছিলো। কারণ এর জন্য তারা দীর্ঘকাল ধরে প্রস্ত্ততি গ্রহণ করেছিলো। তাছাড়া জীবনের ‘কর্মমঞ্চে’ তখন তাদের সমস্তরের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছিলো না। অবশেষে অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম কোন দেশ ও জনপদ তাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিলো না। হয় তারা ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থ- নৈতিক শাসন-শোষণের শিকার ছিলো, না হয় ছিলো সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের শিকার, এমনকি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তারা হয়ে পড়েছিলো ইউরোপের উচ্ছিষ্টভোজী।
ক্ষমতা ও নেতৃত্বের এই যে হাতবদল, এর ফলে সমকালীন পৃথিবীর চিন্তা-চেতনায়, সমাজ-সভ্যতায়, বিভিন্ন জাতির চরিত্র ও নৈতিকতায়, রুচি, চাহিদা ও প্রবণতায় কী প্রভাব পড়েছিলো? এবং এই বিপ্লব ও পরিবর্তন দ্বারা মানবজাতি ও মানব সভ্যতা উপকৃত হয়েছে না ক্ষতিগ্রস্ত? এসম্পর্কে বিচার-পর্যালোচনার পূর্বে আমরা দেখতে চাই পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বভাব ও প্রকৃতি এবং তার গঠনকাঠামো কী? এবং এই সভ্যতার কোলে প্রতিপালিত জাতিসমূহের জীবনদর্শনই বা কী এবং কীভাবে তার বিকাশ ঘটেছে?
অনেকে মনে করেন, বিশ শতকের পাশ্চাত্য সভ্যতা হচ্ছে ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের পরবর্তী ‘জাগরণযুগে’ সৃষ্ট একটি অল্পবয়স্ক সভ্যতা। আসলে তা নয়, বরং এ সভ্যতার ইতিহাসের শিকড় বহু হাজার বছর অতীতের মাটিতে প্রোথিত। অর্থাৎ এটি হচ্ছে গ্রীক ও রোমান উভয় সভ্যতার সন্তান। উভয় সভ্যতা যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজদর্শন এবং চিন্তানৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ফল ও ফসল রেখে গেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা উত্তরাধিকার সূত্রেই সেগুলো ধারণ করেছে এবং উভয় সভ্যতার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য এবং ঝোঁক ও প্রবণতার সুগভীর ছাপ প্রজন্মপরম্পরায় রক্তসূত্রেই তাতে প্রতিফলিত হয়েছে।
গ্রীকসভ্যতাই হলো ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা ও স্বভাব-প্রবণতার প্রথম সর্বোত্তম প্রকাশক্ষেত্র, যা ইতিহাস আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে। এটাই হলো প্রথম সভ্যতা যা ইউরোপীয় দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে ইউরোপীয় মনস্তত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। পরবর্তীতে গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষেরই উপর রোমান সভ্যতার সৌধ গড়ে উঠেছে এবং এরও প্রাণ-প্রেরণা ছিলো অভিন্ন, অর্থাৎ ইউরোপীয় প্রাণ-প্রেরণা। ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীগুলো বহু শতাব্দীর পথপরিক্রমায় নিজেদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, রীতি-নীতি, চিন্তা-চেতনা, দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তি সযত্নে নিজেদের মধ্যে লালন-প্রতিপালন করে এসেছে। অবশেষে ঊনিশ শতকে এক নতুন ঝলমলে ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। পোশাকের চোখধাঁধানো চাকচিক্য ও মনকাড়া ফুল নকশার কারণে আপনার মনে হতে পারে, এটা বুঝি আলাদা বুননের নতুন পোশাক, অথচ প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন গ্রীক-রোমান সভ্যতাই হচ্ছে এর ‘তানা-বানা’র উৎস। সুতরাং আমাদের জন্য ভালো হবে প্রথমে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পরিচয় এবং তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও প্রাণ-প্রেরণা সম্পর্কে সম্যক অবগতি অর্জন করা, যাতে আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বিশ শতকের পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্ত্তনিষ্ঠ সমালোচনা করতে পারি এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।
গ্রীকসভ্যতার বৈশিষ্ট্য
এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানব-ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় গ্রীকজাতি হচ্ছে এক স্বর্ণপ্রসভা জাতি। জ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের যোগ্যতায়; চিন্তা, চেতনা ও বুদ্ধির উর্বরতায় এবং দর্শনে, মননে ও অবদানে তাদের শীর্ষ অবস্থান সর্বস্বীকৃত। বিরল প্রতিভার অধিকারী বহু জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে, যাদের অবদানে বিশ্বের জ্ঞানভান্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে।
আমরা জানি, গ্রীকদর্শন ও সাহিত্য বিশ্ব-ইতিহাসে দীর্ঘকাল যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, কিমুত সেটা এখানে আমাদের আলোচ্য- বিষয় নয়। আমরা এখানে শুধু দেখতে চাইবো গ্রীকরা যে সভ্যতা জন্মদান করেছে তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণ ও প্রেরণা কী ছিলো?
এখনকার বিচার-পর্যালোচনায় আমরা ঐসব বিষয় এড়িয়ে যাবো, যা গ্রীক সভ্যতার মূল উপাদান নয়, বরং পার্শ্ব-উপাদান, কিংবা যা সকল সভ্যতারই সাধারণ উপাদান। আমরা শুধু ঐসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করবো, যা গ্রীক সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য এবং যা তকে অন্যান্য সভ্যতা থেকে, বিশেষত প্রাচ্য সভ্যতা থেকে পৃথক করে। ঐ বিষয়গুলো এই-
(ক) যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাতে বিশ্বাস এবং যা কিছু ইন্দ্রিয়াতীত তাতে অবিশ্বাস ও সংশয়।
(খ) ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় নিরাসক্তি এবং পার্থিব জীবন ও ভোগবিলাসে অতিআসক্তি।
(গ) উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা।
গ্রীক সভ্যতার এই যে বিভিন্ন মৌলিক উপাদান, এগুলোকে আমরা যদি এক শব্দে প্রকাশ করতে চাই তাহলে ‘বস্ত্তবাদিতা’ হলো সবচে’ যথার্থ শব্দ এবং এটাই হচ্ছে গ্রীক সভ্যতার মূল পরিচয়। গ্রীকদের যা কিছু জ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি, এমনকি তাদের ধর্ম, সর্বত্র ঐ বস্ত্তবাদিতার ছাপ ও প্রভাব অতি প্রকট। আল্লাহ তা‘আলার ছিফাত ও গুণাবলীকে তারা দেবদেবীর আকার ছাড়া কল্পনা করতে পারেনি। যেমন খাদ্যের দেবতা, দয়া ও করুণার দেবতা, ক্রোধ ও শাস্তির দেবতা। এভাবে তারা বহু দেবমূর্তি তৈরী করে বিভিন্ন মন্দিরে সেগুলোর অধিষ্ঠান করেছে। তারা তাদের দেব-দেবীর প্রতি জড়দেহের যাবতীয় স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করে রূপকথার এক দীর্ঘ জাল বিস্তার করেছে। সৌন্দর্য ও ভালোবাসার মত বস্ত্তনিরপেক্ষ ভাব ও মর্মকেও তারা স্থূল আকার দান করেছে। তাই তাদের রয়েছে সৌন্দর্যের দেবী ও ভালোবাসার দেবী। এরিস্টেটল-এর দর্শনে এই যে, ‘দশবুদ্ধি ও নয় আকাশ’-এর ধারণা, সেটাও মূলত এই বস্ত্তবাদিতারই কারিশমা, যার প্রভাব থেকে গ্রীকমানস কখনো মুক্ত হতে পারে না।
ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তা- নায়কগণও গ্রীক সভ্যতায় বস্ত্তবাদের প্রাধান্যের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণাপত্রে সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। কয়েক বছর আগে জার্মান পন্ডিত ডক্টর হ্যাস জেনেভায় ‘ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ’ শিরোনামে তিনটি ভাষণ প্যদান করেছেন। প্রসঙ্গত, তিনি সেই বুদ্ধিজীবী সমাজের একজন যারা মনে করেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্যের সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, বরং তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বকীয়তাপূর্ণ একটি সভ্যতা। এখানে আমরা আমাদের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ পেশ করছি। তিনি বলেন-
‘প্রাচীন গ্রীক সভ্যতাই হলো বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার মূল উৎস। গ্রীক সভ্যতার কর্ণধার যারা তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই ছিলো মানুষের সকল শক্তির সুসঙ্গত ও সুসমন্বিত বিকাশ। এক্ষেত্রে একটি সুদর্শন ও সুঠাম দেহকেই মনে করা হতো আদর্শ উদাহরণ। বলাবাহুল্য যে, এ চিন্তাধারায় ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলোই ছিলো মুখ্য। তাই শরীরচর্চা, শারীরিক খেলাধূলা, নৃত্যকলা ইত্যাদির গুরুত্ব ছিলো সবচে’ বেশী। পক্ষান্তরে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিপালন তথা গান, কবিতা, সাহিত্য ও নাটক, এমনকি দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চাও একটি নির্ধারিত সীমা থেকে অগ্রসর হতে পারেনি। এদিকে তাদের বেশ সতর্ক দৃষ্টি ছিলো যে, বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ দ্বারা শারীরিক উন্নতি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর আত্মা ও আধ্যাত্মিকতা এবং হৃদয় ও অন্তর্বাদিতা! সত্য এই যে, গ্রীকদের ধর্মব্যবস্থায় এসবের কোন স্থান ছিলো না। তাতে না ছিলো ধর্মবিষয়ক জ্ঞান, না ছিলো কোন ধর্মীয় শ্রেণীর উপস্থিতি। এর পরো বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে আধ্যাত্মিকতার যা কিছু ছাপ ও প্রভাব দেখা যায় তা মূলত প্রাচ্য থেকে ধার করা। সেগুলোকে গ্রীক সভ্যতার অঙ্গ মনে করা ঠিক নয়।
বহু ইউরোপীয় পন্ডিত গ্রীক সমাজে ধর্মের প্রভাবহীনতা, ঐশী ভীতির অনুপস্থিতি এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ভাবগাম্ভীর্যের অভাব, সেই সঙ্গে খেলাধূলা ও আনন্দ-বিনোদনের অতিশয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। যরংঃড়ৎু ড়ভ বঁৎড়ঢ়বধহ সড়ৎধষং-এর লেখক লেকী বলেন-
‘গ্রীক চেতনা ছিলো নিছক বুদ্ধি ও মস্তিষ্কনির্ভর, পক্ষান্তরে মিসরীয় চেতনা ছিলো সম্পূর্ণ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক। তাই রোমান লেখক এ্যপিউলিয়াস বলেছেন, ‘মিসরীয় দেবতারা সন্তুষ্ট হন কাকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটিতে, পক্ষান্তরে গ্রীক দেবতারা খুশী নাচ-গানে ও নৃত্যগীতে।’
এ্যপিউলিয়াসের এ মন্তব্যের দ্বিতীয় অংশের সত্যতা, কোন সন্দেহ নেই গ্রীকদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। কারণ কোন জাতির ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে আনন্দ-উৎসব ও ক্রীড়া-কৌতুকের এতটা ‘বাড়বাড়তি’, সেই সঙ্গে ঈশ্বরভীতির এতটা ঘাটতি নেই যতটা রয়েছে গ্রীকসমাজে। ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও ভক্তি গ্রীকদের ধর্মজীবনে ততটুকুই ছিলো যতটা থাকে সমাজের বড় ও বয়োবৃদ্ধদের প্রতি। প্রচলিত কিছু আচার আনুষ্ঠানিকতাকেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিবেদনের জন্য যথেষ্ট মনে করা হতো।
এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ গ্রীকদের ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মদর্শনই ছিলো এমন যে, তারপর অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভয়ভীতি, আনুগত্য ও আত্মনিবেদনের ভাব জাগ্রত হওয়ার কোন অবকাশই থাকে না। ঈশ্বরসত্তা থেকে সকল গুণ ও ক্ষমতা বিযুক্ত করে যখন ঘোষণা করা হবে যে, সৃষ্টিজগতের পরিচালনায় তাঁর কোন ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণ নেই এবং নেই নিরন্তর সৃজনক্রিয়া ও আদেশ-নিষেধ, অর্থাৎ ঈশ্বর হলেন অবসরপ্রাপ্ত একটি নিষ্ক্রিয় সত্তা; এখন নিয়ন্ত্রণশক্তি হচ্ছে তথাকথিত ‘সতত সক্রিয় বুদ্ধি ও মহাশূন্যীয় নিরন্তর গতি’। এ-ই যখন হবে কারো বোধ ও বিশ্বাস তখন স্বভাবতই প্রথাসর্বস্বতার বাইরে বাস্তব জীবনে এবং কর্মমুখর অঙ্গনে ঈশ্বরচিন্তার কোন প্রয়োজন এবং ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদনের কোন প্রেরণা সে অনুভব করবে না। ভয় ও ভালোবাসা এবং প্রত্যাশা ও প্রার্থনার কথা তার চিন্তায়ও আসবে না। ঈশ্বরের শক্তি ও বড়ত্বের সামনে সে অবনত হবে না; বিপদে, দুর্যোগে, সমস্যা ও সংকটে ঈশ্বর-সমীপে তার কোন কাকুতি-মিনতি থাকবে না এবং অভিভূত হৃদয়ে ঈশ্বর-বনদনায় সে নিমগ্ন হবে না। কেন হবে?! তার তো বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর হচ্ছেন যাবতীয় গুণ ও শক্তি থেকে বিচ্যুত এবং বিশ্বজগতের পরিচালনা থেকে নির্বাসিত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় একটি সত্তা; কোন কিছুতে কোন হস্তক্ষেপের ইচ্ছা ও ক্ষমতা যার নেই; যিনি ‘প্রথম বুদ্ধি’ সৃষ্টি করার পর বিশ্বজগতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা থেকে পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেছেন। এমন বিশ্বাসে যারা ‘আক্রান্ত’ তাদের জীবন তো ঈশ্বরহীন- রূপেই যাপিত হবে এবং হওয়া উচিত। আচরণগত দিক থেকে তাদের জীবন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী নাস্তিক থেকে মোটেই ভিন্ন হতে পারে না, শুধু এইটুকু ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণ ছাড়া যে, ঈশ্বর ‘প্রথম বুদ্ধি’ সৃষ্টি করেছেন এবং অবসর গ্রহণ করেছেন।
সুতরাং আমরা যখন শুনি, গ্রীকদের জীবনাচরণে ঈশ্বরচিন্তা ও আল্লাহভীতির কোন ছাপ ছিলো না, বরং তাদের উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান ছিলো যেন প্রাণহীন দেহ, কিংবা কাগজের ছবি; তদ্রূপ যখন শুনি, তাদের ঈশ্বরভক্তি ছিলো নিছক আচার-প্রথায় সীমাবদ্ধ যেমন হয় সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধদের প্রতি, যখন এসব শুনি তখন অবাক হওয়ার কিছু থাকে না; বরং এর বিপরীত কিছু শুনলেই আমরা অবাক হতাম। কেননা ইতিহাসের পাতায় মানুষ বহু শিল্পী, কবি, আবিষ্কারক ও বিজয়ী বীরের আলোচনা পড়ে, কিন্তু তাদের সঙ্গে ভয় ও ভীতি, ভক্তি ও প্রীতি এবং উপাসনা ও প্রার্থনার সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এটা তো শুধু তখনই হতে পারে যখন মানুষ এমন এক পরম সত্তা ও পরম শক্তিতে বিশ্বাস করবে, যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, যিনি সবকিছু দেখেন, শোনেন, জানেন এবং পরিচালনা করেন, যিনি সর্বশক্তিমান, সর্ববিষয়ে সকলে যার মুখাপেক্ষী, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, যিনি দয়াময়, করুণাময় ও মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।
গ্রীকদর্শন ও সমাজব্যবস্থায় যেহেতু পার্থিব জীবনই ছিলো মুখ্য এবং ভাস্কর্যপ্রীতি, নৃত্যগীত ও সঙ্গীত তথা ললিতকলার প্রতি আসক্তি ছিলো সীমাহীন, সর্বোপরি লেখক, সাহিত্যিক ও দার্শনিকসমাজ ছিলো বাধাবন্ধনহীন ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী সেহেতু গ্রীকদের জীবন ও চরিত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব ছিলো খুবই ভয়ঙ্কর। নীতি ও নৈতিকতায় দেখা দিয়েছিলো সীমাহীন নৈরাজ্য এবং প্রতিষ্ঠিত সকল ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছিলো মহাবিদ্রোহ। প্রবৃত্তির পিছনে ছুটে চলা, জীবন ও যৌবনকে যথেচ্ছা ভোগ করে যাওয়া এবং ক্ষুধার্ত হায়েনার মত সবকিছুর উপর ঝাপিয়ে পড়া- এই ছিলো তখনকার ফ্যাশন এবং মুক্তবুদ্ধি ও আলোকিত চিন্তার প্রতীক। প্লেটো তার ‘রিপাবলিক’ গ্রন্থে সক্রেটিসের পক্ষ হতে একজন গণতান্ত্রিক যুবকের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে একথাই মনে হবে, যেন বিশ শতকের কোন বোদ্ধা সমালোচক আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন আলোকিত যুবকের চরিত্র তুলে ধরছেন। সক্রেটিসের গণতান্ত্রিক যুবকের চিত্র এবং বিশ শতকের আলোকিত যুবকের চরিত্র যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ । সক্রেটিস বলেছেন-
‘যদি তাকে বলা হয়, মানুষের সব ইচ্ছা ও চাহিদা সমান গ্রহণযোগ্য নয়। কিছু আনন্দ ও বিনোদন আছে যা উত্তম ও সম্মানযোগ্য, যা সাদরে গ্রহণ করা যায়। আবার কিছু আছে অনুত্তম ও অসঙ্গত, যা পরিহার করা এবং বিধি-নিষেধের আওতায় রাখাই কর্তব্য, তখন সে এই সুসঙ্গত নীতিকথা মানতে চায় না, এমনকি শুনতেও চায় না; বরং উপহাস করে মাথা দোলায় এবং জোরদার বয়ান দিয়ে বলে, ভালো-মন্দের পার্থক্য ছাড়া সকল চাহিদাই সমান সমাদরযোগ্য। এভাবেই সে জীবন কাটায়; মাথাচাড়া দেয়া প্রতিটি চাহিদা চরিতার্থ করে, করতেই থাকে। কখনো মদে চুর হয়ে গানের সুরে ডুবে থাকে, কখনো খেয়ালের বসে উপবাস পালন করে; তখন পানি ছাড়া কিছু সে মুখে দেয় না। কখনো সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে খুব উৎসাহী, কখনো এমন অলস যে, সবকিছু সিকায় তুলে রেখে বসে আছে। কখনো দার্শনিকের আলখেল্লা ধারণ করে, কখনো রাজনীতির মঞ্চে সময়মুখী বক্তৃতা ঝাড়ে। কখনো যুদ্ধবাদী সেজে সেনা-অধিনায়কের স্ত্ততি গায়, কখনো (শান্তিবাদী সেজে) সফল ব্যবসায়ী হওয়ার বাসনায় বাণিজ্য করে। এককথায় জীবনে তার কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই, কিন্তু এই উদ্দেশ্যহীন জীবনকেই সে মনে করে সুখী-সুন্দর ও কুসুমাস্তীর্ণ জীবন। এভাবেই সে জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হয়।’
পাশ্চাত্য মানসিকতার আরেকটি বড় উপসর্গ হলো উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। এশিয়ার তুলনায় ইউরোপে জাতীয়তাবাদী চেতনা অনেক বেশী ব্যাপক ও প্রকট। অবশ্য এর পিছনে ভৌগলিক প্রকৃতিরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কেননা এশিয়ায় প্রাকৃতিক অঞ্চল অতি বিস্তৃত। এখানে রয়েছে বৈচিত্রপূর্ণ আবহাওয়া এবং বহু ভাষা ও জনগোষ্ঠী। এশিয়ায় যেমন রয়েছে ভূমি-উর্বরতা, তেমনি রয়েছে জীবনোপকরণের প্রাচুর্য। একারণেই প্রকৃতিগত ভাবেই এশিয়ার সাম্রাজ্যগুলো হয়ে থাকে সুবিস্তৃত। এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইতিহাসের বিস্তৃততম ও সমৃদ্ধতম বিভিন্ন সাম্রাজ্য। পক্ষান্তরে ইউরোপে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা খুবই তীব্র। সেখানে সকল জনগোষ্ঠীকে নিরন্তর জীবনসংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। কারণ একদিকে ভূমি ও আয়তন অল্প, অন্যদিকে আবাদি ও জনবসতি খুব ঘন, তদুপরি জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ অতি সীমিত। পর্বতশ্রেণী ও নদনদীর প্রাকৃতিক সীমারেখা ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী- গুলোকে একটি স্থায়ী প্রাকৃতিক বেষ্টনীতে ঘিরে রেখেছে। বিশেষ করে ইউরোপের পশ্চিম-মধ্য অঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মোটেই উপযোগী নয়। সুতরাং ভৌগলিক প্রকৃতির কারণেই ইউরোপে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছে এবং প্রাচীন কাল থেকেই সেখানকার রাজনৈতিক ধারণা নগররাষ্ট্রকে অতিক্রম করতে পারেনি, যার সীমানা হতো খুব বেশী হলে কয়েক মাইল; তবে সেগুলো ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বশাসিত। নগররাষ্ট্রীয় এই রাজনৈতিক ধারণার আদর্শ উদাহরণ হলো গ্রীকদেশ, যেখানে ইতিহাসের শুরু থেকেই ‘বহুদশ’ ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিলো।
এই প্রেক্ষাপটে গ্রীকজাতি যদি জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার প্রবক্তা হয়ে থাকে তাহলে অবাক হওয়ার তো কিছুই নেই। সুপ্রসিদ্ধ লেখক লেকী স্বীকার করেছেন, গ্রীসে জাতীয়তাবাদই ছিলো মূল চিন্তা- ধারা, পক্ষান্তরে সক্রেটিস, ইন্সাগোরিউস ও অন্যান্য দার্শনিক মাঝে মধ্যে যে আন্তর্জাতিকতার ধ্যানধারণা ব্যক্ত করেছেন, তা কখনো গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এমনকি এরিস্টেটলীয় নীতিব্যবস্থা (ংুংঃবস ড়ভ বঃযরপং)ও গ্রীক-অগ্রীক বিভেদ-রেখার উপরই গড়ে উঠেছিলো এবং স্বদেশপ্রেমের মর্যাদা ছিলো ঐসকল নৈতিকগুণাবলীর উপরে, যা গ্রীক দার্শনিকগণ সম্মিলিতভাবে নির্ধারণ করেছিলেন। এমনকি এরিস্টেটল শুধু স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশানুগত্যেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তার চিন্তার সংকীর্ণতা ছিলো এত দূর যে, তিনি বলতে পেরেছেন, ‘গ্রীকদের উচিত অগ্রীকদের সাথে জীবজন্তুর মত আচরণ করা।’
এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ গ্রীকসমাজে বেশ জনপ্রিয় ছিলো এবং তাদের চিন্তাচেতনার গভীরে প্রবেশ করেছিলো। এমনকি যখন জনৈক দার্শনিক বললেন, ‘তিনি তার সহমর্মিতা শুধু স্বদেশে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না, বরং তা ব্যাপ্ত হবে সমগ্র গ্রীসে’, তখন তার স্বদেশবাসীর জন্য তা বিস্ময় ও অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।
(চলবে ইনশাআল্লাহ)