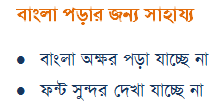নিজেকে মাসলাক (পথ ও পন্থা) সূত্রে দেওবন্দী বলতে বা লিখতে আমি দ্বিধাবোধ করি। কারণ তা থেকে ‘সম্প্রদায়-প্রীতির’ গন্ধ আসে। তাছাড়া কিছু মানুষ ‘দেওবন্দী মাসলাক’ শব্দ দ্বারা এ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, ‘দেওবন্দী’ বুঝি কোন মাযহাবী ফেরকা (ধর্মীয় উপদল)-এর নাম, যারা উম্মতের মূলধারা ও গরিষ্ঠ অংশের পথ ও মত থেকে সরে আলাদা কোন পথ বের করে নিয়েছে। অথচ হাকীকত ও প্রকৃত সত্য এই যে, দারুল উলূম দেওবন্দের চিন্তা-অঙ্গনের অনুসারী আলিমগণ ঈমান ও আমল এবং আকীদা-বিশ্বাস ও আচরণ-উচ্চারণের ক্ষেত্রে হুবহু ঐ ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্যের প্রবক্তা, যা চৌদ্দশ বছর ধরে উম্মতের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রজন্ম-পরম্পরায় চলে আসছে। তারা নতুন কোন আকীদাগত ফেরকা সৃষ্টি করেননি, বরং জমহূরে উম্মত (উম্মাহর মূলধারা ও গরিষ্ঠ অংশ) যুগপরম্পরায় যে সকল আকীদা ও বিশ্বাস পোষণ করে এবং যেসকল আমল ও কর্ম পালন করে, ওলামায়ে দেওবন্দও ঠিক ঐগুলোরই অনুসারী। তবে কখনো যদি তাঁদের (জীবন ও কর্ম এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের) উপর ‘ধূলোবালি’ আসতে দেখা গেছে তখন হিকমত ও প্রজ্ঞার সঙ্গে এবং অনমনীয়তা ও অবিচলতার সঙ্গে তা রোধ করার এবং দূর করার চেষ্টা অবশ্যই তারা করেছেন, যে ধূলোবালিকে অজুহাত করে বিদ্বেষী মহল এ ধারণা ছড়াতে চেয়েছে যে, তারা এক আলাদা ফেরকাপন্থী।
এ বিষয়ে হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহম্মদ তৈয়ব ছাহেব রহ.-এর রচিত ‘উলামায়ে দেওবন্দের দ্বীনী অভিমুখ ও মাসলাকী রূপ’ হচ্ছে অতি উত্তম একটি কিতাব, যার ভূমিকা লিখতে গিয়ে বিষয়টি আমি আরো স্পষ্ট ও বিশদরূপে আলোচনা করেছি।
তবে এখন আমি যে কথাটা বলতে চাই তা এই যে, আকীদা ও দ্বীনী বিষয়ে উলামায়ে দেওবন্দকে আমি নিজের জন্য ‘আদর্শ’ মনে করি। তারপরো একথা বলতে দ্বিধাবোধ করি যে, মাসলক ও পথ-মতের দিক থেকে আমি দেওবন্দী। কারণ তা থেকে ‘সাম্প্রদায়িকতা’র গন্ধ আসে।
তবে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই আমি বলতে পারি যে, জন্মসূত্রে অবশ্যই আমি দেওবন্দী। আল্লাহ তা‘আলার অপরিসীম দয়া ও দানে এ সৌভাগ্য অমি প্রাপ্ত হয়েছি যে, আমার জন্ম দেওবন্দে! সেই কল্যাণপ্রসূ বস্তি ও জনপদে যেখানকার ‘দারুল উলূম’ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, গুণ ও গরিমা, আযীমাত ও ইস্তিকামাত (বিধানের কঠোরতম স্তরের উপর অবিচল নিষ্ঠা) এবং মহত্তম কর্ম ও কীর্তি-গৌরবের অধিকারী এমন সব মহান ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব তৈয়ার করেছে, এই আখেরি যামানায় যাদের নযির পাওয়া অসম্ভব না হলেও মুশকিল অবশ্যই।
দেওবন্দে আমাদের পূর্বপুরুষ ‘মিয়াঁজী’ উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঐ যুগে ব্যবহৃত মিয়াঁজী উপাধি সম্পর্কে আমার আব্বাজান রহ. লিখেছেন
‘দেহাতে পল্লীতে যেসকল মক্তব প্রসার লাভ করেছিলো, যেখানে কোরআনশিক্ষার পর উর্দূ-ফার্সী ও অঙ্ক-গণিতের শিক্ষাদানের সাধারণ প্রচলন ছিলো, যার শিক্ষার মান বর্তমানের মিডেল স্কুলের চেয়ে উন্নত ছিলো, ঐ সকল মক্তবের শিক্ষকবৃন্দ ‘মিয়াঁজী’ উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করতেন। তাঁরা দ্বীনী তা‘লীমের সঙ্গে আমলের পবিত্রতা এবং আচরণের বিশুদ্ধতার অধিকারী হতেন। উদাহরণস্বরূপ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ,-এর শায়খ নূর মুহম্মদ ছাহেব রহ. তাঁর এলাকায় মিয়াঁজী নামে পরিচিত ছিলেন। তদ্রƒপ মিয়াঁজী মুন্নে শাহ ছাহেব রহ. পুরো দেওবন্দ এলাকায় ‘কাশফ ও কারামাতওয়ালা বুযুর্গরূপে পরিচিত ছিলেন।
হযরত আব্বাজান রহ. আরো লিখেছেন ‘নিজের খান্দান ও বংশপরিচিতির নির্ভরযোগ্য ও সনদ-সমর্থিত কোন নসবনামা ও বংশলতিকা আমার হাতে আসেনি। তবে শরীয়ত এ সকল ক্ষেত্রে সংযুক্ত সনদের শর্ত আরোপও করেনি, বরং বড়দের, বুড়োদের যবানিতে সাধারণ প্রসিদ্ধিকে যথেষ্ট মনে করেছে।
আমি আমার খান্দানের বুযর্গানের কাছ থেকে ‘নিবিড় পরম্পরা’যোগে শুনেছি যে, আমাদের খান্দান হযরত উছমান রা. এর আওলাদের অন্তর্ভুক্ত।’
আমার জন্ম হয়েছে ৫ই শাওয়াল, ১৩শ বিয়াল্লিশ হিজরীতে। এ জন্মতারিখই আমি পেয়েছি আব্বাজানের ‘বায়ায খাতায়’ (যে খাতায় যাবতীয় প্রয়োজনীয় কথা, বিষয় ও তথ্য টুকে রাখা হয়)।
যেহেতু তারিখ-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঐ পরিবেশ-পরিম-লে হিজরী সন-মাসেরই হিসাব রাখা হতো সেহেতু হযরত আব্বাজান রহ. হিজরী তারিখের সমান্তরালে খৃস্টীয় তারিখ লেখেননি। তবে পরে বিভিন্ন পন্থায় হিসাব করে জানা গেছে, আমার জন্ম হয়েছিলো ৩সরা অক্টোবর ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে।
এ ঘটনাও আমি আম্মাজান ও ভাইবোনদের কাছে শুনেছি যে, জন্মগ্রহণের পর একই দিন আমাকে যে বিছানায় শোয়ানো হয়েছিলো তাতে ছাদ থেকে ঝুপ করে একটা সাপ পড়েছিলো। যদি তখন সেটাকে কোনভাবে বিছানা থেকে সরিয়ে মেরে ফেলার ব্যবস্থা না হতো তাহলে হয়ত এ দুনিয়া আমার ‘গোনাহ’ থেকে নিরাপদ হয়ে যেতো (যা তাওবা দ্বারা মুছে যায়, কিন্তু মুসলিম জাহান কত বিশাল কর্ম ও কীর্তি থেকে বঞ্চিত হতো!অনুবাদক)
যাই হোক, জীবনের প্রারম্ভ-কালের শুধু চার বছর সাত মাস (অক্টোবর ১৯৪৩ এর মে থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত দেওবন্দের বস্তিতে যাপনের সুযোগ আমার হয়েছিলো। সেটা ছিলো শৈশবের স্মৃতিহীন ধূসর এমন একটা সময় যখন শিশুর নিজস্ব খেলাধূলার জগতের বাইরে অন্য কিছুর কোন প্রকার অনুভূতি থাকে না। পরে যখন সে বড় হয় তখন ঐ সময়কালের সবকিছু ভুলে যায়।
আমার অবস্থা ভিন্ন। দেওবন্দের শৈশবকালের এমন বহু বিষয় আমার এত স্পষ্ট মনে আছে, যেন এখন আমি নিজের চোখে দেখছি!
এটা ছিলো ঐ সময় যখন দেওবন্দের বাড়িঘরে বিজিলী ছিলো না। না পাখা-বাতি, না নলের পানি, না তেল বা গ্যাসের চুলা। বিজলী বাতির জায়গায় ছিলো কুপি-মোমবাতি বা হ্যারিকেন। নলের পরিবর্তে মটির মটকা বা পিতলের কলসে পানি রেখে দেয়া হতো, যা ভরার জন্য সাধারণত কোন ভিস্তির ‘সেবা’ গ্রহণ করা হতো, যারা চামড়ার বড় মশকে পানি বহন করে ঘরে ঘরে সরবরাহ করতো।
কোন সচ্ছল ও সৌখিন এলাকা হলে এজমালি নলকূপ বসানো হতো। তারপর হ্যান্ডেল উপর-নীচে চেপে বালতি-লোটা ভরা হতো। পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ছাড়াও এর একটা ফায়দা এই ছিলো যে, তাতে হাতের, বরং পুরো শরীরের ব্যায়াম হয়ে যেতো। আমার বয়স যেহেতু এধরনের ব্যায়ামের উপযোগী ছিলো না সেহেতু বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শুধু অন্যদেরকে নলকূপের হ্যান্ডালের সঙ্গে (উপর থেকে নীচে চাপার জন্য) ঝুলতে দেখেই খুশী হয়ে যেতাম। ঘরে পান করার সোরাহি ছিলো যাতে রাখা পানি খুব ঠা-া থাকতো।
বিজলীপাখার পরিবর্তে ছিলো হাতপাখা, যা এখন বিজলী চলে গেলে ‘অসহায়ভাবে’ মনে পড়ে।
মে-জুনের মৌসুমে গরমের তাপে দেয়াল ও সবকিছু উত্তপ্ত হয়ে থাকতো, তখন ভিস্তি এসে ইটবিছানো উঠোন-আঙ্গিনায় মশক থেকে পানি ছিটিয়ে যেতো। এর পর যখন পাখাসঞ্চালনের মাধ্যমে গুমোট বাতাস নিজের দিকে আনা হতো তখন মেঝে থেকে সোঁদা সোঁদা খোশবু আসতো। সেই সঙ্গে সম্ভাব্য শীতলতাও পাওয়া যেতো।
গরমের মৌসুমে যখন আম্মাজানের সঙ্গে খাটিয়ায় শয়ন করতাম তখন আমার এবং তারাভরা আকাশের মধ্যে না গ্যাস-বিজলীর কোন আড়াল হতো, না বিজলীবাতির ঝলকে তারাদের আলো কোনরকম নিষ্প্রভ হতো। ঝলমলকরা তারকারাজির মধ্যে নিহারিকাপুঞ্জ থেকে বিচ্ছুরিত শুভ্র আলো অনেক্ষণ ধরে আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম। ঐ নির্দোষ শৈশবে আমরা ভাবতাম, এটা হলো আসমানি সড়ক, যা আল্লাহ তা‘আলা ফিরেশতাদের চলার জন্য বানিয়েছেন। ঐ আসমানি সড়কপথে ফিরেশতাদের আসাযাওয়া কল্পনা করতে করতে আমার চোখজুড়ে ঘুম এসে যেতো।
০০০
দিল চায়, আমার এ স্মৃতি- লেখা সেই দূর শৈশবের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা দিয়ে শুরু করি। তবে এজন্য প্রয়োজন হবে সংক্ষেপে আমাদের পরিবারের ঐ সময়ে সদস্যদের আলোচনা করে নেয়া।
্এখানে আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতি শফি ছাহেব রহ.-এর পরিচয় পেশ করার প্রয়োজন নেই। কেননা এখনো আমার পরিচয় তাঁর মাধ্যমে হয়, তাঁর পরিচয় আমার মাধ্যমে হয় না। আজ আমি যা কিছু তা তাঁরই সঙ্গে সম্পৃক্তির কল্যাণে। যদি ভালো কিছু আল্লাহর তাওফীফে হাছিল হয়ে থাকে তবে তা তাঁরই মাধ্যমে, তাঁরই ফয়য-বরকতে। আর যদি কোন মন্দ কিছু থেকে থাকে তবে তা তাঁর ছোহবত ও তারবিয়াত থেকে যথাযোগ্য ফায়দা হাছিল না করার কারণে। আমার আব্বাজানের জন্য আমি যেন কবির সেই কবিতাপংক্তির প্রতিবিম্ব
যদি হয় দিল আমার কালো/ তবে তা তোমার গুলযারের গুল-তিলক/ যদি হয় লালাট আমার শুভ্র-উজ্জ্বল/ তবে তা তোমার গুলযারের গুলবাহার!
সুতরাং এখানে স্বতন্ত্রভাবে না হলেও আমার এ স্মৃতিচারণে তাঁর আলোচনা বারবার আসবে, এসেই যাবে।
যখন থেকে আমি অনুভূতির চোখ মেলেছি, আব্বাজান রহ.কে দু’টি কাজে মশগুল দেখেছি। ঐ সময় যদিও তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতির পদ এবং শিক্ষকতার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বহু তালিবে ইলম বিশেষভাবে তাঁর শিষ্যত্বগৌরব অর্জনের অভিলাষী ছিলো। তারা আব্দার-অনুরোধ ও মিনতি করে আমাদের ঘরে এসে তাঁর কাছে পড়তো। এটাকেই আজকের যুগে কোচিং বা টিউশন বলে; তবে বড় পার্থক্য এই যে, কোচিং ও টিউশন হচ্ছে এখন একজন শিক্ষকের জীবিকা ও রুটিরুযির মাধ্যম। পক্ষান্তরে দ্বীনী মাদরাসায় উস্তাদ-শাগিরদ সম্পর্ক হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ঊর্ধ্বজাগতিক। কোন তালিবের জন্য যদি নিয়মিত শ্রেণীকক্ষের পড়া যথেষ্ট না হয় তাহলে উস্তাদ পরম মমতা ও উদারতার সঙ্গে তাকে আলাদা পড়িয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, বরং পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে তিনি শাগিরদের হক আদায় করে থাকেন। এ উপলক্ষে তালিবে ইলম থেকে কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করার কথা মাদরাসা মহলে কল্পনাও করা যায় না, উস্তাদের আর্থিক অবস্থা যতই ভঙ্গুর হোক। তো আমাদের আব্বাজান রহ. এই মহৎ অনুভূতি ও জাযবার ভিত্তিতেই আগ্রহী তালিবানে ইলমকে আমাদের ঘরে বা মসজিদে পড়াতেন।
আমাদের মহল্লার মসজিদের নাম তো ছিলো ‘আদীনী মসজিদ কিন্তু মানুষের মুখের বোলচালে তা হয়ে পড়েছিলো ‘দীনী মসজিদ। ফারসিভাষায় ‘আদীনা’ অর্থ জুমা। সুতরাং আদীনী অর্থ এমন মসজিদ যেখানে জুমা হয়, অর্থাৎ জামে মসজিদ।
প্রথম দিকে আমাদের দাদা হয়রত মাওলানা ইয়াসীন ছাহেব রহ. এ মসজিদের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। পরে আব্বাজান রহ. মুতাওয়াল্লী হয়েছেন। এ মসজিদেও কখনো কখনো আব্বাজান-এর নিজস্ব দরস হতো।
দ্বিতীয় কাজটি হলো, যখন তিনি ঘরে থাকতেন, তাকে কিছু না কিছু লেখা অবস্থায়ই পেয়েছি। এমনকি গরমকালের রাত্রে যখন আমাদের বাড়ির আঙ্গিনায় ‘লণ্ঠন’ জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হতো, দেখা যেতো দোয়াতে কঞ্চিকলম চুবিয়ে ঐ লালটিনের আলোতে তিনি কিছু না কিছু লিখে চলেছেন। তখন কঞ্চি- কলমই ছিলো লেখার সাধারণ উপকরণ। বর্তমানের ঝর্ণা কলমের তখন প্রচলন ছিলো না। এছাড়া তিনি তাঁর বৈঠকখানার সংলগ্ন একটি ছোট আয়তনের ‘হুজরা’ বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ইবাদত করতেন। আমরা তাঁর যিকির বা তিলাওয়াতের আওয়ায পেতাম।
শৈশবের ঐ অবুঝ সময়ে হযরত আব্বাজান রহ.-এর ইলমী ও আমলী যোগ্যতা সম্পর্কে আমার আর কী ধারণা হবে! (সঠিক অর্থে তো এখনো প্রকৃত ধারণা নেই) তবে এতটুকু অবশ্যই ছিলো যে, শৈশবের ঐ ছোট্ট জগতে তিনিই ছিলেন আমার শৈশবীয় ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু। তিনিও আমাকে খুবই শফকত-পেয়ার ও ¯েœহ-আদর করতেন। আমার বড় ভাইদের প্রায় সকলে তাঁর ¯েœহের সঙ্গে ‘ডাট-মারের স্বাদও চেখেছেন’, কিন্তু আমার ভাগে শুধু তার আদরসোহাগই এসেছে।
একবার (সম্ভবত বার বছর বয়সে) আম্মাজানের সঙ্গে বড় ভাইয়ের কাছে লাহোর চলে গিয়েছিলাম। তখন তিনি ভাইজান মরহূমের নামে এক পত্রে লিখেছিলেন
‘তাক্বী (সাল্লামাহু)কে ছাড়া আমারও দিন পার করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।’
***
দেওবন্দের সেই ‘বাচ্পানের’ যামানায় আব্বাজানের একটিমাত্র সফরের কথাই আমার মনে আছে; মাদরাজের সফর। তখন তাঁর বিচ্ছেদ আমার জন্য ছিলো খুবই কঠিন ও ধৈর্যক্ষয়ী। এর উপর ‘তোররা’ হলো এই যে, যখন আব্বাজানের সফর থেকে ফিরে আসার সময় হলো তখন আমি যিদ করে ভাইজানদের রাজী করিয়েছিলাম, আব্বাজানের ইসতিকবালের জন্য আমিও তাঁদের সঙ্গে রেলস্টেশন যাবো।
আদরের ছোট ভাইয়ের যিদ বলে কথা! তারা রাজী হলেন, আর আমার আনন্দের কোন ‘ঠিকানা’ থাকলো না!
সবচে’ বড় আকর্ষণ বা শওক তো ছিলো আব্বাজানকে দেখা এবং ইসতিকবাল করা, তবে এর মধ্যে দু’টি পার্শ্ব-আনন্দের সংজোযনও ছিলো।
প্রথমত স্টেশন যাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক সওয়ারি ছিলো তাঙ্গা (ঘোড়াগাড়ী)। ঐ সময়ের জন্য তাঙ্গা ছিলো অভিজাত ও শাহী সওয়ারি। মহল্লায় ফাগ্গো নামে সুপরিচিত এক হিন্দু তাঙ্গাওয়ালা ছিলো। এধরনের উপলক্ষে তার গাড়ি পাওয়ার জন্য আগে থেকেই ফরমায়েশ দিয়ে রাখা হতো। এখানেও তাই করা হয়েছিলো। তাঙ্গায় চড়ার সুযোগ আমাদের খুব কমই হতো। নিকট দূরত্বের জন্য তো ছিলো ‘পায়দল’; মধ্যদূরত্বের জন্য ছিলো আম্মাজানের সঙ্গে ডোলী বা পাল্কিতে চড়া। তাঙ্গা কেরায়া করার জরুরত হবে, এতটা দূরে যাওয়ার উপলক্ষ কদাচিৎই হতো। সুতরাং আব্বাজানের ইসতিকবালে যাওয়ার মূল আনন্দের সঙ্গে তাঙ্গা নামের শাহী সওয়ারিতে সওয়ার হওয়ার পার্শ্ব আনন্দটাও শামিল ছিলো।
দ্বিতীয়ত রেলস্টেশনের পরিদর্শনও নিজস্ব সত্তায় উচ্চস্তরের বিনোদনের চেয়ে কম ছিলো না। বলাবাহুল্য, দেওবন্দের বস্তির পরিম-লে আবদ্ধ আমার মত বাচ্চার জন্য এ সুযোগও ছিলো বিরল। মোটকথা কয়েক দিক থেকেই আমার জন্য এটা ছিলো আনন্দপূর্ণ ও বিনোদনপূর্ণ সুযোগ। কিন্তু ঠিক সময়ে কী জানি কীভাবে আমার হাত পুড়ে গেলো। হাত পুড়লো কী, কপালই যেন পুড়ে গেলো! কেননা এ দুর্ঘটনার কারণে আমাকে ঘরেই থাকতে হলো। স্টেশনের যাওয়ার সবক’টি আনন্দ থেকেই আমি বঞ্চিত হলাম। বস্তুত এই একটি বঞ্চনা আমার জন্য কয়েকটি বঞ্চনার
সমষ্টি ছিলো, যার কারণে ঐ বঞ্চনার তৎকালীন অনুশোচনা এখনো আমার মনে আছে।
তবে পরবর্তী আনন্দের দৃশ্যটিও ভোলার মত নয়! হায়, কী মধুর দিনগুলো ছিলো! কী নির্দোষ আনন্দের জীবন ছিলো!!
হযরত আব্বাজান ঘরে প্রবেশ করে অন্য কোন দিকে মনযোগী হওয়ার পরিবর্তে সবার আগে আমাকেই ডাকলেন এবং এগিয়ে এসে কোলে তুলে নিলেন।
লণ্ঠনের আলোতে আব্বাজানের কালো ঘন দাড়ির ঔজ্জ্বল্য এবং ¯েœহ-আনন্দে উদ্ভাসিত মুখম-ল আজ এত বছর পরও আমার কল্পনার চোখে এমনই জীবন্ত, যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি।
(ইনশাআল্লাহ চলবে)